-
বাংলা সিনেমার সংকট নিয়ে: পঞ্চম পর্ব

কিঞ্চিৎ সুখী পাখিদের সংবেগ এবং আকাশে থমকিয়ে থাকা মেঘ …
আমি বুঝে গেছি যে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির ‘সংস্কৃতি’ উন্নত চলচ্চিত্রবোধ দিয়ে তৈরি হবে না। একদা ‘উন্নত চলচ্চিত্রবোধ’-এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল রাজনৈতিক বোধ। আসলে উন্নত চলচ্চিত্রবোধ ছিল উন্নত মানবজীবন, উন্নত মানবসমাজ, উন্নত চেতনার দ্যোতক। আর যাই হোক, সেই উন্নতি আর ‘উন্নয়ন’ এক ছিল না, এবং উচ্চমানের মানবজীবনের সঙ্গে কালচার-ইন্ডাস্ট্রির যোগ ছিল না। সেই চাহিদা এখন তামাদি হয়ে গেছে। সেইজন্যই পঁচিশ বছর আগে চলচ্চিত্রবোধ নিয়ে তৈরি অনেক ‘সাধ’ এখন, অন্তত আমার কাছে, খানিক অবদমিত নিউরোসিসেরই দ্যোতক হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে সাধ অবদমিত হতে বাধ্য, তা তো নিউরোসিসের জন্ম দেবেই।
জীবনে যে নিউরোসিসের ব্যক্ত হওয়ার সাধ্যি নেই, গল্পে তাকে ব্যক্ত হতে দেখলে আশ্বস্ত লাগে। ‘মানিকবাবুর মেঘ’-এ যদি দেখতাম – মানিকবাবু তার একাকিত্বের গলা টিপে দেওয়া পারিপার্শ্বিক নিয়ে, সমাজ নিয়ে ক্ষিপ্ত হিস্টেরিক হয়ে যাচ্ছেন, তার জরদ্গব পিতার বেতালসম ওজন বাঙালির অবসোলিট ইতিহাস ও ঐতিহ্যের রূপকধর্মিতা পাচ্ছে, তারপর পিতার মৃত্যুর পর মেঘের সন্ধান পেয়ে সবকিছু উলটে গিয়ে একটি দিশাহীন নিউরোটিক সমাজে তিনি নির্ভার সাবলাইম শান্ত প্রেমিক হয়ে যাচ্ছেন – স্বস্তি পেতাম যে তিনি আমার কষ্টটা বোঝেন। গল্পে একটা চরিত্রের আর্ক লাগে। লার্স ভন ত্রায়ারের ‘মেলানকোলিয়া’ মনে পড়ে – ছবির শুরুতে নায়িকা হিস্টেরিক, প্রায় মানসিক ভঙ্গুরতার খাদের কাছে দাঁড়ানো একজন মানুষ; ডগমে শৈলী স্মরণ করে ছবির ফর্মও অস্থির। এইবার শোনা যায় পৃথিবী ধ্বংসের সম্মুখীন; সেই বিপন্নতায় সমাজ যত উন্মাদ হিস্টেরিক হয়ে যায়, নায়িকা হয়ে যায় শান্ত। ছবির আঙ্গিকও হয়ে যায় শুধু স্থিতধী নয়, ধ্বংসের সম্মুখে অদ্ভুত সুন্দর! কেন নায়িকা শান্ত হয়ে যায়? কারণ অস্তিত্ত্বের বিপন্নতায় সে দৈনন্দিন অভ্যস্থ ছিল …।
‘মানিকবাবুর মেঘ’-এ চরিত্র বা আঙ্গিকের সেরকম কোনও আর্ক নেই; নেই সমসাময়িক ইতিহাসের তেমন কোনও ভার। সিনেমাটোগ্রাফি শুরুতেও নান্দনিক সুন্দর, শেষেও তাই। চন্দন সেনের অভিনয়ে যে ‘সত্য’ আছে, ছবিতে তার সন্ধান নেই। ছবিটি মানিকবাবুর নিউরোসিসকে বাইরে থেকে দ্যাখে; আঙ্গিকগত ভাবে একাত্ম হলে সমসময় নিয়ে ক্ষ্যাপামি করতে পারত। কিন্তু ক্ষ্যাপামি ছবিটির অভিব্যক্তি নয়, ছবিটির ‘অবজেক্ট’।
আমার ছবিটিকে নিয়ে একটি আপত্তি আছে। আপত্তিটি ব্যক্তিগত; আমি জানি বেশিরভাগ পাঠকের কাছেই তা গ্রাহ্য হবে না। ছবিটি একধরণের ছবি হতে চায়না, সেখানেই আপত্তি। মৃদু আপত্তি, অভিযোগ নয়। আশা করি সেই আপত্তিটা বোঝালে আগের দুই কিস্তির অনেকগুলি প্রসঙ্গতে পূণরায় আলোকপাত করা যাবে। মানিকবাবুর আত্মীয় বাঙালির কল্পনায় আছে। কিন্তু ‘মানিকবাবুর মেঘ’ সেই আত্মীয়তাকে অস্বীকার করে। তারা ‘বঙ্কুবাবুর বন্ধু’-র বঙ্কুবাবু বা ‘হরিপদ একজন সাদামাটা ছোটখাটো লোক’-এর হরিপদ (অঞ্জন দত্তের গানটির সূত্র ছিল ‘মহীনের ঘোড়াগুলি’-র একটি গানে। কিন্তু তাদের মত মানিকবাবু তো ইউএফও পাবেন না, মেঘই পাবেন। কারণ ইউএফও দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে কালচার হয় না, মেঘ দিয়ে হয়। জঁর দিয়ে বাঙালির কালচার হয় না। তাই ‘মানিকবাবুর মেঘ’ সাইফাই হতে চাইলো না, এই না-চাওয়াটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ।
বঙ্কুবাবু বা হরিপদ আধুনিক মানুষ ছিলেন; মানিকবাবুকে ‘অনাধুনিক সারল্য’ পারফর্ম করতে হয়। ইউএফও একটি আধুনিক কল্পনা; মেঘ টেনে আনলে মেঘদূতম্ টানা যায়, ধ্রুপদীয়ানা হয়। মানিকবাবু সুকুমার রায় পড়েন নির্মাতাদের অ্যাবসার্ডিটির তত্ত্ব দিতে, কারণ সুকুমার রায় আমাদের সাংস্কৃতিক আইকন হিসেবে পরিচিত। তিনি কার্ল সাগান বা দানিকেনও পড়তে পারতেন, বা হুইটলি স্ট্রাইবার। কিন্তু তাহলে তো প্যান্ডেমিকের সময় থেকে সারা পৃথিবীতে হিস্টেরিয়ার মত বাড়তে থাকা ইউএফও-উৎসাহের অংশীদার হয়ে তিনি সমসাময়িক হয়ে যেতেন! সমসাময়িক অথচ উন্মাদ – এই আত্ম নিয়ে ছবিটি ইন্টারেস্টেড নয়। একটা বাংলা শর্ট ফিল্ম আছে, উজ্জ্বল পাল পরিচালিত, নাম ‘ক্লার্ক’, একই বিষয় নিয়ে, একইরকম চরিত্র নিয়ে। ছবির ধরনটাও প্রায় এক। কিন্তু সেখানে মেঘের বদলে কী আছে, কীভাবে আছে, এবং কীরকম চমকপ্রদভাবে আছে, সেটাই দেখার। এই ছবিটি অস্বীকার করে না যে অমিত সাহা অভিনীত তার প্রধান চরিত্রটি ‘বঙ্কুবাবুর বন্ধু’ বা ‘হরিপদ’-র আত্মীয়।
অথচ যে ছবি আমার পাওয়ার ইচ্ছে, তার সম্ভাবনাটা কিন্তু ছবিটাই তৈরি করেছিল, কিন্তু আরোপিত হল নান্দনিকতা। মানিকবাবু বেশি কথা বললেন না, তাই তিনি হিস্টেরিক হলেন না ছবির প্রথমার্ধে। হলে তিনি আমাদের অবদমিত কন্ঠ হতে পারতেন, এই সময় নিয়ে তিনি হয়ত অর্থহীনভাবেই সরব হতে পারতেন (অর্থময় সরবতা তো অনেক শুনলাম; জ্ঞান দেওয়া ভিন্ন কিছু হয়না)। তার ছাদের গাছের সবুজ রঙ দেখাটা আমার দরকার ছিল, যে সবুজ তল্লাটে আর কোথাও নেই, মানিকবাবুর লালনে আছে। ‘অশনি সংকেত’ সত্যজিৎ কেন কালারে করেছিলেন, তখনকার বামপন্থী ক্রিটিকরা বুঝতে পারেননি। সত্যজিৎ সৌন্দর্য আরোপ করেছেন আকালের ছবিতে, তারা অভিযোগ করেছিলেন। কিন্তু সত্যজিৎ দেখাতে চেয়েছিলেন যে বাংলাদেশ সুজলা সুফলা হয়েও আকালে আছে, অর্থাৎ এই আকাল মানুষের তৈরি, প্রকৃতির নয়। ‘মানিকবাবুর মেঘ’-এ আরোপিত হল সাদা-কালো। সেই সবুজের রকমফের এক্সপ্রেসিভ হতে পারত ছবির মুড অনুযায়ী, বা মানিকবাবুর মুড অনুযায়ী। মেঘ আসার পর সেই সবুজ অভিমানী হতে পারত স্রেফ রঙের রকমফেরে, মেঘ-মানিকবাবু-গাছের ত্রিকোণ-প্রেম তৈরি হতে পারতো ‘অযান্ত্রিক’-এর মত – হল না, আরোপিত হল সাদা-কালো। বললাম না, ছবিটা মানিকবাবুকে বাইরে থেকে দেখছে; যেন মানিকবাবু ছবির শিশিতে ভরা একজন বাতিল মানুষ, ছবিটির তার মত বাতিল ছবি হওয়ার সাহস নেই। বাতিল মানুষের সঙ্গে আঙ্গিকগত ভাবে একাত্ম হওয়ার বাতিল ছবির ফর্ম দেখতে চাইলে খুঁজুন পার্থপ্রতিম চৌধুরীর ‘শুভ কেমন আছো’।
‘মানিকবাবুর মেঘ’-এর উদ্দিষ্ট দর্শক যদি মস্কোর ফেস্টিভালের দর্শক হয় তাহলে ছবিটির অনেক রেফারেন্সে subtle হতে পারবে না, তারা তো এই বাস্তবতা চেনে না। আর কলকাতায় যারা চেনে তাদের যদি দেখলে জমিয়ে কাব্য ও কালচার হবে সেই আশ্বাস দেওয়া না যায়, তারা দেখবে না। যারা পর্দায় মানিকবাবুকে দেখে “আহা আটপৌরে সাধারণ জীবন!” বলেন তাঁরা সেই জীবনের উর্দ্ধে উঠে গেছেন বলে বলেন; যেমন যারা এখন “আহা অপু দুর্গা!” বলে তাদের বাড়িতে কন্যাসন্তান সুচিকিৎসার আর সুষম খাদ্যের অভাবে নিউমোনিয়ায় ভুগে মারা যায় না। অতএব, যদি এমন হয় যে এই ফর্মের ছবি শুধুই এরাই দেখবে, তাহলে বানানো একরকম হবে। হয়ত সেটা এরকমই।
বাস্তববাদী ছবির সবচাইতে জোরের জায়গা কোথায়? যেহেতু ঐতিহাসিক বাস্তব সদাপরিবর্তনশীল, তাই সবসময় পুঁজিবাদের রকমফেরে নতুন নতুন বাস্তবতার ভাঁজ তৈরি হচ্ছে। এখন যারা নিম্নমধ্যবিত্ত, তাদের আয়ের পথ ২০ বছর আগের নিম্নমধ্যবিত্তের চাইতে আলাদা। তাদের সেভিংস-এর ধরনও আলাদা (হয়তো তারা লক্ষ্মীর ভাঁড় ব্যবহার করে না), তাদের বিপন্নতার ধরন আলাদা, তাদের নৈতিকতাও আলাদা। অতএব, বাস্তববাদকে ফলপ্রসূ থাকতে হলে এই ঐতিহাসিক বাস্তবের খুব সূক্ষ্ম বদল, ফারাক, তারতম্যগুলোকে দেখতে শিখতে হয়। এর সঙ্গেই একটা জিনিস যুগপৎ চলতে থাকে, সংস্কৃতি নিজের ‘কৃত্রিম বাস্তবতা’ বানায়। হরিপদ কেরানির জগত যতটাই প্রামাণ্য, ততটাই কালচারাল চিহ্নসমষ্টি, অর্থাৎ অনেকটাই শিল্প ও সংস্কৃতি থেকে কুড়িয়ে নেওয়া বা সোজা কথায় ক্লিশে দ্বারা নির্মিত একটা জগত। সেটা যতটা না উত্তর কলকাতার বাস্তব তার চাইতেও কবিতা, গান, গল্প থেকে তৈরি করা বাস্তব। আগের প্রক্রিয়াটা হল বাস্তবে কী কী বদল হচ্ছে তা দেখা, কোনটা নতুন বা ধারাবাহিকতা ভাঙলো তা খেয়ালে রাখা, আর পরেরটার কাজ হল representation-এ continuous বা consistent-কে দেখা। দ্বিতীয় পন্থাটা আমার কাছে আদপেই ব্রাত্য নয়, যদি সেটা সমসময়ের উৎস হতে ভিন্ন আলোর উৎসারণ ঘটায়, বাইরে থেকে আলো ফেলার বদলে। আর যদি সেই পন্থা নিজের কৃত্রিমতা নিয়ে সচেতন থাকে।
অর্থাৎ এমনও তো হতে পারে যে সিনেমা এমন এক সিন্থেটিক জগৎ দেখালো যেটা আসলে কোথাও নেই, যেটা আসলে বাঙালির ঐতিহাসিক বাস্তবতা থেকে কিছু কোলাজ বানিয়ে গড়া একটা ‘সিনেমাটিক বাস্তব’, যেখানে একলা হরিপদর বাড়িতে যে ইউএফও আসে তাই নয়, ওর তিন পুরুষ ধরে এসেছে! ওর প্রতি প্রজন্মই ইউএফও-য় হাপিশ হয়ে গেছে। ইউএফও-ই আবার একদিন আরেক প্রজন্মকে ওই বাড়ির ছাদে নামিয়ে দিয়ে যায়। বাড়ির চাকর-বাকর কেয়ারটেকাররা সেটা জানে, তারা আবার ওর দেখভাল করে, হরিপদরা আবার কেরানি হয়ে যায়।
এমনটা না চাইলে, বাস্তববাদ ব্যবহার করলে, দৃশ্য-শব্দ-ডিটেলের উপাদান হিসেবে ব্যবহার না করে অস্তিত্বের বাস্তববাদ ব্যক্ত হোক। ‘মানিকবাবুর মেঘ’ নিয়ে অনেক লেখা হচ্ছে। সেই লেখাগুলো পড়েই বোঝা যাচ্ছে যে এই ছবি এমন এক নান্দনিকতা উদ্রেক করছে, যেখানে নিউরোসিসের কোনও স্থান নেই। তুলতুলে কাব্যিক সুখী গদ্য সেখানে। এই হয়, জীবনানন্দ থেকে বিনয় পেরিয়ে আমরা কাব্যিকতা বলতে এই ভাষায় মজে থাকা বুঝি; এই ছবি দেখে বাঙালি সেই ভাষায় মজার একটা সুযোগ পেয়েছে!
আমাদের অবদমিত কথাগুলো ব্যক্ত করতে হবে, নিউরোটিক হতে হবে নতুন ছবিতে। তার আগে আমাদের অবদমনকে স্বীকার করতে হবে, চিনতে হবে। আমরাই আমাদের এক নাগরিক কেরানিকে দুরত্ব থেকে দেখব না। তার অসুখ আমাদেরও অসুখ, আমাদের ছবির অসুখ হোক। তুলনায় ‘পারিয়া’-র যে ফর্ম ও আঙ্গিক, সেই ছবিতে সেই নিউরোসিস ব্যক্ত করার সম্ভাবনা আছে। ‘পারিয়া’-ও একাকী অসুখী একটি মানুষের ছবি। মানিকবাবুর কাছে যা মেঘ, লুব্ধকের কাছে তা কুকুর – মানবসমাজ জাত অর্থহীনতার যুগে অ-মানুষী অবলম্বন। তফাত হল, কুকুরকে অ্যাবিউজ করা যায়, মেঘকে যায় না। যায় না? গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর যুগে মেঘকে টক্সিক কেমিকেলে ঠুসে দিলেই মেঘকে অ্যাবিউজ করা হয়, হচ্ছে। ‘টক্সিক ক্লাউড’ কাকে বলে গুগল করুন। সেই মেঘ বিষবৃষ্টি ঝরালে তখন মানিকবাবু কী করবেন? কেন মানিকবাবু মেঘের মধ্যে মানুষের বিষ ঠুসে দেওয়া টের পেলেন না?
‘মানিকবাবুর মেঘ’-এর এই কেরানির কোট আর ধুতির মত ‘সাদা-কালো’, এই ‘সংলাপহীনতা’ আর্ট নয়, কালচার, গ্লোবাল আর্টহাউজে পশ্চিমবঙ্গের কালচারাল আর্কাইভাল এথনোগ্রাফিক অবদান। সেইজন্যই ছবিটি বিরক্ত না করে আমাদের আরাম দিচ্ছে, আমরা নিজেদেরকেই ‘বাইরের চোখ’ দিয়ে দেখছি বলে। ছবিটি আদপেই ব্যর্থ নয়, কালচারালি সাক্সেসফুল, ব্যর্থ আমার ছবির সাধ।
বা বলা ভাল, এই জীবনের সার সত্য, ব্যর্থ আমার নতুন বাংলা ছবির সাধ। কেন যে নিজের ভাষায় নতুন ছবি দেখার সাধ এখনও আছে! বাংলা ছবি ওপার বাংলাতেও হয়, তার মান উর্ধ্বমুখী। কিন্তু ইতিহাসের খেয়ালেই সেখানকার সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত আমার ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত নয়; ভাষা এক, ভূমি এক, সংগীত এক, কাব্য এক হলেও। নিজেদের সিনেমা প্রয়োজন হয় নিজেদের প্রেক্ষিতে বাঁচাকে অর্থময় করতে।
এই লেখায় যে আমি ‘পারিয়া’ বা ‘মানিকবাবুর মেঘ’-কে আদপেই অপর্যাপ্ত ছবি বলছি তা নয়, ছবিগুলোয় আরো কী মাত্রা যুক্ত করা যেত তাই বললাম। এটা ‘কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম’ হল কিনা, পাঠকদের বিচার্য। ‘পারিয়া’ ডার্ক অ্যাকশন ছবি হতে চায় যার একটি শুভবোধসম্পন্ন হৃদয় আছে, শুধুমাত্র তামসিকতার এক্সারসাইজ হতে চায়না। ‘মানিকবাবুর মেঘ’ প্রান্তিক একটি চরিত্রের সংবেদনশীল একটি ছবি হতে চায়। আমার সমালোচনা ছবিগুলির এই অভীপ্সার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, এটাও স্বীকার করছি যে ছবিগুলি সেরকম খানিকটা হয়েছে। কিন্তু পুরোপুরি হতে পারেনি। পারাটা দরকার। আমি যে মাত্রাগুলি চাইছি সেগুলি অযাচিত কিনা তা পাঠকের বিচার্য।
এই লেখায় যার বিরোধিতা আমি করেছি, তা হল একধরণের আরোপিত সংস্কৃতির ধারণার, সে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত বাঙালির হোক বা গ্লোবাল আর্টহাউজ সিনেমার। কারণ এই আরোপিত ‘কালচারাল’ পলি বাংলা ছবিকে আরো আন্তরিক হতে বাধা দিচ্ছে বলে আমি মনে করি। বাংলা ছবিকে আরো ‘রিলেটেবল’ হতে হবে; এবং তার গণ্ডী পেরিয়ে রিলেটেবল হতে হবে, এবং তার ভাষিক সীমানার মধ্যেই রিলেটেবল হতে হবে। অন্য কথায়, কলকাতা এবং মাল্টিপ্লেক্স ছাড়িয়ে যেতে হবে, এবং আপামর বাঙালির কাছে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে হবে, নেহাতই বিনোদন বা কালচারের নুড়ি-পাথর হিসেবে নয়।
এই লেখায় আমার সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আপত্তিটা হয়ত অনেকের অদ্ভুত ঠেকবে। আমি সেই ব্যাপারে সবার সহমতও প্রত্যাশা করছি না। আগেও বলেছি, শিল্পকর্মই সংস্কৃতির উপাদান। কিন্তু শিল্পকর্মের গ্রহণে যে খোলা মনের মুক্তি কাম্য, তার নিরিখে কোনও কোনও যুগে সংস্কৃতি খাঁচার মত। সে অর্থে কালচার হল আর্টের চিড়িয়াখানার মত, তাতে বিচিত্র প্রাণীরা সংরক্ষিত থাকে, কিন্তু বদ্ধতায়। সংস্কৃতি নিয়ম-নিদানে বদ্ধ থাকে, সংস্কৃতি তৈরি হয় একটি জাতি বা গোষ্ঠীর সংখ্যাগুরুর ঐকমত্যে। এই মুহুর্তে, নতুন সিনেমাকে সংস্কৃতির বিরোধীতা করতে হবে – আমার মতে।
বাংলার কাব্যিক আর্ট সিনেমার সংস্কৃতিই বলবে ‘মানিকবাবুর মেঘ’-এ নিউরোটিক ভায়োলেন্স অসম্ভব, massy ছবির সংস্কৃতিই বলবে ‘পারিয়া’-র নায়ককে গতে বাঁধা পৌরুষেই বাঁধতে হবে। যে পৌরুষে অধুনার অ্যাকশন-হিরোর আলফা-ম্যাস্কুলিনিটির মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি নেই, তার দ্বারা যেন rage সম্ভব নয়। অর্থাৎ, যখনই কেউ একটি ছবি বানাচ্ছেন, তখন সেই ছবির যে সর্বসম্মত ‘কালচার’, তাকে লঙ্ঘন করা যাচ্ছে না, বরং তা থেকে ছবিটি যেন স্বীকৃতি চাইছে। ‘পারিয়া’ বলছে আমি কি massy হলাম? ‘মানিকবাবুর মেঘ’ বলছে আমি কি arty হলাম? দর্শকও সেই ধারণার ঘেরাটোপের সীমাবদ্ধতাই চাইছে। একে বলা যায় ossification – বাংলা শিল্প-সংস্কৃতির হাড়-গোড় জমাট বেঁধে গেছে, তাতে নতুন কল্পনার নমনীয়তা দেওয়া যাচ্ছেনা।
‘পারিয়া’ প্রসঙ্গে অনেকে কোরিয়ান ছবিতে ভায়োলেন্সের কথা তুলেছেন। কোরিয়ার ছবির কথা এরকম তীব্র ভায়োলেন্সের যে কোনও ছবির প্রসঙ্গেই ইদানিং তোলা হয়। কিন্তু সেই তুলনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রাকে ভুলে যাওয়া হয়। কোরিয়ার শৈল্পিক অভিব্যক্তিতে han নামে একটি ধারণা আছে, যার ইংরেজি প্রতিশব্দ হয়না, যে ধারণার উৎস কোরিয়ার ইতিহাসে প্রোথিত। উইকিপিডিয়া উদ্ধৃত করছে – “Han is frequently translated as sorrow, spite, rancour, regret, resentment or grief, among many other attempts to explain a concept that has no English equivalent … A complex emotional cluster often translated as ‘resentful sorrow.” এই ‘ভাব’-টি কোরিয়ার ছবি যে কোনোরকমের জঁরেই প্রকাশ করতে পারে, তীব্র ভায়োলেন্স তার একমাত্র ধরন নয়, তীব্র বিরহতেও তার প্রকাশ সম্ভব, সম্ভব অজানা আতংকের উদ্রেকেও। অতএব, সিনেমাটিক ভায়োলেন্সে যাঁরা কেবলই কোরিয়ান ছবির প্রভাব দেখতে পান, তাঁরা কেবলমাত্র উপরিতলটি দেখছেন। দেখছেন না এই ‘আধিক্যের নন্দনতত্ত্ব’ কীভাবে প্রায় অব্যক্ত একরকম জাতীয় অনুভূতিকে আকার দিচ্ছে। তাই অনুকরণ ছাড়া কিছু শিখছেন না।
যেভাবে এই ‘বোধ’ কোরিয়ান জঁর ছবিকে উন্নীত করে – এইভাবেই সংস্কৃতি শিল্পের সহায়ক হতে পারে। অর্থাৎ সংস্কৃতিতেই মুক্ত-নমনীয় একটি ‘ফাঁকা আকার’ আছে যাতে যে কোনোরকম ‘অভিজ্ঞতা’-কে ধারণ করানো যায়। কিন্তু ক্রাফটের বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন এখানেই যে অভিব্যক্তিতে একরকম ইশারা রেখে দিতে হবে; আবার ইশারাটা রাখতে হবে ‘আধিক্য’ দিয়ে। অর্থাৎ যা ‘দেখানো হচ্ছে’, তার উর্দ্ধে, বাইরে যেন ইঙ্গিত করবে ছবির আধিক্য। এই ‘উদ্রেক’-এর ফলে যেটা হয়, কেবলমাত্র উদ্দিষ্ট দর্শকের রুচি-শ্রেণি-কালচার-পছন্দের মধ্যে ছবির গ্রহণ সীমাবদ্ধ থাকে না। আরেকটু বোঝাচ্ছি, আমাদের বাংলা ছবি যত দিন যাচ্ছে ততই তার address (যার বাংলা উদ্দেশ্য ও ঠিকানা দুই-ই হতে পারে) সংকুচিত করে দিচ্ছে। একটি ছবি একটি উদ্দীষ্ট গোষ্ঠীর বাইরে যেতে পারছে না। কিন্তু কোরিয়ান ছবির (বা শিল্পের) এই বিচিত্র মাত্রাটি ছবিটিকে শুধুমাত্র একটি গোষ্ঠীতে সীমাবদ্ধ রাখে না, কারণ ‘হান’ সবার মনেই বাসা বাঁধে, মধ্যবিত্ত বা প্রান্তিক সবার। যিনি দেখছেন তিনি আলোড়িত হলেই, যেহেতু ছবির আবেগ-অনুভূতিতে আধিক্য আছে এবং আছে না-বলা কথার ইশারা, অভিব্যক্তি রূপকধর্মীতা পাচ্ছে আর দর্শক তাঁর নিজের বোধ এবং অভিজ্ঞতা দিয়ে শুন্য স্থান পূর্ণ করতে পারছেন। জমাট বাঁধা কালচার এটাই করতে দেয় না।
কেন কোরিয়ার প্রসঙ্গ আনলাম? কোরিয়ার ‘হান’ নিয়ে পড়তে গেলে দেখবেন তার উৎস ঠিক খুঁজে না পাওয়া গেলেও, কোরিয়ার ইতিহাসে যে বারংবার বহিরাগত শক্তিশালী জাতির, চীন ও জাপানের, শাসনে পর্যুদস্ত হওয়ার অভিজ্ঞতা, দেশবিভক্ত হওয়ার অভিজ্ঞতা, নিজেরই অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার বা অতীতকে স্পর্শ করতে গেলে যন্ত্রণাকীর্ণ হওয়ার ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাতেই সেই উৎস আছে বলে অনেকে মনে করছেন। তারপর এই বোধ ছড়িয়ে পড়ছে জনপ্রিয় এবং কুলীন-শিল্পে, সংস্কৃতির মূলধারা এবং প্রান্তিকে, সর্বত্র। আমাদের এই পোড়া বাংলার ইতিহাসে সমকক্ষ বোধ পাওয়া কি খুব কঠিন? কঠিন তখনই হয়, যখন প্রথমত, তা deny করা হয়, অবদমিত হয়। দ্বিতীয়ত, এমন কালচার তৈরিই হয় যা কিনা অসুখী-অস্বস্তির যা কিছু তাকে বাইরের ঘরের বাইরে রাখে। আজ সত্যিই অবাক লাগে ভাবতে কীভাবে এই ভাষায় একই সঙ্গে ‘সপ্তপদী’ ও ‘সুবর্ণরেখা’ তৈরি হয়েছিল। এই দুটি ছবির আত্মীয়তা কোথায়, তা পাঠকের কল্পনা আর স্মৃতির উপরেই ছেড়ে দিলাম। এবং আরেকটি ছবির কথা এই প্রসঙ্গেই মনে করিয়ে রাখলাম, যা সবার ভাল লাগেনি, প্রদীপ্ত ভট্টাচার্যের ‘রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত’।
এই লেখা আপাতত মুলতুবি থাকলো
যখন এই লেখা লিখছি তখন প্রতিবেশী দেশে অগ্নিগর্ভ অবস্থা। সেই দেশের ভাষা বাংলা, এই দেশের ল্যান্ডস্কেপের সঙ্গে আমাদের ল্যান্ডস্কেপের তফাত নেই, তফাত নেই ভূমিলগ্ন মানুষের অবয়বের, তফাত নেই গাছের বা পুকুরের বা পাখির। সেই দেশে বাংলা ভাষায় সিনেমার যে উজ্জ্বল সম্ভাবনা ছিল তা নিশ্চয়ই ধাক্কা খেলো, কিন্তু বলা যায়না এক নতুন দিশাও পেয়ে যেতে পারে। তাই, আপাতত এই মুহূর্তে এই লেখার কোনও প্রয়োজন নেই।
দিনবদল হোক বা নতুন একটি ফিল্ম – তার জন্ম হয় তরুণ মনে। যে সিনেমা সেই তরুণের প্রৌঢ় অভিভাবকদের মনে প্রথমে আসে, সেই সিনেমা বর্তমানে টিকে থাকতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতের দিশা দিতে পারে না। এটাই আক্ষেপের, তরুণরা দিনবদল আনে, কিন্তু ক্ষমতায় আসে তাদের অভিভাবকরা। বাংলা সিনেমা প্রৌঢ়দের হাত থেকে তরুণদের হাতে আসুক। এবং সেই তরুণের যে vision – তাকে ক্ষুণ্ন করলে, ব্যাহত করলে কোনও ইন্ডাস্ট্রির যে আখেরে কিছু লাভ যে হবে না তা আশা করি এতদিনে প্রমাণ হয়ে গেছে, এবং গিল্ডরা সেটা জানেন।
একটা ছবি বেরিয়েছে – ‘কালিয়াচক চ্যাপ্টার ওয়ান’। ছবিটি কেমন, বা কজন সেটা দেখবে সেটা প্রশ্ন নয়। হয়তো দুর্বল ছবিই হবে। কিন্তু ছবিটি মালদায় বানানো। ওখানকার যুবকরা, অভিনেতারা অভিনয় করেছেন, তাদের ভাষা, তাদের সুরে কথা বলছেন, তাদের অঞ্চলে অভিনয় করছেন – এটা খুব মূল্যবান বলে মনে হয় আমার। সিনেমা ডিজিটাল হওয়া মাত্র এটা হওয়ার কথা ছিল; কেন হয়নি তা ইতিহাস বলবে।
এই লেখা পড়ে অনেকের মনে হতে পারে আমি বাংলা ‘আর্ট সিনেমা’-র devaluation ঘটালাম, বদলে ‘বাজারি’ ছবির পুনর্জাগরণ চাইছি। মূলধারার ছবির যতই আপৎকালীন প্রয়োজন থাকুক না কেন, সেটা তো ‘কমপ্রোমাইজড’ সিনেমা– বিদ্বজ্জনের মনে হবে। কিছু কথা ‘পলিটিকাল রূপক’-এ বলি তাহলে; জ্ঞান দিচ্ছি না, নিজেকেই বোঝাতে চেষ্টা করছি। উন্নত আর্ট সিনেমাই একটি আধুনিক শৈল্পিক চেতনার অভীষ্ট, ঠিক যেমন ধর্মনিরপেক্ষ ওয়েলফেয়ার স্টেট একটি আধুনিক দেশের অভীষ্ট। কিন্তু যে প্রজন্মকে সেই ধর্মনিরপেক্ষ ওয়েলফেয়ার স্টেটের মূল্য বোঝানো হয়নি, বা সেই মূল্যবোধ সীমাবদ্ধ থেকে গেছে মুষ্টিমেয় শিক্ষিতদের হাতে, সেই গোটা প্রজন্ম যখন দ্রোহের তাড়নায় রাস্তায় নামবে, যেহেতু তাদের সেই দ্রোহের ধারণা ভাবনার দিক দিয়ে সংখ্যাগুরুর নিরিখে ‘কমপ্রোমাইজড’, তা কি স্থগিত থাকবে? থাকবে না। অপশাসন যখন পড়বে নিজের ভারেই পড়বে, আগামী তৈরি থাকুক বা না থাকুক। দ্রোহের ক্ষণ সবসময়ে প্রস্তুতির পর আসে না; এবং সফল দ্রোহের পরও আগামীর শাসনও কম্প্রোমাইজড হয়ে যেতে পারে, যেহেতু যারা দ্রোহ করে তারা ক্ষমতাসীন হয় না। কিন্তু তাতে দ্রোহের মূল্য কমে না, ইতিহাস রচিত হয় মানুষের হাতে, তাও দ্রোহের ‘ড্রেস-রিহার্সাল’-টি হয়, কী চাওয়া হয়েছিল, কী পাওয়া গেল না এবং কেন পাওয়া গেল না তা আর অনুমানে সীমাবদ্ধ থাকেনা, অভিজ্ঞতায় জারিত হয়। আগামী অতএব সবসময়েই সম্ভাবনা হিসেবে জ্যান্ত থাকে। ক্ষয়িষ্ণু গণতন্ত্রে যে জিনিসটা অবমূল্যায়িত হয় তা হল গণতন্ত্রের মর্ম। সেই আবহে যে প্রজন্ম বাড়বে সে যে সেই মূল্যটা জানবে না তাই বাস্তব; কিন্তু তাও যে সে অপশাসনকে রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুভব করেছে সেটাও সত্য।
বাংলা সিনেমার ‘আর্ট’-এর দিকটা ক্ষয়ে গেছে। ক্ষয়ে গেছে সাধারণ ফিল্ম-সেন্স; সিনেমায় শিল্পচেতনা মধ্যবিত্তর প্রিভিলেজের ও আয়েসী যাপনের উপাদান হয়ে গেছে, তাতে বহুদিন হল যেটা নেই সেটা হল কোনরকম earnestness। আর্টহাউজ সিনেমার ক্ষেত্রে আমরা শুধুই গ্লোবাল কর্পোরেটের নান্দনিকতায় টিক মার্ক দিয়ে যাচ্ছি। অতএব একে ফেলে দিতে হবেই; দিতে হবে যাতে ভবিষ্যতে আবার নতুন করে ফিরিয়ে আনা যায়। একটা প্রজন্ম কেটে গেছে যাদের ফিল্ম-সেন্সের শিক্ষা নেই, যাদের জানানো হয়নি সিনেমার সম্ভাবনার কথা। তারা যদি বাংলা সিনেমাকে রিজেক্ট করে বিনোদনমূলক ‘কম্প্রোমাইজ’ চায়, তাই আসবে, কিন্তু তাতেও আন্তরিকতার অভিব্যক্তি থাকার সম্ভাবনা বেশি। কারণ শহুরে উন্নত সিনেমার ‘শাসকরা’ তাদের দায়িত্ব পালন করেনি, তাদের ক্রাইসিস স্বীকার করেনি, নিজেদের গণ্ডীতে তৃপ্ত থেকেছে, তাতে হারিয়ে গেছে অভিব্যক্তির সমস্ত সম্ভাবনা, হয়ে গেছে কালচারের চিহ্নসমষ্টি। এই সিনেমা থাকবে না। তার বদলে যে সিনেমা আসবে তাও ‘পর্যাপ্ত’ হবেনা, কিন্তু তাতে অধুনার রিজেকশন থাকবে। হয়ত স্পষ্ট ওয়েলফেয়ার স্টেটের ধারণা না থাকলে যেমন মৌলবাদ বা দক্ষিণপন্থা দ্রোহকে হাইজ্যাক করে নিতে পারে, সেভাবেই আগামীর নতুন বাংলা সিনেমাকে হাইজ্যাক করে নিতে পারে প্লেবিয়ান বা লুম্পেন অস্থিরতার অপরিশীলতা। কিন্তু তাও এই নিষ্ফলা মেট্রোপলিটান মধ্যবিত্তের বাংলা সিনেমা যাক; আসুক নিরলঙ্কার অস্থিরতা যাতে অস্তিত্বের এনার্জি আছে। কেন? কারণ এই মধ্যবিত্তটাই আর আধুনিকমনস্ক নেই, জরদ্গব হয়ে গেছে।
আপাতত মনটা পশ্চিমবঙ্গের বাংলা সিনেমায় নেই, বাংলাদেশে আছে …।
একটা দুর্বোধ্য উথাল-পাথাল সময়ে বাঁচছি। সেখানে সিনেমা থেকে আর কিছু চাইছি না, চাইছি এই সময় নিয়ে কিছু গল্প দেবে যা দিয়ে অস্তিত্বকে দ্যোতনাময় করব, কিছু শৈল্পিক অভিজ্ঞতা দেবে যার মাধ্যমে এই বেবাক জীবনকে একটু নতুন করে বুঝবো, কিছু কল্পিত চরিত্রকে আর মুহূর্তকে অর্থময় করে মনে রেখে দেবো এই অর্থহীনতার বিশ্বে, অসাড় করা সময়ে অচেনা আবেগের আড় ভাঙবে, আর ফাউ হিসেবে পাবো রসাস্বাদনের আনন্দ। শর্ত এতটুকুই, সেই সিনেমাকে আন্তরিক হতে হবে, ফাঁকি মারলে বা চালাকি করলে চলবে না। ইতিহাসেরই খেয়াল, আন্তরিকতার অনুভবের চাইতে ফাঁকি আর চালাকিগুলো চোখে পড়ে যায় বেশি।
(শেষ, আপাতত)
-
বাংলা সিনেমার সংকট নিয়ে: চতুর্থ পর্ব
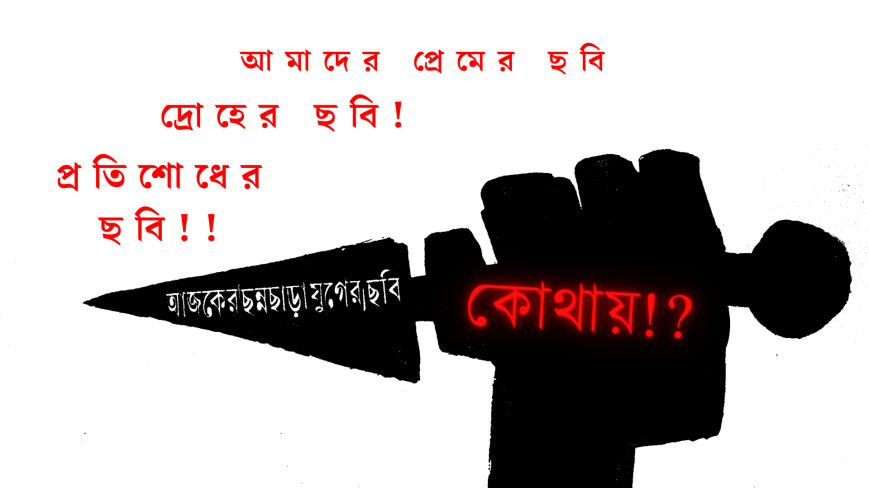
আমাদের পুনরুজ্জীবিত জনপ্রিয় মূলধারা প্রয়োজন
একটি প্রস্তাব আছে। সাংস্কৃতিক পশ্চিমবঙ্গীয় ফিল্মমেকাররা তো মূলধারা নিয়ে ভাবা বন্ধ করে দিয়েছেন। যারা ‘বৌদ্ধিক’ চলচ্চিত্রচর্চা-য় অংশগ্রহণ করতে চান, তাঁরা বিকল্প-তে পা না রাখলে কৌলিন্য পান না; যাঁরা মূলধারায় কাজ করেন, তাঁরা বৌদ্ধিক ‘চলচ্চিত্রচর্চা’-য় পা রাখেন না। এতে আখেরে লাভ হচ্ছে না, কারণ সবাই মূলধারার ছবিই আসলে প্র্যাক্টিস করছেন, বাংলায় আর্ট সিনেমা প্র্যাক্টিস বহুদিন হল হচ্ছে না। অর্থাৎ নতুন ছবির ভাষা, নতুন ছবির ফর্ম নিয়ে দীর্ঘদিন কোনও ভাবনাচিন্তার অবকাশ, সমর্থন বা পরিবেশ পাচ্ছেন না ফিল্মমেকাররা। পেলেও তা জনমানসে বা আগামীর ফিল্মমেকিং-এ ছাপ ফেলতে পারছে না। যদি আখেরে মেনস্ট্রিম ফরমাটে ছবি করাই সার সত্য হয়, তাহলে তা নিয়ে তাত্ত্বিক বা ক্রিটিকাল ভাবনা হবে না কেন? এখানেই সমস্যা। যে তরুণ সিনেমা নিয়ে বৌদ্ধিক চর্চা করতে চান, তিনি মূলধারার ছবি দেখা বন্ধ করে দিয়েছেন। যিনি মূলধারার ছবি দ্যাখেন, তিনি বৌদ্ধিক কথাবার্তা শুনলেই ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মত রেগে যান।
গত দশ-পনেরো বছরের আমাদের যে ছবিগুলো প্রিয়, তার তালিকা করলেই দেখা যাবে বেশিরভাগই পরিচালকদের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবি, এবং তারপর তাঁরা পরের ছবি হয় করতে পারছেন না, নয়ত অনেক বছর পরে করছেন – এটা অনেককিছু প্রমাণ করে যা খুব আশাব্যঞ্জক নয়। আখেরে গতানুগতিক সোজাসাপ্টা গল্প বলাতেই সবাইকে ফিরতে হচ্ছে। একটি সোজা ফর্মুলা হল কলকাতা থেকে দূরে গ্রামে চলে যাওয়া (গিল্ডের হাত থেকে বাঁচা যায়; দশজনের বদলে সত্তরজনের ক্রু নিতে হয়না; শুটিং-এর দিন বাড়ানো যায়); তারপর সেই গ্রামে গোটা দুয়েক বালককে নিয়ে ছবি করা (বালিকা নিয়ে ছবি করতে গেলেই বিশগুণ কঠিন হয়ে যেত!)। এই ফর্মুলায় বেশ কিছু ভাল ছবি আমরা পেয়েছি। কিন্তু যখন তা পুনরাবৃত্ত হচ্ছে তখন ঙ্কী করা যাচ্ছে না তা বড্ড স্পষ্ট হয়ে যায়; এবং বোঝা যায় সংবেদনশীল ছবিও হয়ে পড়ছে ফর্মুলা-নির্ভর।
যদি আখেরে গতানুগতিক ঢং-এ ছাঁচে ফেলা গল্পই বলতে হয়, তাহলে সেই কাজটিকেই যত্ন করে করা নয় কেন? সেই কাজটাই – জনপ্রিয় বক্স-অফিস ফ্রেন্ডলি ছবি বানানোকে – যাতে যত্ন করে করা যায় তার জন্য একটি প্রতিকূল কাজের আবহ, ওয়ার্ক-কালচারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা নয় কেন? ইন্ডাস্ট্রিকেই বাঁচানোর জন্য ইন্ডাস্ট্রির নিয়ামকদের সঙ্গে ঝগড়া করা নয় কেন? ইতিহাস ঘেটে দেখুন, যখনই আমাদের ‘আর্ট সিনেমা’ উৎকর্ষে পৌঁছেছিল, তখন আমাদের মূলধারার ছবিও লাভজনক হত, কারণ সেই ছবিও উৎকর্ষে পৌঁছেছিল। অর্থ বিনিয়োগ হলে তার লাভসমেত ফেরত আসাটা নিশ্চিন্ত ছিল বলেই প্রযোজকরা এমন ছবিতে বিনিয়োগ করতে পারতেন যার ব্যবসার তেমন গ্যারান্টি নেই, কিন্তু ভিন্নধর্মী শৈল্পিক উৎকর্ষের সম্ভাবনা আছে, এবং এদিক ওদিক পুরষ্কৃত হলে সেই ছবি দেখার উৎসাহ বাড়ার সম্ভাবনা আছে। বাংলা ছবির জনপ্রিয় মূলধারাকেই সচেতনভাবে পূনরুজ্জীবিত করাটা নতুন ফিল্মমেকারদের কাজ হবে না কেন, যেহেতু আখেরে তাতে বিকল্প ছবির প্রযোজনার সম্ভাবনা বাড়াবে? এবং সত্যি বলতে কী ইন্ডাস্ট্রির যে অবস্থা, আর্ট সিনেমা নয়, সফল জনপ্রিয় ছবি করাই এখন নতুন ফিল্মমেকারদের প্রায়োরিটি হওয়া উচিৎ। জনপ্রিয় ছবিতেই নতুন ভাবনার জোয়ার আনা ছাড়া ইন্ডাস্ট্রিকে বাঁচানোর আমাদের আর উপায় আছে কি? সেই ভাবনা-চিন্তায় সমসাময়িক আন্তর্জাতিক পপুলার ‘ফিল্ম সেন্স’এর প্রয়োগ থাকবে না কেন? এবং তাকে ‘চলচ্চিত্রচর্চা’, অর্থাৎ চলচ্চিত্র-সংক্রান্ত বৌদ্ধিক ডিসকোর্সের অন্তর্গত করে তোলা হবেনা কেন? অর্থাৎ, মূলধারার ছবি বানানো ভাবনা-চিন্তা ব্যতিরেকে হবে কেন?
আমি কিছু তরুণ ফিল্মমেকারদের চিনি, যারা পরীক্ষামূলক জনেরিক ছবি (যেমন হরর) করতে ইচ্ছুক। কিন্তু তারা নিশ্চিত নন যে তাদের কাজ বঙ্গবাজারে উৎসাহ উদ্রেক করবে; তাই তাদের ফেস্টিভাল মার্কেটের জন্য কাজ করতে হচ্ছে। ফেস্টিভালে গিয়ে তারা দেখছেন যে সেখানকার কর্তাব্যক্তিরা ভিন্ন কিছু মাত্রা চান, যেসব মাত্রা অধিরেখ করা হয়ত তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। অতএব তারা ত্রিশঙ্কুতে ঝুলে থাকেন। এর মূল কারণ বাংলা মূলধারায় জঁর নিয়ে আলোচনা হয়না, হয়না বৌদ্ধিক মহলেও, এমনকি দর্শকমহলও জঁর নিয়ে ওয়াকিবহাল নন। মানে, তাঁরা একটা হরর ছবি ভয়ের হল কি হল না তা বোঝেন; কিন্তু সেই ধরণের ছবির ইতিহাস নিয়ে অবগত নন। বিস্তারিত করার সুযোগ নেই, এই ‘ইতিহাসচেতনা’ ছাড়া এই যুগে জঁরধর্মী ছবি করা যাবে না।
কেন বাংলা ছবিতে জঁরের ধারণা অত্যন্ত দুর্বল? কারণ শুধুমাত্র অবস্থাপন্ন প্রৌঢ়দের কালচারাল ডিমান্ড সাপ্লাইয়ের ব্যবসায় মত্ত থাকলে জঁর নিয়ে না ভাবলেও চলে। যে রাজ্যে যুবসম্প্রদায়ের কর্মসংস্থান নেই তাকে চলচ্চিত্রের প্রধান কনজিউমার করার কীই বা প্রয়োজন এই ইন্ডাস্ট্রির? তাই প্রতিষ্ঠিত প্রজন্মের কালচারপনাই আমাদের ছবির প্রধান পুঁজি। এমনকি মিস্ট্রি ছবিতে মিস্ট্রিটি ঘটার আগে এক ঘন্টা ধরে প্রৌঢ়দের কালচারের প্রদর্শনী চলেছে – এমন বাংলা ছবিও আমি দেখেছি।
অধুনা বাঙালির জঁর-চেতনার দুর্বলতা নিয়ে খানিক বলি। এর সবচাইতে বিরক্তি-উদ্রেককারী সিম্পটম হল বাংলা সিনেমার একের পর এক ফেলুদা আর ব্যোমকেশ করে যাওয়ায়। আপনি বলতে পারেন, পাশ্চাত্যেও তো সেই শতখানেক বছর হল শার্লক হোমস হয়ে আসছে। না, তুলনীয় নয়, তারা হোমস নিয়ে প্রচূর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে, আমরা একটা-দুটো দৃশ্যে ফেলুদাকে মোবাইল ধরিয়ে কসমেটিক মেক-আপ দিয়েছি, আখেরে ব্যাপারটা বেখাপ্পা ভাবে সেই সত্যজিৎ যা লিখেছেন তাই চলছে, তবে সত্যজিতের স্মার্টনেস ছাড়া।
প্রথমত, গত একশো-দেড়শো বছর ধরে গোয়েন্দা সাহিত্যে নানান ধরনের বিবর্তন হয়ে আসছে, তার মধ্যে স্থিতিশীলতা পেয়েছিল ব্রিটিশ গোল্ডেন এজ-এর প্রাইভেট ডিটেকটিভের আধারে লেখা গল্প, যার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হল আর্থার কোনান ডয়েল এবং আগাথা ক্রিস্টির উপন্যাস। কিন্তু আমেরিকাতেই বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে আরম্ভ করে বিশ্বযুদ্ধের পরে যে একদম নতুন মডেলের গোয়েন্দা গল্প আসে, যার অন্যতম লেখক হল ড্যাশিয়েল হ্যামেট এবং রেমন্ড শ্যান্ডলার, এবং যে গোয়েন্দা গল্প থেকে ‘ফিল্ম নোয়া’ (film noir) নামক আস্ত একটি চলচ্চিত্রীয় ধারা শুরু হয় চল্লিশের দশক থেকে, তার প্রভাবই আমাদের জনপ্রিয় গোয়েন্দা সাহিত্যে পড়েনি, পরের স্ক্যান্ডিনেভিয়ান উপন্যাসের ধারার কথা তো ছেড়ে দিলাম। এই প্রতিটি ধারায় শুধুমাত্র নতুন গোয়েন্দার মডেল যে আমরা পাচ্ছি তাই নয়, পালটে যাচ্ছে আখ্যানের ধরন, পালটে যাচ্ছে গল্পগুলির নৈতিক বিশ্ব এবং উদ্রেক করছে বিবিধ তদন্তের জটিলতা। সেরকম বিবর্তন আমাদের জনপ্রিয় গোয়েন্দা-কল্পনায় নেই, যারা লিখেছেন সেরকম গল্প (বা ‘ছোটলোক’-এর মত সিরিজের চিত্রনাট্য) আমাদের জনপ্রিয় কল্পনায় বড় প্রভাব ফেলতে পারেনি। অতএব মিতিনমাসি ইত্যাদিতে সেই একই মডেল ঘুরে ফিরে আবর্তিত হয়, সেখানে এই জঁরের ইতিহাস নিয়ে কোনও সচেতনতা নেই। এখানে আমি বইয়ের পাতায় বা পর্দায় ব্যতিক্রমের কথা একদম বলছি না, আমি বলছি সাধারণ ধারণার কথা। অথচ, এই যে বিশ্বসাহিত্যে এখন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটরের কল্পনা অস্তমিত হয়েছে (এবং বাংলা সিনেমায় সেই অস্তমিত সুর্যই একমাত্র আলো), তার বদলে কেন্দ্রীয় স্থান নিয়েছে police procedural, সেরকম গল্পের আদিতম উদাহরণ হল বাংলাতেই লেখা ‘দারোগার দপ্তর’।
সিনেমা থেকে ছোট্ট বিরতি নিয়ে ব্যক্তিগত কথা বলি। আমি গত কয়েক বছর ধরে গল্প-উপন্যাস লিখছি। আমি মূলত লিখি কল্পবিজ্ঞান গোত্রের গল্প। দুটি উপন্যাস বেরিয়েছে, একটি গল্প-সংকলন। সায়েন্স-ফিকশন হলেও, আমার গল্পের কাঠামো মোটামুটি রহস্য-গল্প বা থ্রিলারের আকারে লেখা হয়। তাতে অতএব জনপ্রিয় উপাদান থাকে, এমনকি গল্পগুলিতে অ্যাকশন ও ভায়োলেন্সও জায়গা পেয়েছে। এর মধ্যেই আমি বৌদ্ধিকতার কিছু উপাদান রেখে দেওয়ার চেষ্টা করি ওই থ্রিলার-মিস্ট্রি কাঠামোগুলো খুব বেশি নষ্ট না করে। উপন্যাস দুটি ভাল রিভিউ পেয়েছে। কিন্তু আমার হতাশা ভিন্ন জায়গায়। আমার গল্পগুলি সচেতনভাবে ৩৫-এর নিচে বয়সী পাঠকদের উদ্দেশ্য করে লেখা; মূলত ছাত্রযুবদের। কিন্তু তাদের রেসপন্স আমি প্রায় কিছুই পাইনি। যেহেতু আমি আদতে সিনেমার ছাত্র, লেখাগুলিতে অনেক সিনেমাটিক রেফারেন্স থাকে যা গল্পগুলি বোঝার জন্য জরুরি নয়, কিন্তু ধরতে পারলে একধরণের উপভোগ্যতা বাড়ে। যারা ভাল রিভিউ দিয়েছেন, তারা এগুলি খুব একটা ধরতে পারবেন বলে মনে হয়না; বা পারলেও, তা রসাস্বাদনের প্রক্রিয়ায় কীভাবে অন্তর্গত করা তা তার জানা নাও থাকতে পারে যেহেতু তারা হয়ত সিনেমা নিয়ে কম উৎসাহী। এরকম ইন্টারটেক্সচুয়াল অথবা রেফারেন্স-ধর্মী আখ্যান ক্যাম্পাসের ছেলেমেয়েদের কাছে পরিচিত, তারা সেরকম ছবি-সিরিজ দেখে থাকেন। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতার সারমর্ম এরকম – যে তরুণ-তরুণী এই ধরণের গল্প পড়েন, তিনি বাংলা পড়েন না; যে যুবক-যুবতী শুধু বাংলা ভাষাতেই স্বচ্ছন্দ, তিনি এইরকম ফিকশন পড়েন না; অনেকে ফিকশনই পড়েন না। আমার বাকি জীবন এরকম গল্প লিখে চলার ইচ্ছে, আরো বিভিন্ন জঁরে লেখার ইচ্ছে, কিন্তু সেরকম অনুপ্রেরণা পাই না, কারণ আমি বুঝে গেছি যে এই ধরণের গল্পের ছবি দেখার অভ্যেস যাদের আছে, তারা হয় ফিকশন পড়েনা, নয় বাংলাতে এই সাহিত্য পড়ে না।
তাই ক্রিটিকাল সাফল্য পেলেও আমি আমার লেখাগুলিকে ব্যর্থ বলে মনে করছি। এর কারণ আমাদের উচ্চ-সাংস্কৃতিক ধারণা যে জঁর-সাহিত্য ‘কুলীন’ নয়। এই ধারণাগুলি মূলত নব্বইয়ের দশক থেকে তৈরি হয়েছে। সত্যজিৎ রায়ের তিরোধান এখানে বড় ল্যান্ডমার্ক ইভেন্ট, কারণ যদ্দিন তিনি ছিলেন, জঁর-কল্পনার হাল্কা হলেও, কিশোরতোষ সাহিত্যে হলেও, চল ছিল। কিন্তু ওঁর মৃত্যুর পরই যেন আর এইসব ‘বালখিল্য’ চর্চার প্রয়োজন নেই স্থিরীকৃত হয়, কারণ এইসব সাহিত্যে ‘সিরিয়াস’ কিছু হয়না, এমন বেসিকালি অনাধুনিক ধারণায় প্রত্যয়ী হয় বঙ্গ-কালচার। ইদানিং জঁর সাহিত্যের পূণরুত্থান হচ্ছে, কিন্তু ব্যতিক্রম বাদ দিলে তার যে অগভীরতা, তা প্রমাণ করে যে গত তিন, সাড়ে তিন দশকে এই কল্পনায় একটা বড় ভ্যাকুয়াম আছে। যারা এ ধরণের গল্প লিখেছেন, তারাও লিখেছেন চুপিচুপি, বিশেষ কিছু আশা না করে।
সিনেমায় ফিরি। বাংলাভাষায় বৌদ্ধিক চর্চায় একদম ব্রাত্য (কার্যত পারিয়া) অ্যাকশন ছবির কথা ধরি। পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসের কথা ধরুন, সেই অগ্নিযুগে কিছু তরুণ ভায়োলেন্সকে পন্থা করে নিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের। চল্লিশের দশকের বাংলা যুদ্ধ-মন্বন্তর-কুইটইন্ডিয়া-দাঙ্গা ইত্যাদি দিয়ে উত্তাল, এই সময়েই তেভাগা আন্দোলনের হাত ধরে বামপন্থী রাজনীতির উত্থান, কিছুদিন আগে নেতাজি অন্তরালে চলে গেছেন, সেখান থেকে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এইবার পঞ্চাশের একটু স্থিতির পরই ষাটের দশক শেষ হচ্ছে নকশাল আন্দোলন এবং ওপারে মুক্তিযুদ্ধ দিয়ে। সত্তর দশক তো রাজনৈতিক হিংসা এবং রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস দিয়ে আকীর্ণ। এর মধ্যে পঞ্চাশ দশকের জাতিগঠনের আশাবাদ ও সামাজিক স্থিতিই উত্তম-সুচিত্রা যুগের রোমান্টিক মেলোড্রামার ধরনটাকে আকার দিলো। কিন্তু তা বাদ রাখলে বাঙালি কি সমাজে এবং আখ্যানে ভায়োলেন্স নিয়ে একটু কপট নয়? যেখানে ইতিহাস ভায়োলেন্সে আকীর্ণ ছিল গত শতকের অনেকটাই? আমি ‘উচ্চ’-সাহিত্যের কথা বলছি না, বলছি পপুলার ন্যারেটিভের কথা। এইবার ভায়োলেন্স (বা অ্যাকশন, দুটো এক জিনিস নয় ঠিক, সম্পৃক্ত) আমাদের ছবিতে কখন এলো? ৮০-র দশকে; কিন্তু তাও তরলীকৃত ডেরিভেটিভ ফর্মে। কিন্তু যে ছবির থেকে তা derive করা হল – ভেবে দেখুন – অমিতাভ বচ্চন কেন্দ্রিক সেই ‘অ্যাংরি ইয়ং ম্যান’-এর ঘরানা, তা কি পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে সবার আগে উদয় হওয়ার কথা ছিল না? ইতিহাসে যে বদলগুলো হয় তা তো একরকম পপুলার মনস্কামণার চরিত্র ও প্লটও তৈরি করে। সেটা বাংলায় হল না কেন? আমি তো প্রমাণ দিলাম, আমরা খুব ‘শান্ত’ মানুষ ছিলাম না। এই সংঘাত এড়ানো নরম চরিত্রধর্মিতাটাই মধ্যবিত্তের কপট ‘কালচারাল কনস্ট্রাক্ট’।
বরং ষাটের শেষ আর সত্তর দশকের ‘সিরিয়াস’ সিনেমার কথা বলি। সত্যজিতের ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’, সিদ্ধার্থ একজায়গায় গণধোলাই দেয়, ক্লাইম্যাক্সে ভাঙচুর করে (“আমরা কি জানোয়ার?”), মৃণাল সেনের ‘ইন্টারভিউ’, আবার ক্লাইম্যাক্সে ভাঙচুর। তপন সিনহার-র ‘এখনই’, পার্থপ্রতিম চৌধুরীর ‘যদুবংশ’, ঋত্বিকের শেষ ছবিতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে যুবকেরা – মূলত চল্লিশের দশকে যাদের যৌবন অতিবাহিত হয়েছে, সেইসব প্রৌঢ়রা যখন সেই সময়ের যুবকদের নিয়ে ছবি করছেন, সবাই বলছেন যে ভায়োলেন্স এই সময়ের যুবকদের প্রধান বৈশিষ্ট্য – কেন ‘কমার্শিয়াল’ ছবি সেই আর্কেটাইপ তৈরি করতে পারল না? কেন সেটা ‘হিন্দিবাজারি অতএব আমাদের নয়’ এরকমভাবে অবহেলিত হল বা পরে সেইভাবেই অনুকরণ করা হল? যখন আশির দশকের দ্বিতীয়ার্ধে ভিক্টর ব্যানার্জি, চিরঞ্জিত, প্রসেনজিৎরা মারপিট করতে শুরু করবেন – তখন তাতে আর ‘দীওয়ার’, ‘জঞ্জির’-এর নায়কের poignance রইলো না। বরং হয়ে উঠলো মিঠুন চক্রবর্তীর মত খানিক ডেরিভেটিভ লুম্পেন নায়কের প্রতিফলিত ছায়া। অর্থাৎ, তাতে আর আমাদের ইতিহাসের substance রইল না। এবং সেই ‘ডেরিভেটিভ’ ভাব জিৎ এবং দেব অবধি চলেছে, চরিত্রগুলি এবং তাদের গল্প মৌলিক না, ‘অন্যদের মত’। অধুনা যুবকরা যে massy ছবির মত অ্যাকশন বাংলা পপুলারে দেখতে চান, তাও হবে একইরকম ডেরিভেটিভ ও শেকড়হীন।
মৌলিক জঁর-ছবি ছাড়া যুবসম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছোনো যাবে না; এবং তা করতে গিয়ে এমন জঁরের ছবি করতে হবে যা, এক, বাংলায় খুব বেশি হয়নি, আর দুই, যে ছবি সেই জঁরের ইতিহাস সম্পর্কে সচেতন। কারণ, যুবক-যুবতীরা সেইরকম ছবি অন্য ভাষায় দেখতে অভ্যস্ত। আমি আগের কিস্তিতে অ্যাকশন ফিল্ম হিসেবে ‘পারিয়া’-র আলোচনা করলাম। সেই ছবির নায়ক বিক্রম চ্যাটার্জি গত বছরে ‘শহরের উষ্ণতম দিনে’ আর ‘শেষ পাতা’ করেছেন, কিছুদিন আগে ‘সূর্য’ – চারটে ছবি, চাররকম নায়ক চরিত্রে উজ্জ্বল, তবুও তিনি নাকি এখনও স্ট্রাগলিং! এতেই প্রমাণিত হয় যে আমাদের আর তরুণ নায়কের তেমন প্রয়োজন নেই, প্রৌঢ় দিয়েই কাজ চলবে।
যে জাতির শ্রেণি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে যুবসম্প্রদায়ের কাছে সিনেমা কল্পনার খোরাক দিতে পারে না, সেই সিনেমা সুস্থ কী করে থাকে? যে জাতি যুগধর্মে জারিত প্রেমের গল্প, প্রতিশোধের গল্প, দ্রোহের গল্প, মনস্কামনার গল্প শুনতে-দেখতে-চাইতে ভুলে গেছে, নতুন যুগের নায়ক বা নায়িকার কল্পনার প্রয়োজন নেই – সেই জাতি সুস্থ আছে কি?
(চলবে)
-
বাংলা সিনেমার সংকট নিয়ে: তৃতীয় পর্ব

বাংলা অ্যাকশন ছবি: প্রকট কন্ঠ না সুপ্ত হৃদয়?
জনপ্রিয় ছবি আলোচনা করারও ধরন আছে যা জনপ্রিয় ছবির ধরণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল; এবং সেই প্রক্রিয়ায় ক্রিটিকালও থাকা যায়। এই বছরের শুরুর দিকেই একটি কমার্শিয়াল ছবি সাড়া জাগিয়েছিল, সফল হয়েছিল কিনা জানি না। আজকাল সফল হতে গেলে গ্রহ-রত্ন লাগে, কারণ বাঙালি দর্শক যে ছবিকে ‘বাঃ’ বলেন, সেই ছবি দেখতে যান না সব সময়ে। তারা ফেসবুকে ছবির লিংক চান, হয়তো বিনিপয়সায় ছবি দেখতে চাওয়া এমন জাতি আর দ্বিতীয়টি নেই। এই ছবিটির নাম ‘পারিয়া’। ‘পারিয়া’-র হৃদয়টি একদম ঠিকঠাক জায়গায় আছে; ছবিটি পথকুকুরদের প্রতি অ্যাবিউজের বিরুদ্ধে একটি জেহাদ। এবং নির্মাতাদের সামাজিক ক্রোধের মাধ্যম হিসেবে ছবিতে সাংঘাতিক ভায়োলেন্স আছে। আর্ট সিনেমা rage বা ক্রোধের অভিব্যক্তির জায়গা দেয় না (অর্থাৎ আমরা এখন আর্ট সিনেমা বলতে যা বুঝি; ‘সুবর্ণরেখা’, ‘জন অরণ্য’ বা ‘সদ্গতি’-র যুগের আর্ট সিনেমার কথা বলছি না)। তাই দায়িত্ববান ছবিকে যে আর্ট সিনেমাই হতে হবে, এই ছবির নির্মাতারা তা মানলেন না সঠিকভাবেই।
কিন্তু হৃদয় শিল্পীর থাকলেই হয়না। ছবিরও থাকতে হয়। এই ছবিতে বিক্রম চ্যাটার্জি তাঁর শ্রম এবং অধ্যবসায়ের দৃশ্যমান প্রমাণ দিয়ে চমকে দিলেন। ছবিতে চমকে দিলেন খলনায়কের ভূমিকায় সৌম্য মুখোপাধ্যায়ও। কিন্তু আমার চোখে বাধ সাধলো নির্মাণের একধরনের অধৈর্যপনা।
পরিচালক ছবির প্রধান আবেগের জায়গাটি, নায়কের সঙ্গে একটি কুকুরছানার সম্পর্ককে তৈরি করলেন না। একজায়গায় তিনি বললেন যে তিনি প্যানপ্যানে বা গ্যাদগ্যাদে ছবি করতে চাননি। তাহলে ছবির ড্রাইভিং ফোর্স কী? আমি নিজে সারমেয়প্রেমী, সেই জন্যই ছবিটি দেখতে গেছিলাম। কিন্তু যাদের জীবনে সেই প্রেম আছে, তারা সেই প্রেমেরই ইমেজ দেখতে চায় পর্দায়, না হলে সারমেয়-প্রেমটা স্রেফ ইনফরমেশন থেকে যায়। তাদের কাছে মানুষের শ্রেষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে স্নেহের-বাৎসল্যের ওই মুহূর্তগুলি জরুরি। সেই ইমেজটা থেকে, আবেগের আনন্দ থেকে আমাদের বঞ্চিত করলে কীসের ভিত্তিতে cathartic violence দেখতে চাইবো?
মূলধারার ছবিতে ভায়োলেন্স কীভাবে আসে? হয় ভায়োলেন্স চরিত্রেরই বা জঁরের স্থাপত্যের বিষয় হয়, যেমন গ্যাংস্টার জঁরের ছবিতে বা ‘অ্যাংরি ইয়াং ম্যান’-এর চরিত্রে আপনি ভায়োলেন্স আশা করেই যাবেন। নয়তো ছবিতে এমন কোনও সমাধানহীন কনফ্লিক্ট থাকে যে তার resolution হিসেবে cathartic violence-এর প্রয়োজন হয়। ‘পারিয়া’-তে এর কোনোটাই হয় না। নায়ক কেন এরকম সোশিওপ্যাথ একাকী? কেন সেই কুকুরছানাটাতেই তার অবশিষ্ট বাৎসল্য ধাবিত হয়? আমাদের কোনও হদিশ নেই। কেন একইরকম সাইকোটিক খলনায়ক? কেন বিশেষ করে কুকুরদের প্রতি তার রাগ? কোনও হদিশ নেই। তাই এই দুই চরিত্র ঠিক নাটকের ভিত্তিতে যুযুধান হল না, হল স্রেফ তথ্যের ভিত্তিতে। অথচ কিছু ক্লাসিক ছবির চরিত্রনির্ভর কনফ্লিক্টের দারুণ সম্ভাবনা ছিল এই ছবিতে। চরিত্রনির্ভর কনফ্লিক্ট – যেমন ব্যাটম্যান আর জোকার – যার অন্যতম সেরা টেমপ্লেট দিয়ে গেছিল জন ফোর্ডের ‘দ্য সার্চার্স’-এর ইথান এডওয়ার্ড এবং স্কার নামক নায়ক-খলনায়কের জুটি। নাটকের এক সময়ে এই দুটি চরিত্রকে mirror image, যমজ ভাই ইত্যাদি মনে হতে পারে, মনে হতে পারে তারা একই আধুলির এ-পিঠ ও-পিঠ। এই সম্ভাবনা ‘পারিয়া’-তে ছিল। কিন্তু এই দুটি চরিত্রকে প্রতিষ্ঠা করার বদলে ছবিটির সিংহভাগ পরিচালকের অ্যাক্টিভিস্ট অভিজ্ঞতার সামাজিক ‘তথ্য’-এর তালিকা হয়ে গেল। কিন্তু আমরা তো এই চরিত্র দুটির গল্প চাইছিলাম! কারণ চরিত্র দুটি ইনট্রিগিং, অভিনেতারা তাদের সর্বস্ব দিয়ে চেষ্টা করছেন, তাই চরিত্র দুটিই ছবির সবচাইতে জোরের জায়গা, চরিত্র দুটি প্রায় মিথিকাল হওয়ার সম্ভাবনা রাখে – কিন্তু চিত্রনাট্য তাদের যথেষ্ট ঘনত্ব দিলো না।
তাহলে কি স্রেফ অ্যাকশন দৃশ্য নির্মাণের অজুহাত? বাংলা ছবিও পারে – এটা বোঝাতে? না, তা নয়। বললাম তো ছবিটি হৃদয়বান ছবি, এবং আন্তরিক rage-এর ছবি। কিন্তু তাতেও মাত্রার অভাব রয়ে গেল। প্রথমত, পর্দায় মৃত্যুকে মুড়িমুড়কির দরে দেখালে মৃত্যুগুলি মূল্যহীন হয়ে যায়, অ্যাকশন তার নাট্যধর্মিতা হারায়, কোনও গ্রাফ তৈরি হয় না। এই ছবির নায়ক সবাইকেই খুন করে ফেলে (যেজন্য তাকে সাইকোটিক সিরিয়াল কিলার মনে হয়, ভিজিলান্টি হিরোর বদলে) এবং তাই খলনায়কের হত্যাও বিশেষ নাটকীয় মাত্রা পায়না; আবার তথ্য হয়ে যায় মাত্র, অর্থাৎ ছবি জানায় যে সে গেছে। দ্বিতীয়ত, অ্যাকশন দৃশ্যে যদি আঘাতের মোমেন্টেই কাট ঘটে এবং ক্যামেরার সেট-আপ পালটে যায়, তাহলে অ্যাকশনের শৈলীগত উত্তেজনাটাই তৈরি হয় না, মনে হয় কোরিওগ্রাফি সম্পাদনার সুযোগ নিয়ে ফাঁকি মারলো। আর প্রতিটা ছবিরই নিজস্ব যুক্তিপট থাকে। একটি দৃশ্যে নায়কের ঘাড়ের পেশিতে একটি চপার এমনভাবে আটকে যায় যে এক ঝটকায় তা তোলা যায় না। কিন্তু এমন মারাত্মক আঘাতের পরেও যখন দেখা যায় নায়কের হাত সক্ষম, তখন আর সেই ইমেজটি বিশ্বাসযোগ্য থাকে না, নায়ক তো উলভেরিন নয় যে আঘাতের তৎক্ষণাৎ নিরাময় হয়ে যাবে!
সেই দৃশ্যের কিছুক্ষণ পরেই একটি দৃশ্যে অত্যন্ত সুন্দর বিল্ড-আপ আছে, একটি গলিতে প্রায় বিশখানেক গুন্ডা নায়ককে দুই দিক থেকে ঘিরে ফেলে। কিন্তু তারপরেই গোলমাল হয়ে যায়! সব গুন্ডা বান্ডিল হয়ে পড়ে নায়কের উপর; অর্থাৎ নায়কের উপর প্রায় দুতিন স্তরের মানুষের পরত। একদম উপরের স্তরের গুন্ডারা যে কাকে মারছে বোঝা যায় না। নায়কের হাতে ছিল একটা ইঁট। দেখা যায় সব গুন্ডা ছিটকে ছিটকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল। এইবার আমার প্রশ্ন হল – এক নম্বর, দুই নম্বর স্তর পেরিয়ে তিন নম্বর স্তরের গুন্ডাদের নায়ক আঘাত করল কী করে? সে তো প্রভাস বা আল্লু অর্জুনদের মত এমন হাল্ক নয় যে স্রেফ গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল আর সবাই ছিটকে গেল? তাকে তো এভাবে তৈরিই করা হয়নি! গোটা ছবির শৈলী তো বাস্তববাদী।
যাই হোক না কেন – অ্যাকশন ছবি দেখতে যাওয়ার সাধটাই তৃপ্ত হল না। বুঝলাম নির্মাতাদের কাছে আকর্ষণীয় কিছু সেট-আপ ছিল, কিন্তু তা সচল হল না, গতি পেল না। শেষে জন উইককে দেওয়া ট্রিবিউট তাই অগভীর লাগলো। এবং আবার বুঝলাম যে জন উইককে সবাই কী প্রচন্ড ভুল বোঝে!
কিনু রিভস উচ্চমানের অভিনেতা নন, কিন্তু জন উইকের ভূমিকায় তিনি একদম ‘পর্যাপ্ত’, এবং পৃথিবীর শেষ গ্রেট মুভিস্টারের একজন হলেন তিনি। তাঁর একধরনের ক্যারিশ্মা এবং সম্ভ্রম আছে যা খুব কম অ্যাকশন-স্টারেরই থাকে। জন উইক যখন একের পর এক ব্রুটাল অ্যাকশন করেন তখনও কী এক ম্যাজিকে তিনি জ্ঞাপন করেন যে তিনি একজন শোকস্তব্ধ প্রেমিক, তিনি তার শোক নিয়েই চুপচাপ ছিলেন, এবং সেই শোকযাপনের পন্থা ছিল মৃতা স্ত্রীর কুকুরছানাটির খেয়াল রাখা। সেই কুকুরছানাটিকে হত্যা করায় জন উইকের মধ্যে বুগিম্যান জেগে ওঠে। এইবার যা হয়, এই মিথিকাল জগতের নিয়মে তার ওপর দেওয়া হয় বাউন্টি, এবং প্রায় কর্পোরেট-সম এই মিথিকাল সিস্টেমের বিচিত্র নিয়ম-নীতিতে বাধা পড়ে যায় জন উইক। একের পর এক খুনি তাকে মারতে আসে; এই তরঙ্গের মত অ্যাসাসিনের ঢল তার mourning-কে ব্যাহত করছে। তিনি এদের বলতে চাইছেন যে আমাকে রেহাই দাও, বিরক্ত কোরো না, আমার প্রেমের শোককে ডিস্টার্ব কোরো না, কারণ তোমাদের যে ব্যাঘাতের পন্থা তা কাজে দেবে না, কারণ আমি বুগিম্যান বাবা ইয়াগা, আমাকে পরাস্ত করা যায় না। কিন্তু খুনির তরঙ্গ আসতেই থাকে, জন উইক ক্লান্ত হয়েও জয়ী হতে থাকেন। এই ডিগনিটি ও ক্লান্তি নেওয়া হচ্ছে ওয়েস্টার্ন জঁর থেকে, সামুরাই ও নাইটের ইতিহাস থেকে। যেজন্য তাঁর সমকক্ষ প্রতিপক্ষের সামনেই যেন তিনি সম্ভ্রমে সমধর্মী। আর বাকিরা সব ফালতু। ক্লান্ত উইক তাই একের পর এক ফালতু গুন্ডাকে নিষ্ক্রিয় করেন হাতের কাছে যা আছে তাই দিয়ে, আর সমকক্ষের সামনে থাকেন সম্ভ্রমী। এই দিয়েই তৈরি হয় বিচিত্র হিউমারের এবং সারভাইভালের বুদ্ধিমত্তা।
জন উইকের নির্মাতাদের অ্যাকশন ছবির প্রতি এতই নিবিষ্ট প্রেম যে সবচাইতে কম দৃশ্যেও তারা অ্যাকশন কোরিওগ্রাফির কোনও এক রেফারেন্স বা দৃষ্টান্তকে স্মরণ করেন। ক্রাফটের কোনও একটি উপাদান – হয় রঙ, নয় ক্যামেরা বা কুশলীদের মুভমেন্ট, নয় আলো, নয় এডিটিং নিয়ে কিছু না কিছু নিরীক্ষা তাঁরা করেই চলেন, এবং কোনও কোরিওগ্রাফিই ঝাপসা-অস্পষ্ট থাকেনা, চোখ ঠকানো হয়না। অর্থাৎ, স্রেফ ফাইনাল আউটপুট নয়, ফিল্মমেকিং প্রক্রিয়াটির প্রতিই তাঁদের প্রেম ইমেজে ইমেজে বিরাজমান থাকে। তাই হয় নির্মাতাদের সিনেফিলিয়ায়, নয়ত কিনুর পারফর্মেন্সে প্রেম বিষয় বা শৈলীগত ভাবে সদাজাগ্রত থাকে। অ্যাকশন ছবি করতে গেলেই টক্সিক হতে হবে এমনটা নয়। কিনু যেমন সবচাইতে ভায়োলেন্ট দৃশ্যেও স্ত্রীর শোকের অবয়ব হয়ে থাকেন, আমাদের massy ছবির টক্সিক নায়কদের প্রেমের দৃশ্যেও সম্ভাব্য রেপিস্ট আর মার্ডারার মনে হয় – এই হল তফাত।
‘পারিয়া’ এই massy ছবির বিপ্রতীপ একটি উদাহরণ হওয়ার সুযোগটা ফসকালো এই আবেগের জায়গাগুলোর প্রতি অধৈর্য হয়েই। কেন অধৈর্য হল? কারণ নির্মাতাদের অ্যাক্টিভিস্ট সত্তা অগ্রাধিকার পেয়ে বসে আছে। চিত্রনাট্য সামাজিক অন্যায়ের খবর দিতে এতটাই সময় ব্যয় করল যে চরিত্র দুটিকে গভীরতা দিলো না, এবং অ্যাকশন দৃশ্যগুলোর প্রতিও যত্নবান হল না। অর্থাৎ, এই ছবিকে ‘অ্যাক্টিভিস্ট’ ছবি না হলেও চলতো। কিন্তু সেটা হল, তারপর শেষে হঠাৎ মেজাজ পাল্টে নায়ককে জন উইক করে দিলো। কিন্তু এহেন মিথিকাল করতে হত আগে, ছবির শেষে নয়। ছবিটি ‘জীবে প্রেম করে যেই জন’ হয়ে হৃদয় স্পর্শ করল, কিন্তু মিথিকাল গল্প হিসেবে স্মৃতিতে দীর্ঘজীবন পেলো না। যদি কেউ ভাবেন যে আমি ছবিটিকে ‘ক্রিটিসাইজ’ করলাম, তাহলের আগামী দুটো প্যারা পড়বেন, এবং এই প্রবন্ধের শেষ কিস্তিতে ‘পারিয়া’-প্রসঙ্গ আবার আসবে।
গল্পটা মিথিক হতে পারতো। মূলধারার ছবি স্মৃতিতে দীর্ঘজীবন পায় যখন সেই গল্প আধুনিক মিথ তৈরি করতে পারে, আর্কেটাইপাল চরিত্র দিতে পারে। ‘পারিয়া’-তে তার সমস্ত সম্ভাবনা ছিল। আমি দুটি ইমেজ থেকে দুটি চরিত্রের ব্যাকস্টোরি তৈরি করার চেষ্টা করছি। জানি না আমি ‘ভুল দেখেছিলাম’ নাকি – একটি শটে ভিলেন নন্দর চোখ দিয়ে জল বেরোচ্ছিল। আরেকটি ইমেজ, নায়ক লুব্ধক প্রায় নিজেকে strangle করছে। এই দুটি প্রায় নজর এড়ানো ইমেজই আমার কল্পনার সূত্র।
ভিলেন নন্দ যখন বালক ছিল তার লালি নামে একটি ভারি আদরের পোষা কুকুর ছিল, আর ছিল দারিদ্র-দুর্দশায় আক্লিষ্ট অ্যাবিউজিভ বাবা-মা। একদিন নন্দ আর মা-বাবার বিষাক্ত ঝগড়া আর তার জেরে ওর প্রতি অত্যাচার নিতে পারলো না, ঠিক করল যে মা-বাবাকে সে আজ রাতে কোপাবে। তারপর তার কুকুরটাকে নিয়ে পালাবে। সেই অমোঘ রাত্রে যখন মাতাল মা-বাবাকে সে কোপাতে শুরু করেছে তখন লালিটাই গর্জে উঠলো, রুখে দাঁড়ালো, তারপর কামড়ে ধরলো নন্দর চপার ধরা হাত। নন্দ সেই রাতে মা-বাবাকে কুপিয়েছিল; কিন্তু কুপিয়েছিল তার আদরের কুকুরটাকেও। এবং তারপর থেকে কসাই নন্দ খালি কুকুর কোপায় আর কাঁদে, আর নিজেকে বলে যে যেহেতু সে লালিকে মেরেছিল, তাই সে সব কুকুরকে কোপাতে পারে। নন্দ তাই অপেক্ষা করে যে একদিন যোগ্য ব্যক্তি এসে তাকে কোপাবে, আর চক্রাকার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবে। সেই ব্যক্তি হল নায়ক লুব্ধক। বেওয়ারিশ দুই ভাইয়ের একজন। অ্যাবান্ডনড অবস্থায় একটা কুকুর কদিন তাদের আশ্রয় দিয়েছিল। বিশ্বের প্রতিটা বিচ যে তার মাতৃসম, প্রতিটা বিচের গায়ের গন্ধ যে সেই কয়েকদিনের নিরাপত্তাকে মনে করায় এখনও এটা আর কীভাবে লুব্ধক মানুষকে বলবে? তার গল্প রোমাস আর রোমিউলাসের মত। তারা ছেলেবেলায় শুনতো তারা কুত্তার বাচ্চা। এইধরনের শিশুদের যেরকম সমাজে ঠাঁই হয় সেরকম সমাজেই তারা বেড়ে উঠছিল। লুব্ধকের ভাই সমাজবিরোধী হয়ে গেছিল, লুম্পেন ক্রিমিনাল থেকে অপ্রতিরোধ্য গ্যাংস্টার। লুব্ধকের উচিত ছিল তার সমাজের মেয়েদের মানসম্মান বাঁচাতে ভাইকে হত্যা করা। পারেনি, তাই এই আধুনিক কুকুরশাবকের হাতে রোমও তৈরি হল না।
তারপর একদিন লুব্ধক দেখতে পেল নন্দকে, মনে পড়ে গেল তার ভাইয়ের কথা …।
(চলবে)
-
বাংলা সিনেমার সংকট নিয়ে: দ্বিতীয় পর্ব
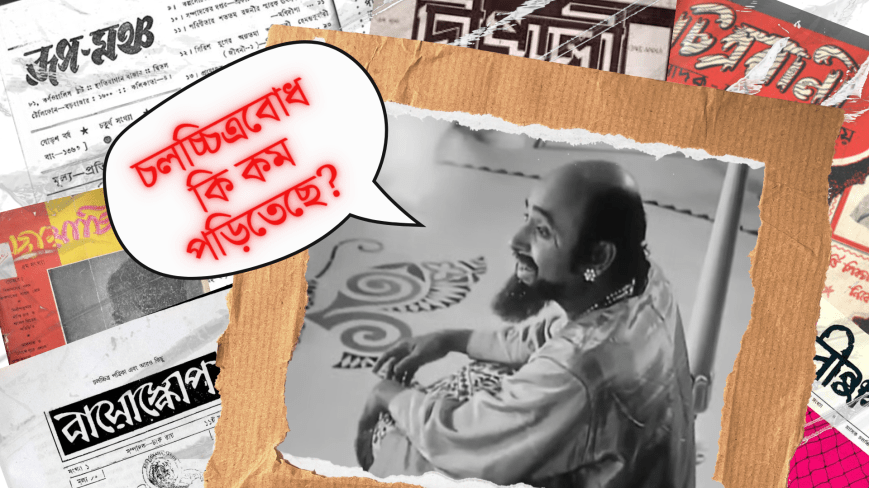
আমাদের চলচ্চিত্রবোধেও সংকট আছে
আমাদের চলচ্চিত্রবোধেরও যে একরকম অবক্ষয় হয়েছে তা স্বীকার করলে ভাল।একটা গৌণ প্রসঙ্গ (কী আইরনি, এক কালে সিনেমা নিয়ে লেখালেখির এটাই ছিল মূল প্রসঙ্গ) – কেন একদা চলচ্চিত্রচর্চা মূলধারা-বিমুখ হয়ে বিকল্প-ধারার দিকে ঝুঁকেছিল? কারণ বাঙালি তখন ‘চলচ্চিত্রের ভাষা’ নিয়ে সচেতন হয়ে উঠেছিল, এবং সেই ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে ইচ্ছুক ছিল, নির্মাতা এবং দর্শক দুজনেই। যে জন্য ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন গোছের স্বল্পদৈর্ঘ্যের কোর্স শুরু হয়েছিল। একটা ধারণা জন্মেছিল যে মূলধারার ছবিতে এই ভাষার চর্চা সম্ভব নয়। অবশ্যই ধারণাটা কিঞ্চিৎ বেঠিক ছিল, কিন্তু ধারণাটা কেন হয়েছিল? কারণ সেই সময়ে মূলধারার ছবি ছিল অত্যন্ত স্টেবল, যাতে নতুন ভাষার প্রায় প্রয়োজন নেই মনে হয়েছিল। মূলধারার সেই স্থিতিশীলতা আশির দশক থেকেই ধীরে ধীরে অপসৃত হতে থাকে, বা সেই ছবির ভাষা হয়ে যায় অপরিশীলিত। এই সময়ে সেই ছবিকে আবার পুনরুজ্জীবিত করার চাইতে নতুন ছবিতে উৎসাহী মেকাররা হয়ে পড়লেন মেনস্ট্রিম-বিমুখ। এই যুগটাও পাল্টালো, নব্বইয়ের দশকে পরের দিক থেকে আর এই ভাষা নিয়ে সচেতনতা দুইধরনের ছবিতেই আর চর্চিত হল না।
চলচ্চিত্র-বোধ কী? চটজলদি সংজ্ঞা – একধরণের শৈল্পিক অভিজ্ঞতার বোধ যা শুধুই সিনেমায় হয়, তার জন্য একরকম বিশেষ ভাষা লাগে চিত্র-শব্দ-মন্তাজ-অনুষঙ্গের। ভেবে দেখুন, এই বোধ কিন্তু ‘আর্ট’ এবং ‘কমার্শিয়াল’ দু’ধরনের ছবিতেই ক্রিয়াশীল থাকতে পারে। এখন এই চলচ্চিত্রের ভাষা-সচেতনতা বা চলচ্চিত্র-বোধ জিনিসটাই ‘এলিয়েন’ হয়ে গেছে। অর্থাৎ, নির্মাতারা সেই ভাষাতেই ছবি করেন আর দর্শকরা সেই ভাষাতেই ছবি বোঝেন, কিন্তু ভাষাটার ব্যাকরণ নিয়ে আর বিশেষ ভাবেন না। লাভের মধ্যে, ঠিক যেভাবে “কেন কী” বা “তিনি বলেছিল” জাতীয় উদ্ভট বাংলার চল চারিদিকে, সেভাবেই “কেন কী’ জাতীয় চলচ্চিত্র-ভাষার চল বাংলা সিনেমায়। এর প্রধান কারণ – বাংলা-ভাষায় চলচ্চিত্র-বোধ চর্চার অভাব ও অসচেতনতা, এবং তার জায়গায় সোশাল-মিডিয়ার কমন-সেন্সিকাল প্র্যাক্টিসের চলে আসা।
আশি ও নব্বইয়ের দশকে যখন আমি একজন কিশোর-যুবক হিসেবে সিনেমায় উৎসাহিত হয়ে উঠছিলাম তখন ভিন্নধারার ছবির ধারণা তৈরি করতে প্রতিষ্ঠিত এবং লিটল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হত প্রচুর লেখা। অর্থাৎ, সিভিল সোসাইটিতে সেই ধরনের আলোচনার প্রতি আগ্রহ ছিল, চর্চাও ছিল। মনে রাখতে হবে, বিশ্বসিনেমা তখন কিন্তু এখনকার মত আমাদের নাগালে ছিল না; কিন্তু তা উৎসাহে ভাটা ফেলেনি। এখন সারা বিশ্বের ছবি আমাদের অনায়াস নাগালে আছে। চলচ্চিত্রবোধ নিয়ে একই কথা কি বলতে পারি? বিশেষ করে সেই সমস্ত লেখালেখির প্রতি উৎসাহের সমকক্ষ কিছু আছে কি?
আমার গত বিশ বছরের লেখালেখির অভিজ্ঞতা কিন্তু তেমন আশাব্যঞ্জক নয়। মুষ্টিমেয় কিছু গোষ্ঠী ব্যতিরেকে আমাদের লেখালেখি, বলাবলি কিছু ‘বিচিত্র কথন’-এ পর্যবসিত হয়ে গেছে। রেস্তোরাঁয় আবহসঙ্গীতের মত, চলছে কিন্তু কেউ শুনছে না, এসব বলা হয়ে থাকলে ভাল ‘কালচার’-এর আবহ তৈরি হয়; আমরা সেই আবহই তৈরি করি মাত্র। উন্নত চলচ্চিত্রবোধ একসময়ে উন্নত শিল্পবোধের অংশ ছিল। উন্নত শিল্পবোধ উন্নতমানের ক্রিটিকাল নাগরিকত্ব নির্মাণের সহায়ক ছিল।
সেই নাগরিকত্বের ধারণাই নেই আর; তার স্থান নিয়েছে কনজিউমারের অ্যাস্পিরেশন। তাহলে যুক্তি-পরম্পরায় উন্নত চলচ্চিত্রবোধের প্রয়োজন আর থাকেনা; বরং অবস্থাপন্ন মধ্যবিত্তের প্রেস্টিজিয়াস ছবির প্রয়োজন রইল স্রেফ ‘কালচারাল কুলীন’ হতে। এমন ভিন্নধর্মী ছবি কিন্তু হওয়া সম্ভব যা এই ‘বাঙালিয়ানা’ (স্বচ্ছল-দাম্ভিক বা দুঃস্থ-বেচারা, দু’ধরনের উদাহরণই পাওয়া যায়) নির্মাণে উৎসাহী নয়। সাংস্কৃতিক শ্লাঘা সেই ছবির কাম্য নয়; সেই ছবি সাংস্কৃতিক কৌলিন্যকামী নয়। তেমন ছবিতে কি মিডিয়া বা মধ্যবিত্ত-ভোক্তা সমাজের উৎসাহ থাকবে?
কালচার একটি জনগোষ্ঠীর কনসেনশাসে তৈরি কিছু চিহ্ন মাত্র। সংস্কৃতির ভিতর-বাহির থাকে; সংস্কৃতি সদাসর্বদা ব্যস্ত থাকে তার ভিতরে কী আছে, আর কী তাতে শোভা পায়না – এইসব নিয়ম-নিদানে। সেভাবেই কালচারের ব্যবসা হয়, এটা আমাদের দর্শক ঠিক ‘খাবে না’, এই আন্দাজ কালচারেরই আন্দাজ। আর্ট সেই আলোকিত বৃত্তের সীমানার বাইরের অন্ধকারে কী আছে তাতেই উৎসাহী থাকে। উত্তর কলকাতার ভগ্ন ঐতিহ্য, দক্ষিণ কলকাতার মগ্ন লিবারালপনা – এইসব আর্টের বিষয় নয়, কালচারের বিষয়। তাই শিল্প-সংস্কৃতি যুগ্মপদটি পরিহার করে, কালচারই যে ইন্ডাস্ট্রি, কালচারই যে বিজ্ঞাপন – এটা মেনে নেওয়া ভাল। আর্ট সেই চৌহদ্দির বাইরের জিনিস, যদিও আর্টের ফসল হল কালচারের fodder, কালচার শিল্পকর্মকেই চিবিয়ে খেয়ে জাবর কেটে বাঁচে। পরিহাস এই – কালচার ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির আর কোনও পুঁজি নেই, পণ্য নেই, ভোগ্য নেই, আত্মপরিচয় নেই; সেজন্যই বাঙালির কালচারাল প্রোডাকশন লাগে, তার শৈল্পিক মূল্য অকিঞ্চিৎকর হলেও।
বাঙালি তাই এখন কালচার খায় শুধু, তা নিয়ে ভাবে না। সেইজন্যই চলচ্চিত্রবোধের অবক্ষয়। এইজন্যই দেখবেন যে ইউটিউব রিভিউয়ার বেশ উচ্চমানের রিভিউ করতে সক্ষম, তাকে অ্যালগরিদম বজায় রাখতে বাজে ছবিও রিভিউ করে যেতে হয়, এবং বিবিধ ‘আপডেট’, ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে ‘স্পেকুলেশন’ দিতে দিতে সে কার্যত হয়ে যায় ইন্ডাস্ট্রির মুখপাত্র। বাজারে যা ট্রেন্ডিং তা নিয়ে মতামত জানাতে অথবা ফ্যানবেস catering করতে হয় views-এর সংখ্যা স্টেডি রাখতে। এহেন অবস্থায় সমালোচনা করতে যে দুরত্ব প্রয়োজন হয় তা যায় ঘুঁচে। অর্থাৎ, একজন দক্ষ ইউটিউব রিভিউয়ারের মধ্যে একটা স্পষ্ট সত্তার বিভাজন তৈরি হতে বাধ্য – একদিকে সমালোচক, অন্যদিকে ইন্ডাস্ট্রির মাউথপিস। কারণ সে ক্যাপিটালিস্ট প্রোডাকশনের প্রক্রিয়ায় ঢুকে গেছে যখন থেকে তার চ্যানেলের মনিটাইজেশন শুরু হয়েছে। ক্ষতিটা এখানেই হয় যে সে ছবি বিশ্লেষণ করায় দক্ষ, কিন্তু যেহেতু সেও বাজারে প্রবেশ করে গেছে, তার উন্নত চলচ্চিত্রবোধের ভোক্তা কমতে আরম্ভ করবে। জনপ্রিয়তাবিরোধিতা তার পরতায় পোষাবে না। আখেরে market is the greatest leveler, আর বংবাজারের প্রধান প্রোডাক্ট হল কালচার। সিনেমা নিয়ে কমন-সেন্সও তাই, অতএব, কালচার।
কিছুদিনের মধ্যেই তার অন্য বোধোদয় হবে। কনজিউমার মার্কেট ক্রিটিকাল সমালোচনা পছন্দ করেনা। কনজিউমার আর বাজারের যোগসূত্র যখন ইমেডিয়েট, তখন আর এই লোকটির প্রয়োজন নেই যে কিনা প্রোডাক্টের গুণমান বিচার করার স্পেশালিস্ট। সেই কাজটি ভোক্তার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই হবে। তাই রিভিউয়ারকে হতে হবে কনজিউমারের প্রতিনিধি। যেহেতু বাংলায় চাকরি নেই, চাকরি থাকলেও মাইনে কম, মানুষের হাতে উদবৃত্ত অর্থ কম, মধ্যবিত্ত পাঁচশো টাকায় কফিশপে এক ঘন্টা আড্ডায় ব্যয় করে কিন্তু সেই টাকাটা সিনেমা দেখা বা বই কেনার আগে তিনবার ভাবে। আপাতত রিভিউয়ারের মূল্য এটুকুই যে রিভিউয়ার বলে দিচ্ছে ছবিটা দেখবেন নাকি দেখবেন না। যদি কোনো সুদিনে মানুষের হাতে টাকা বেড়ে যায়, তখন আর রিভিউয়ারের চুলচেরা বিশ্লেষণের প্রতি কনজিউমারের ধৈর্য থাকবেনা।
বলাই বাহুল্য, রিভিউ আর সমালোচনা এক নয়, সমালোচনা আর ক্রিটিকাল সমালোচনা এক নয়, ক্রিটিকাল সমালোচনা আর তত্ত্ব এক নয়। তাই চর্চা এখন শুধু বাজারি ছবি নিয়েই হয়, সেই চর্চা থেকে ‘নতুন সিনেমা’ বা ‘অন্য সিনেমা’-র চাহিদা তৈরি হওয়ার সুযোগ হ্রাসমান। যিনি ভাবছেন যে এহেন সিনেমার আর কোনও প্রয়োজন নেই, তিনি আর্টি ছবিকে ‘আঁতেল’ ছবি মনে করেন, দেখেন না, তাঁকে জানানো যে মূলধারার ছবিতেও ‘নতুনত্ব’ এবং ‘ভিন্নত্ব’ প্রয়োজন হয় এবং সেটা কীরকম তা বুঝতে বা বোঝাতে গেলেও প্রয়োজন হয় উন্নত চলচ্চিত্রবোধ। বাজারি ছবি মানেই শিল্পমূল্যের নিরিখে খারাপ ছবি নয়। সেভাবেই বাজারি ছবি নিয়ে আলোচনা করার প্রক্রিয়াও তাকে দূরছাই করার প্রক্রিয়া নয়। এই ভুল ধারণার জন্যই আমাদের প্রচূর ভাল ছবির appraisal হয়নি। বাংলার মেনস্ট্রিম সিনেমার শ্রেষ্ঠ সময়ের মূল্যায়ন হয়েছে একমাত্র যে বিভাগে আমি পড়াই সেখানে, অহমিকা সহকারে বললাম। যে ফিল্ম-স্কুল, ইন্ডাস্ট্রি, ফিল্ম-সোসাইটির লোকজন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম স্টাডিজকে পছন্দ করে না, তাদের জ্ঞাতার্থে জানাই, বাংলা মূলধারার স্বর্ণযুগের যে ফর্ম, তা নিয়ে সিরিয়াসলি আমরাই পড়াশোনা করি; আপনারা সেই ছবির বোধজগৎ এবং ভাষাকে ভুলে গেছেন বলেই আপনাদের মূলধারার ছবি এখন এতটা দিশাহীন।
(চলবে)
-
বাংলা সিনেমার সংকট নিয়ে: প্রথম পর্ব

বাংলা সিনেমার সংকট নিয়ে, আবার …। আবার , কারণ এককালে বোঝার চেষ্টা করেছিলাম বলে … এই লেখায় এবং এই লেখায়।
প্রথমেই এই দীর্ঘ লেখায় সংকট বলতে কী বুঝছি তা বলে রাখি। পাঠক যদি সেগুলিকে সংকট বলে মনে করেন তাহলেই বাকিটা পড়বেন। এই বছরে পশ্চিমবঙ্গ আর কেরালার ছবির বক্স-অফিস কালেকশন তুলনা করলে বুঝবেন। এই বছরের সবচাইতে সফল পাঁচটি মালয়ালাম ছবি হল (সূত্র IMDB) –
১। মানজুম্মেল বয়েস – ২৪১.১০ কোটি টাকা (কেরালা বক্স অফিসে ৭২ কোটি টাকা)
২। আদুজীভিথম – ১৫৮.৪৮ কোটি টাকা (কেরালা বক্স অফিসে ৭৯.২৮ কোটি টাকা)
৩। আভেশম – ১৫৬ কোটি টাকা (কেরালা বক্স অফিসে ৭৬.১০ কোটি টাকা)
৪। প্রেমালু – ১৩৫.৯০ কোটি টাকা (কেরালা বক্স অফিসে ৬২.৭৫ কোটি টাকা)
বিশেষ সাড়া জাগিয়েছিল বলে, বক্স অফিসের নিরিখে না হলেও, ৫ম ছবিটি হল ‘ব্রহ্মযুগম’ (৫৮.৭০ কোটি টাকা; কেরালা বক্স অফিসে ২৪.১৫ কোটি টাকা)
বাংলা ছবির এহেন পরিসংখ্যান পাওয়া খুবই মুশকিলের (সংকটের অন্যতম লক্ষ্মণ)। তাও টলিবাংলা বক্স-অফিস নামক একটি ফেসবুক পেজের ওপর ভরসা করে, শুধুমাত্র জাতীয় মাল্টিপ্লেক্স চেনের হিসেব এরকম (সিঙ্গেল স্ক্রিনের হিসেব পাওয়া যায় না) –
গত বছরের শেষের দিকে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘প্রধান’ রাউন্ড ফিগার ১ কোটি ৮২ লাখ (তেরো সপ্তাহ)
১. অযোগ্য: প্রায় ৯৯ লাখ (ছ’ সপ্তাহ)
২. এটা আমাদের গল্প: প্রায় ৬৮ লক্ষ (সপ্তম সপ্তাহ)
৩. নয়ন রহস্য: প্রায় ৫৩ লাখ ( সপ্তম সপ্তাহ)
৪. অতি উত্তম: রাউন্ড ফিগার ৫০ লাখ ( অষ্টম সপ্তাহ)
৫. বুমেরাং: রাউন্ড ফিগার ২৭ লাখ (চতুর্থ সপ্তাহ)
এই বছরটা নাকি বাংলা সিনেমার মন্দ যাচ্ছে না!
সেই সঙ্গে মালয়ালাম সিনেমায় এই ছবিগুলির সঙ্গে আমাদের সফল পাঁচটি ছবির ‘কনটেন্ট’ ও ফর্ম তুলনা করবেন; তুলনা করবেন শুধু ছবিগুলির রোজগারই নয়, ছবিগুলির বাজেটেরও। সেই সঙ্গে ভেবে নেবেন যে ‘মানজুম্মেল বয়েস’-এর মত ছবি কলকাতায় ২০ কোটি টাকার বাজেট পাবে কিনা, কেন পাবে না, এইরকম মান অর্জন করার পরিকাঠামো পাবে কিনা এবং সর্বোপরি, দর্শকের সমর্থন পাবে কিনা।
কেন এই ফারাক? আফটার অল বাংলা ছবি বলে? আমরা কতদিন এমন ‘আফটার অল’ থাকবো? আমরা কতদিন এমন ‘আফটার অল’-এ তৃপ্ত কুয়োর সোনাব্যাঙ হয়ে থাকবো?
যত তাড়াতাড়ি আমরা মেনে নিতে পারব যে বাংলা সিনেমা (আসলে পশ্চিমবঙ্গীয় সভ্যতা) প্রবল সংকটাপন্ন, তত আমাদের সিনেমার মুক্তি দ্রুত আসবে। বাংলা সিনেমা বিবিধ ট্র্যাপে ঢুকে গেছে। এক জাতীয় বাংলা ছবি মাল্টিপ্লেক্সের বাইরে চলবে না, এক জাতীয় ওটিটির বাইরে টিকবে না, এক জাতীয় ছবি ইউটিউবে থাকবে, এক জাতীয় ফেস্টিভালে ঘুরবে, এক জাতীয় গ্রাম-মফস্বলে যেতে চায়, কখনোই পারবেনা, এক জাতীয় ছবি গ্রামকে ইউরোপে নিয়ে যাবে।
সর্বজনপ্রশংসিত ‘মানিকবাবুর মেঘ’ দেখে এলাম, আর্ট ফিল্ম ঘরানার ছবি; এবং ‘কাউন্টারশট পডকাস্ট’-এ লুব্ধক চ্যাটার্জির সাক্ষাৎকার শুনলাম, তাঁর আসন্ন ছবিটিও আর্ট ফিল্ম ঘরানার ছবি। ‘মানিকবাবুর মেঘ’ পরিচালকের প্রথম ছবি; তাই ধরে নিচ্ছি তরুণ বাঙালি পরিচালকদের অভীষ্ট হল আর্ট সিনেমা। কেন এটা বললাম? কারণ একমাত্র ‘ফেস্টিভাল’-এর ফিল্ম হলেই মিডিয়া খবর দেয় যে এটি পরিচালকের প্রথম ছবি। শেষ কোন কমার্শিয়াল ছবিকে পরিচালকের প্রথম ছবি হিসেবে চিনেছেন? যাই হোক, ছবি এবং পডকাস্ট দুটোই নানানভাবে মন ছুঁয়ে গেল, কিন্তু মন ভরল না। কিন্তু কেন, এই নিয়ে লিখতে দ্বিধা হয় আজকাল, কারণ মনে হতে পারে আমি এই ছবিটাকে বা তরুণ পরিচালকদের সমালোচনা করছি; আমি আদপেই সেই ভাবটি পোষণ করতে চাইনা। আমি আমার দৃষ্টি থেকে ছবিটাকে ক্রিটিকালি দেখতে চাই, পডকাস্টে যা আলোচিত হয়েছে ক্রিটিকালি শুনতে চাই।
কিন্তু বাংলা ছবির পাশে সদর্থে দাঁড়াতে গেলে যে ক্রিটিকাল দৃষ্টি ছাড়া উপায় নেই! ক্রিটিকাল দৃষ্টি যেটা দেখাতে পারে সেটা হল ছবিগুলি কোন দিকে ইঙ্গিত দিচ্ছে, কোন দিকে যেতে পারছে বা পারছে না, অর্থাৎ দিশা কোনদিকে হতে পারে। সোশাল মিডিয়ার আবহে এই ক্রিটিকাল দেখার ভিন্ন সংজ্ঞাকে এখন বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা মুশকিল। অভিনন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত প্রথম চলচ্চিত্রটি ‘ভাল ছবি’, লুব্ধকের ছবিটিও ‘ভাল ছবি’-ই হবে। হয়েই আছে; না হয়ে উপায় নেই। কিন্তু শুধু ব্যর্থ ছবিতে নয়, সফল বা ভাল ছবিতেও সংকটের সিম্পটম থাকে। সেই সিম্পটম নিয়ে কথা বলা মানে ছবিটাকে খারাপ বলা নয়, এই ডিসক্লেমার দিয়ে রাখলাম; বরং বলা যে ছবিটা নিজের করা কোন প্রতিশ্রুতি রাখতে পারছে না এবং কেন পারছে না, এবং সেই না পারাটা কীরকম সংকটের ইঙ্গিতবাহী।
এই লেখায় আমি একটি কমার্শিয়াল ছবিরও আলোচনা করব, তথাগত মুখোপাধ্যায়ের ‘পারিয়া’, যে ছবিটিও সর্বজনপ্রশংসিত হয়েছে। এর সঙ্গে এটাও বলে রাখা উচিত যে সোশাল মিডিয়াধর্মী তাৎক্ষণিক নেগেটিভিটি, যাতে ভাবনাচিন্তার কোনো ভূমিকা নেই, সেখানে ক্রিটিকাল কিছু থাকেনা, আমি সেইসমস্ত মতামত থেকে নিজের দুরত্ব রাখছি। তেমনই কাজের কিছু থাকে না হার্ড-মেন্টালিটি গোত্রের সমর্থনেও। কিন্তু আপাতত আবহ এরকমেরই; বললেই তো আর নিজেকে দূরে রাখা যায় না। দেখি, আমার আলোচনার মেজাজ কীভাবে নিজের অবস্থান নির্ণয় করতে পারে।
বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির বৃদ্ধি ঘটছে না, মানের অবনতি হচ্ছে। এই পিঠ ঠেকে যাওয়া, একটি দুটি পাড়ায় কোণঠাসা হয়ে যাওয়া ইন্ডাস্ট্রির ঘুরে দাঁড়ানো ছাড়া উপায় নেই। গত তিরিশ বছরে আমাদের পরিশীলিত চলচ্চিত্রবোধের প্রসারণ ঘটানো সম্ভব হয়নি; আমরা যত্ন করে তার ক্ষেত্র সংকুচিত করেছি। সেভাবেই যত্ন নিয়ে সংকুচিত করা হয়েছে আমাদের ছবির মার্কেট।
একদা পশ্চিমবঙ্গে আর্ট সিনেমার তরুণ দর্শক নাক-উঁচু ছিলেন। পনেরো বছর আগে একজন বিশ্বসিনেমায় দীক্ষিত যুবক বলতে পারতো যে সারা পৃথিবীতে এতই উচ্চমানের ছবি হয়েছে এক শতাব্দীতে, যে তা দেখেই তার ইহজীবন কেটে যাবে, সে কেন অপর্যাপ্ত বাংলা সিনেমা দেখে সময় নষ্ট করবে? সেই অবস্থা এখন মূলধারার ছবিতে হয়েছে। অন্য কথায়, বাংলার কমার্শিয়াল সিনেমার দর্শক এহেন নাক-উঁচুপনা করেন আজকাল। বাংলা মূলধারার দর্শক, যুবকরা এখন আর বাংলা ছবির কাছে কিছু প্রত্যাশা করে না। স্পেকটাকল্-ধর্মী ছবির জন্য তার তামিল-তেলুগু ছবি আছে, ভিন্নধর্মী ছবির জন্য মালয়ালাম ছবি আছে। আর যুবতীরা কী দেখে বা দেখতে চায়? আমি নিশ্চিত কারুর ধারণা নেই।
এই বছরের সফল বাংলা ছবিগুলির তালিকা আবার দেখুন, হয় তা অতীত-আশ্রয়ী (উত্তমকুমার রিসাইকেল্ড, ফেলুদা রিসাইকেল্ড) নয় তা প্রৌঢ়-আশ্রয়ী (‘অযোগ্য’ এবং ‘এটা আমাদের গল্প’)। বাংলা সিনেমার দুই চল্লিশোর্দ্ধ্ব সুপারস্টার দেব আর জিৎ হলেন প্রোডিউসার-স্টার, তাঁদের সাফল্য গোটা ইন্ডাস্ট্রির সাফল্য হতে পারে না, কারণ বছরে তারা কয়েকটা ছবিই করতে পারেন। অতএব তাদের হিসেবের বাইরে রাখলে কালচারাল নস্টালজিয়া এবং অবক্ষয়ে রোদনের নন্দনতাত্ত্বিক আবেশ পাওয়ার জন্যই বাংলা ছবি আছে; আর আছে এক রক্ষণশীল পরিবার-কেন্দ্রিকতার সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় ধরে রাখার জন্য বাংলা সিনেমা। দুটি ক্ষেত্রেই বাংলা সিনেমা বয়োজ্যেষ্ঠদের সিনেমা, বয়োজ্যেষ্ঠ মানসিকতার সিনেমা। এই লেখা যখন লিখছি, তখন এসভিএফের একটা ছবিকে কেন্দ্র করে একরকম অচলাবস্থা শুরু হয়েছে ইন্ডাস্ট্রিতে। এই প্রসঙ্গগুলো অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু সেইগুলি নিয়ে এই লেখায় কিছু থাকবে না কারণ তা নিয়ে লিখতে গেলে ইন্ডাস্ট্রির ইনসাইডার হতে হয়। আমি আপাতত এই সংকটকে দেখব শুধুমাত্র দর্শক হিসেবে।
কমার্শিয়াল, আর্ট ইত্যাদি বিভাজন আর কার্যকরী নয়
কারণ একধরণের সংকট সর্বব্যাপী, শুধুমাত্র একটি খোপে সীমাবদ্ধ নয়। আমি আশি-নব্বইয়ের দশকে শুনতাম ভিন্নধর্মী পরিচালকরা বলছেন যে কমার্শিয়াল ছবির দৌরাত্ম্যে তাঁদের শিল্পীজীবন অতীষ্ঠ হয়ে যাচ্ছে। আবার হালে কিছু ইউটিউব রিভিউয়ারদের প্রধান অভিযোগ যে বাংলা কমার্শিয়াল ছবি তীব্র সংকটে আছে, মুষ্টিমেয় নাগরিক দর্শকদের জন্য ‘আঁতেল’ ছবি বানিয়ে বানিয়ে যারা আপামর জনতা, সেই দর্শকগোষ্ঠীকে হারিয়েছে টালিগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রি। তাই এই আলাদা খোপের সংকট নিরীক্ষা করে লাভ হবেনা, সেগুলি অন্ধগলি। সার্বিকভাবেই সমস্যা হল এরকম যে – বাংলা ছবি দিশাহীন, দর্শক ঠিক কোন ছবিকে চায়, কোন ছবির পাশে থাকবে তা নির্ণয় করা মুশকিল। হয়তো বাংলা ছবির দর্শকদের বাংলা ছবি দরকার নেই।
‘কাউন্টারশট পডকাস্ট’-এ লুব্ধক চ্যাটার্জিকে খুব আশাবাদী একজন মানুষ মনে হল। তাঁর কথা আশ্বাস দেয়, শুনতে ভাল লাগে। কিন্তু যাঁরা আশা হারাচ্ছেন, চলে যাচ্ছেন মুম্বই বা অন্যত্র এটা বুঝে যে এখানে কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়ছে, তাঁদের নেতিবাচনকেও তো মন দিয়ে শোনা প্রয়োজন, তাঁদের যেটা প্রতিবন্ধকতা মনে করা হচ্ছে তার সুরাহা ভাবা প্রয়োজন। সমস্যাটা এই নয় যে ‘ভিন্নধর্মী’ কাজ করা কঠিন হয়ে পড়ছে বাংলায়, সমস্যাটা এখানেও যে মূলধারার ছবিরও কোনও সুস্থির আকার নেই এই ইন্ডাস্ট্রিতে।
এবং এই ‘সুস্থিরতা’-র ভিত হল এক এবং একমাত্র যদি দর্শকদের ধারণা থাকে যে তাঁরা এই দুই ধরনের ছবির কাছ থেকে ঠিক কী চাইছেন। আমরা যে সময়ে আছি, তখন দর্শকদেরও সেই ধারণা অস্পষ্ট। অথচ তাঁদের ছবি দেখার অভিজ্ঞতা কিন্তু তিরিশ বছর আগের মত সীমাবদ্ধ নয়। তাঁরা ওটিটি-তে সুনির্মিত একটা ইংরেজি বা হিন্দি ভাষায় ক্রাইম-ড্রামা দেখেও পানসে বাংলা ডিটেকটিভ গল্পকে হিট করিয়ে দেন। যুবসম্প্রদায়ের কমার্শিয়াল ছবির কাছে যে চাহিদা তৈরি হয়েছে (যেখানে স্ট্যান্ডার্ড রেফারেন্স হল দক্ষিণের ছবি) সেই স্কিল, কারিগরি উৎকর্ষ এবং পুঁজির স্থাপত্য বাংলা সিনেমা তার নিয়ত ছোট হতে থাকা বাজারে কোনওদিনও মেটাতে পারবে না। বাংলা মূলধারার ছবির আর কোনও নির্দিষ্ট আকৃতি-প্রকৃতি নেই যা হলে মানুষকে টেনে আনতে পারে। কেবল আবার একটা সেকেলে ধরনের (একেলে বিষয়ের হলেও) গোয়েন্দা গল্প, আবার নস্টালজিয়া-পণ্য বা বয়োজ্যেষ্ঠ-কেন্দ্রিক পারিবারিক গল্প ছাড়া আর কিছুতে দর্শকের ন্যূনতম উৎসাহ আছে বলে মনে হয় না। বাংলা ভিন্নধর্মী ছবির একমাত্র মূল্য হল হৃদয়ে আলোড়ন তোলা সহজপাচ্য পেলব সেন্টিমেন্টালিজম, যা অবধারিত একরকম বিগতর ব্যথা নান্দনিক ভাবে উদ্রেক করে। ভেবে দেখুন, আখেরে দুই ধরনের ছবিরই বিষয়-বস্তু এক; অতএব দুই ধরনের ছবিতেই যে সম্ভাবনার রাস্তা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে সেটা হল ‘নতুনত্বের’; দুই ধরনের ছবিই আমাদের যা টিমটিম করে আছে, বা যা হারিয়েছে তা নিয়ে ব্যস্ত। অতএব, সংকট আছে দুই ধরনের ছবিতেই।
মূলধারার (‘কমার্শিয়াল’ শব্দটা নিয়ে অসুবিধে হয়) এবং বিকল্প বাংলা ছবি – দুই ধরনের ছবিতেই যে একধরণের সংকট আছে, সেটা না স্বীকার করলে এগোনো যাবেনা। সংকটের নিরিখে বাংলা সিনেমায় কমার্শিয়াল, আর্ট ইত্যাদি বিভাজন কার্যকরী থাকে না।
তবে, বিভাজনটা বললেই চলে যাবে না; থাকবেই। কারণ কিছু কিছু ছবি যদি পর্যাপ্ত সংখ্যার দর্শকের আশীর্বাদ না পায় তবে তাকে ফেস্টিভাল সার্কিটের ওপর নির্ভর করতে হবে, এমনকি বিদেশি দর্শকদের ওপরও। এটা প্রযোজনার ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে। কিছু ছবি প্রযোজকদেরই পৃষ্ঠপোষকতা পাবে না, তখন তাকে হয় কর্পোরেট নয় বিদেশি ফান্ডের ওপর নির্ভরশীল হতে হবে। এই ফান্ডগুলোর সঙ্গেও আসে শর্তাবলি। বেশিরভাগ ইউরোপীয় ফান্ডই রাষ্ট্রীয় ফান্ড, তাদের কলাকুশলীদের জীবিকা তৈরি করার জন্য (কারণ ইউরোপে নিজেদের মূলধারার ছবির বাজার খুব খারাপ)। তাই তাদের টেকনিশিয়ান নিতে হয়। তাদের নান্দনিক শর্তাবলিও থাকে। এবং অবধারিত যে জিনিসটা কমতে থাকবে এহেন, সেটা হল পরিচালকের নিজের ঐতিহাসিক বাস্তবতা থেকে জাত নিজস্ব vision – বিশ্ববাজারে একরকম ভারতবর্ষের ধারণা, একধরনের ইমেজ ও সাউন্ডের গঠন, একধরনের ethnographic exotica ছবির ওপর আরোপিত হতে থাকবে, বা থাকার সম্ভাবনা বাড়বে। এই ছবিগুলিকেই বলা হয় ‘আর্টহাউজ সিনেমা’।
এটা মানলে ভাল, নয়ত ডিনায়ালে থাকতে হবে যে ফেস্টিভালের ইউরোপের ম্যাপে আমরা আর exist করিনা, সেখানে আমরা মুছে গেছি, অতএব সেখানে আমরা সবসময়েই বিগতর স্পেসিমেন, ঈষৎ বিচিত্র, ডেটা ক্যাপিটালিজমের যুগে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাপিটালিজমের মিউজিয়াম। আমি ইউরোপীয় ফেস্টিভাল সার্কিটে বাংলা সিনেমা নিয়ে আর উৎসাহী নই এই কারণেই, কারণ আমরা ওদের কাছে ethnographic curiosity বই আর কিছু নই। যা সমসময়ে, যে আধুনিকতায় আছি সেই আধুনিকতায় এনগেজ করবে – বৃহত্তর বিশ্বসিনেমা বাংলা সিনেমার কাছে এমন ছবি প্রত্যাশা করা বন্ধ করে দিয়েছে। কারণ আমরা সেই বিপন্ন অস্তিত্বের জন্তু যারা নিজেদের সংস্কৃতির স্যাংচুয়ারি নিজেরাই বানাচ্ছি।
আর্ট সিনেমা আর আর্টহাউজ সিনেমা কি একই জিনিস?
বাংলা আর্ট সিনেমা যখন তার শ্রেষ্ঠ মুহূর্তে ছিল তখন আন্তর্জাতিক ভিন্ন সিনেমার ক্ষেত্রে তার কিছু অবদান ছিল। শতবর্ষে সত্যজিৎ-মৃণাল-ঋত্বিক নিয়ে ভাবা, লেখার সময়ে বুঝতে পারছি এঁরা ঔপনিবেশিক এবং পরবর্তী পর্যায়ে আধুনিকতার উত্থান এবং মধ্যবিত্তের সংকট নিয়ে ক্রমাগত ভেবে গেছেন, যেভাবে ভাবা ঠিক পাশ্চাত্যের অগ্রগণ্য দেশগুলির পক্ষে সম্ভব ছিল না। ইতিহাসের মৌলিকতার দিকে এই শিল্পীদের পাখির চোখের দৃষ্টি ছিল। অতএব আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁদের নির্দিষ্ট কিছু বলার ছিল। এবং সেই বলার জন্য তাঁরা নতুন কিছু ফর্মের সন্ধান করে গেছেন। যেমন, সত্যজিৎ ভেবেছেন বাস্তববাদের রকমফের নিয়ে, ঋত্বিক একধরনের আধুনিকতাবাদী মেলোড্রামার ব্যবহার নিয়ে, মৃণাল সেন ব্রেখটীয় ফর্ম নিয়ে, নাটক এবং সিনেমার সংশ্লেষ নিয়ে। সেই সময়ে বিকল্প এবং মূলধারার মধ্যে ফারাকও কম ছিল। বাংলা সিনেমা সেই সময়ে নানাবিধ ‘মডেল’ দিয়ে গেছে অন্যান্য আঞ্চলিক, এমনকি হিন্দি ছবির ইন্ডাস্ট্রিকেও। এখন সে দেশের এবং বিশ্বের পশ্চিমের দিকে মুখ হা-পিত্যেশ করে বসে থাকে মডেলের আশায়।
গত তিরিশ বছরের বাংলা আর্ট সিনেমা নতুন ফর্ম নিয়ে কী ভেবেছে? ফিল্মমেকাররা আর্টহাউজ সার্কিটের কিছু ফর্ম নিয়ে এনে অ্যাপ্লাই করছেন মাত্র, তাতে স্বকীয় কিছু মোচড় না দিয়ে। যেমন, যখন ‘স্লো সিনেমা’ ফেস্টিভাল সার্কিটে প্রায় তামাদি হওয়ার জোগাড় তখন ‘স্লো সিনেমা’-কে আবিষ্কার করা কি রিপ-ভ্যান-উইঙ্কিলিজম নয়? নতুন ফর্মের সন্ধান করার বদলে যা আর্টবাজারে চলে তার সারসংক্ষেপ পেশ করে লাভ কি? সেভাবেই, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্যাপিটালিজমের যুগে আধুনিকতা নিয়ে ক্ষুরধার ভাবনা রেখে গেছেন পথিকৃৎ-রা; আমরা ক্যাপিটালিজমের একদম ভিন্ন পর্যায়ে থেকে পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহাসিক বাস্তবতা নিয়ে সেরকম কি ভাবতে পারছি? আমাদের ঐতিহাসিক বাস্তবতাও তো পাল্টেছে। সেখানে বিগততে যা ছিল তাকে গ্যালারিতে সংরক্ষণ করার বদলে পরিবর্তনকে কীভাবে বুঝছি আমরা? উত্তর কলকাতার রঙিন ছবি তুলে তা কালার-কারেক্ট করলে বিজ্ঞাপন হয়; তাকে সাদা-কালো করে তুললে গ্যালারিতে ফোটো-এক্সিবিশন হয়। অন্তত সেই পরিসরে যাদের দিন আনা দিন খাওয়া যাপন তাদের সঙ্গে সংযোগ হয়না।
কিছুদিন আগে (বোধ করি বাংলাদেশে অধুনার টালমাটাল অবস্থার আগে রেকর্ড করা, কারণ উনি বলছেন বাংলাদেশে একধরনের ‘ফ্যাসিস্ট’ আবহে র্যাডিকাল পলিটিকাল ছবি করা কীভাবে অসম্ভব) পেশ করা একটি ইউটিউব সাক্ষাৎকারে অমিতাভ রেজা চৌধুরী বুঝিয়েছেন যে আর্ট ফিল্ম সার্কিট আসলে একধরনের বাজার ছাড়া কিছুই নয়, এবং সেখানকার মতই তাতে বাজারি ছবি হয়, যাতে তাঁর আগ্রহ নেই তেমন। আমি একদম সেই মুহূর্তে লিংক দিয়ে দিলাম, আপনারা শুনতে পারেন। অর্থাৎ, একজন আর্টহাউজ সিনেমায় অংশগ্রহণ করবেন কি করবেন না, সেগুলোও রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত। এই মুহূর্তের কিছুক্ষণ আগেই উনি বলছিলেন যে কীভাবে পুঁজির একধরনের রমরমার ফলে বাংলাদেশে একধরনের আন্তর্জাতিক ছবি করার সম্ভাবনা এখনই, নয়তো সেটা ফসকে যাবে (হয়তো গত সপ্তাহের ঘটনা এই নিরিখে একটা বড় সেটব্যাকে ফেলবে বাংলাদেশের ছবিকে)। অমিতাভ নতুন ছবিকেও ইন্ডাস্ট্রি বা ব্যবসার ‘গ্রোথ’-এর নিরিখেই দেখছেন; এবং সেভাবে দেখছেন মানে তার শিল্পমূল্যকে অবহেলা করছেন না।
বোঝা উচিত, ঠিক এইভাবেই, পশ্চিমবঙ্গের ছবি কিন্তু তথাকথিত আন্তর্জাতিক, এবং অধুনা কর্পোরেট, ‘আর্টহাউজ বাজার’ থেকে ফসকে গেছে। সেই বাজারে, সেই পুঁজিতে তার ‘অ্যাক্সেস’ নেই আর। তার কারণ বিবিধ এবং জটিল। এমনও হতে পারে, সেখানে ইন্টারেস্টিং এবং সময়োপযোগী কোনো ফর্ম বা আধুনিক অভিজ্ঞতার দলিল পশ্চিমবঙ্গের ছবির পক্ষে পেশ করা সম্ভব হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না, সেটা সন্ধান করতে হলে আগে স্বীকার করতে হবে যে সেই বাজারে উপস্থিতি আমরা হারিয়েছি।
আর্টহাউজ সিনেমা একধরণের আন্তর্জাতিক ব্যবসা-ব্যবস্থা; আর্ট সিনেমা কিন্তু একদম আঞ্চলিক আন্তর্জাতিকতার ফসল ছিল। ব্যাপারটা বোঝাই। আর্ট সিনেমার জন্ম হয় দু’ভাবে – এক, বিশ্বসিনেমার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ফলে বোঝা যায় যে সিনেমার কিছু ‘ধরণ’ স্থানীয় ইন্ডাস্ট্রিতে চর্চিত হচ্ছে না, সেগুলি তৈরি করার ইচ্ছে জাগে নবীন ফিল্মমেকারদের মধ্যে, আন্তর্জাতিক সিনেমায় তখন নতুন সিনেমার কিছু ধারা বহমান থাকলে তাতে অংশগ্রহণের ইচ্ছে তৈরি হয়। যেমন বিশ্বযুদ্ধের পর নিওরিয়ালিস্ট বা নবতরঙ্গের ধারা। দুই, স্থানীয় ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে কিছু শৈল্পিক-রাজনৈতিক চাহিদা তৈরি হয় ভিন্ন ছবির। অর্থাৎ এখানে নান্দনিক ধরনটি হয় একদম নিজস্ব, যেমন যুদ্ধপরবর্তী বিভিন্ন লাতিন আমেরিকান নতুন সিনেমার মুভমেন্ট। এই দু’রকম কারণও মিলে মিশে যেতে পারে।
অধুনার বাংলা সিনেমার সংকটটা এখানেই। বাঙালির আন্তর্জাতিক সিনেমার প্রতি এক্সপোজার দশ-বিশগুণ বেড়েছে, কিন্তু আন্তর্জাতিক কিছু আঙ্গিকে তার স্থানীয় অভিজ্ঞতা কীভাবে বুনে দিতে হবে এই নিয়ে আমাদের ধারণা কমেছে। সহজ উদাহরণ, এই জন্যেই আমাদের নিজস্ব কল্পবিজ্ঞান সিনেমা নেই (পুঁজি এবং উন্নত প্রযুক্তির দোহাই দিয়ে লাভ নেই; কম বাজেটের কল্পবিজ্ঞান ছবিও হয়), নেই ফ্যান্টাসি সিনেমা। এ তো জঁরের উদাহরণ দিলাম শুধু, এই প্রসঙ্গে পরে আরো বলবো। যারা জানেন সাইফাই বা ফ্যান্টাসি (বা হরর বা সুপারন্যাচারাল) মানেই মূলত বিনোদন-ধর্মী ছবি, তার সঙ্গে আর্টহাউজের কী সম্পর্ক? তাদের আপাতত এটাই বলার – ভুল জানেন।
দ্বিতীয়ত, আর্ট সিনেমা সিভিল সোসাইটির চাহিদা ছাড়া হয়না। হয়ত কোনও ছবিই হয়না। অর্থাৎ, শুধুমাত্র মেকারদের ইচ্ছে যথেষ্ট নয়; দর্শককুলেরও ভিন্ন সিনেমাটিক অভিজ্ঞতার একটা চাহিদা, একটা খিদে প্রয়োজন হয়। কিন্তু শিল্প কি আমাদের দৈনন্দিন চাহিদার মধ্যে পড়ে আর? শুধুই তো ছুটি পেলে কনজাম্পশনের জন্য সিনেমার কথা মনে আসে আমাদের। সেক্ষেত্রে আরো একটা পানসে ফেলুদাই ভোগ্য হবে আমাদের ভাগ্যে। কনজিউমার সত্তা ঠিক উন্নত শিল্পবোধের সহায়ক নয়, যদি না জাতিগত ভাবেই আমাদের শিল্পবোধ উন্নত হয়। বাঙালিদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আর সেরকম নেই, স্বীকার করে নেওয়া ভাল। আমরা যখন কনজিউমার-কালচারে নিমজ্জিত হলাম নতুন শতক আসার পর, তখন আমাদের চলচ্চিত্রবোধ তলানিতে ঠেকেছিল; তাই সিনেমার ক্ষেত্রে কোয়ালিটি-কনজাম্পশনের ঘটনাটা আমাদের আর ঘটে না।
(চলবে)
-
“সব ছবিরই দর্শক আছে – সেই দর্শককে খুঁজে বের করতে হবে” চলচ্চিত্রকার লুব্ধক চ্যাটার্জীর সঙ্গে আড্ডায় সায়ন্তন

আজকাল অনেকেই একটা কথা প্রায় বিনাপ্রশ্নে মেনে নেন, খানিকটা উপপাদ্যের স্বতঃসিদ্ধের মত, যে ‘চেনাছকের বাইরে গিয়ে ছবি করলে তার দর্শক হবে না’। অর্থাৎ কেউ যদি চিরাচরিত ফর্মুলা মেনে জাবর কাটতে না চান, তবে তাকে লোকসান পোয়াতে হবে। আমাদের পডকাস্টের নতুন অতিথি কিন্তু অন্য কথা বলছেন। তাঁর দাবি – সব ছবিরই দর্শক আছে, কেবল তাকে খুঁজে নেওয়ার পরিশ্রমটুকু করা চাই।
কাউন্টারশটের দ্বিতীয় পর্বে আমাদের সঙ্গে আড্ডায় রয়েছেন নবীন পরিচালক শ্রী লুব্ধক চট্টোপাধ্যায়। লুব্ধকের ছবি রটারডাম চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হয়েছে, সম্প্রতি তাঁর নতুন পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবি ‘হুইসপার্স অফ ফায়ার অ্যান্ড ওয়াটার’ (২০২৩) -এর প্রদর্শনী হয়েছে প্রসিদ্ধ লোকার্নো চলচ্চিত্র উৎসবে। বাঙালি দর্শক স্বভাবতই তাঁর সাফল্যের কথা শুনে আশায় বুক বাঁধে। কেরিয়ারের শুরু থেকে বিশ্বচলচ্চিত্রের আঙিনায় তাঁর অনায়াস আনাগোনা, অন্যদিকে তাঁর ছবির বিষয় এবং প্রকাশভঙ্গি জুড়ে থাকে ব্যক্তিগত, দেশজ অভিজ্ঞতার ছায়া। দেশের প্রান্তিক মানুষের জীবন নিয়ে তিনি ছবি করেন, অথচ ছবির ভাষায় রেখে দেন সার্বজনীনতার পরশ। এই প্রসঙ্গে উঠে আসে শিল্পী হিসেবে নিজের প্রকাশভঙ্গি নির্বাচনের কথা, ক্যামেরার সঙ্গে মানুষ ও প্রকৃতির টানাপোড়েনের ইতিবৃত্ত, এবং শিল্পীর নৈতিক দায়। সর্বোপরি, আপস না করে, সকল বাধা পেরিয়ে, ক্রমাগত ছবি করে যাওয়ার পিছনে যে উদ্যম ও পরিকল্পনা প্রয়োজন, তাই নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা। যাঁরা স্বাধীনভাবে ছবি করতে চান, অন্যধারার ছবি সম্বন্ধে যাঁদের কৌতূহল রয়েছে — তাঁরা সকলেই এই আড্ডা থেকে ভাবনাচিন্তার খোরাক পাবেন, এই আশা রইল।
সম্পূর্ণ আড্ডাটি শুনতে পাবেন এইখানেঃ
-
চলচ্চিত্রকার যুধাজিৎ বসুর সঙ্গে আড্ডায় লাবণ্য
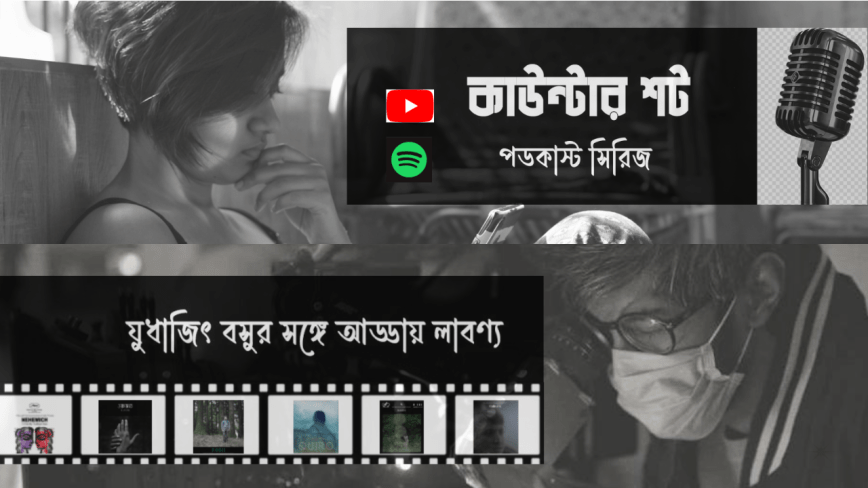
কাউন্টার শট পডকাস্ট সিরিজের প্রথম পর্বে থাকছে আমাদের সহসম্পাদক লাবণ্য দে-র সঙ্গে তরুণ পরিচালক যুধাজিৎ বসুর কথোপকথন।
যুধাজিৎ পুনের ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া-র ছাত্র, তাঁর বানানো ছবির সংখ্যা চারটি, কিন্তু তাতেই সাড়া পড়ে গেছে এদেশ ও ভিনদেশের দর্শকের একাংশের মধ্যে। যুধাজিতের তথ্যচিত্র ‘কালসুবাই’ (২০২০) শ্রেষ্ঠ ছবির সম্মান পেয়েছে ওবেরহাউসেন উৎসবে। ২০২৩ সালের ছবি ‘নেহমিচ’ জায়গা করে নেয় কান চলচ্চিত্র উৎসবের প্রসিদ্ধ লা সিনেফ বিভাগে। এছাড়াও দুনিয়ার তাবড় তাবড় চলচ্চিত্র উৎসবের মঞ্চে সমাদৃত হয়েছে তাঁর ছবি। আজকের পর্বে যুধাজিৎ কথা শুরু করেছেন ভিনদেশি আন্তর্জাতিক ফেস্টিভালের গুরুত্ব নিয়ে। এরপর কথাপ্রসঙ্গে এসেছে তাঁর শর্ট ফিল্ম বানানোর অভিজ্ঞতা; জানিয়েছেন দর্শকের সংখ্যা সীমিত হওয়া সত্ত্বেও স্বতস্ফূর্তভাবে ছবি করে যাওয়ার প্রেরণা তিনি কোথা থেকে পান। ফিল্মমেকিং এবং ফিল্মের তাত্ত্বিক চর্চা–এ দু’য়ের দূরত্বকে যুধাজিৎ নিজে কোন চোখে দেখেন–কথা বলেছেন তা নিয়েও। এছাড়াও রয়েছে গান, সাহিত্য, ফোটোগ্রাফি, এবং আজকের ডিজিটাল মিডিয়ার রমরমা নিয়ে একঘন্টার জমজমাট আলোচনা।
সম্পূর্ণ পডকাস্টটি শুনতে পারেন এখানে:
-
যন্ত্রের জঠরে অদৃশ্য দেশ: পরাধীন ফিলিস্তিন ও আক্রান্তের স্মৃতি

-আবার যে কখনও হাইফাকে দেখব, তা আমি ভাবতেও পারিনি।
-তুমি হাইফাকে দেখছ না। তোমাকে ওটা দেখানো হচ্ছে।
হাইফায় ফেরা, ঘসসান কানাফানি, পৃ. ১৫১
Why did you bring me back here when I can’t feel this place? I can’t even see it, they are showing it to me.
You father was born 100 years old and so was the Nakba, রাজান আলসালাহ
১
ফিলিস্তিনি সাহিত্যিক ঘসসান কানাফানি-র নভেলা হাইফায় ফেরা (عائد إلى حيفا) ছেপে বেরোয় ১৯৬৯ সালে1। ১৯৪৮ সালের এপ্রিল মাসে ব্রিটিশ এবং ইজরায়েলি সেনার দ্বারা উৎখাত হওয়া অজস্র ফিলিস্তিনির মধ্যে এক দম্পতি– সইদ ও সইফয়া, এই দুজন কুড়ি বছর পর তাদের বাসস্থান হাইফা শহরে ফিরে আসে, তাদের এই ফিরে আসার বৃত্তান্ত এই নভেলার উপজীব্য। দুই দশক আগে বাড়িঘর ছেড়ে পালানোর সময় তাদের তৃতীয় সন্তান, পাঁচ বছরের খালদুনকে তারা পিছনে ফেলে এসেছিল, আসতে বাধ্য হয়েছিল। নিজেদের পুরোনো বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে তারা বদলে যাওয়ার নিশানগুলো দেখে। পোল্যান্ড থেকে আসা এক ইহুদি পরিবারের হাতে চলে গেছে বাড়ির মালিকানা; বাড়ির ফলকে বদলে যাওয়া মালিকের নাম থেকে শুরু করে নতুন কলিং বেল, আসবাব, ফুলদানি এসবের সাথে সহাবস্থান করছে তাদের চেনা পুরোনো সিরিয়ান গালিচা, দেয়ালে বাঁধানো জেরুসালেমের ফোটো। সইদের মনে হয়, সেই বাড়ি এককালে তাদের হলেও, আজ কুড়ি বছর বাদে সে তার পুরোনো বাসিন্দাদের চিনতে পারছে না, তাদেরকে ‘অ্যাকনলেজ’ করছে না–ঠিক যেমন আজন্ম-চেনা শহর হাইফাও তাদেরকে আপন করে নিচ্ছে না। কিন্তু আরো বীভৎস মজা অপেক্ষা করছিল তাদের জন্য। অচিরেই তারা আবিষ্কার করে, তাদের হারিয়ে যাওয়া ছেলে খালদুন এখনও জীবিত, এই বাড়িতেই তাকে অপত্যস্নেহে বড় করে তুলেছে ইহুদী দম্পতি। সে এখন ইজরায়েলি বাহিনীর যোদ্ধা, কদিন পরেই অস্ত্র হাতে লড়তে নামবে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে। সইদ এবং সইফিয়ার কুড়ি বছর আগের স্মৃতি হাইফায় ফেরা ইস্তক ঘা খেয়ে খেয়ে বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন, দূরের স্বপ্নের মত অলীক হয়ে যায়। আখ্যানের উপান্তে এসে সেই বিচ্ছিন্নতা পৌঁছয় চরমে। আজন্ম যে সর-জমিনের সঙ্গে আত্মীয়তা বোধ করে এসেছে, এমনকি যে রক্তের টান তাদের অন্তরাত্মাকে কুড়ে কুড়ে খেয়েছে—বছর কুড়ি বাদে ফিরে আসার পর এক অচেনা বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে মনে হয় যেন সবই মিথ্যে। সইদ সফিয়াকে জিজ্ঞাসা করে, ‘স্বদেশ কাকে বলে?’ স্বদেশ মানে কি তাদের ফেলে যাওয়া জিনিসগুলি, যেগুলো কুড়ি বছর পরেও বাড়ির মালিকরা বাতিল জিনিসের মত বের করে দেয়নি? স্বদেশ মানে কি তাদের হারিয়ে যাওয়া সন্তানের স্মৃতি, তাকে ঘিরে জন্ম নেওয়া আশা, দুরাশা, খোয়াব? সইদ নিজেই তার জবাব দেয়, “স্বদেশ হল সেই দেশ, যেখানে এসব কিছুই ঘটার কথা ছিল না।” (১৮৬) ‘এসব’—অর্থাৎ বাস্তুহারা হওয়া, দেশচ্যুত হওয়া, নিজের সন্তানকে ‘অপর’ হয়ে যেতে দেখা।
কানাফানির উপন্যাস প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় পাঠকের উদ্দেশে: ফিরে যাওয়া, প্রত্যাবর্তন, স্মৃতি– এসবের সার্থকতা কী? আদপেই কি স্মৃতির স্বদেশে ফিরে যাওয়া সম্ভব? ঋত্বিক ঘটকের কোমল গান্ধার (১৯৬১) ছবির নায়ক ভৃগু যখন বলে, দুই বাংলার সংযোজক রেললাইনটি ‘কেমন যেন’ যোগচিহ্ন থেকে বিয়োগচিহ্ন হয়ে গেছে (পার্টিশনের পর), তখন তাতে প্রত্যাবর্তন ও স্মৃতি— দুইয়েরই সংকট ধরা পড়ে। জাতিরাষ্ট্রের সীমানা টপকে অবলীলায় পূর্ববঙ্গে ফিরে যাওয়া যদিও বা সম্ভব হয়, মনের মধ্যে জ্বলজ্বল করছে যে অতীতের স্বদেশ– কালের ভাঙা সেতু ডিঙিয়ে সেখানেও কি ফিরে যাওয়া যায়? ঠিক এখানেই বাস্তুচ্যুত মানুষের অস্তিত্বের বিড়ম্বনা তীব্র হয়ে ওঠে। তার স্মৃতিতে অতীত হল সব পেয়েছির দেশ, আর সেই অতীতের ন্যারেটিভ শেষ হয় এক হৃদয়বিদারক বিলয়বিন্দুতে, যখন সে দেশচ্যুত হয়েছিল। এই কল্পিত স্মৃতির মোড়কে সে তার বর্তমানের সকল না পাওয়ার, না হওয়ার শূন্যতাকে ঢেকে রেখেছে। সেখানে ফিরে যাওয়ার একবগ্গা ইচ্ছে বর্তমানের আস্তাকুঁড়ের ওপর এক মায়াবি আবরণ টেনে দেয়—ভাঙা মানবসত্তাকে জোড়া লাগানোর আশ্বাস জোগায়।
কিন্তু ধরা যাক, সে-দেশে ফিরে যাওয়া গেল। এতদিন সময়ের পলি পড়ে পড়ে তার কিছু দিক মনের মধ্যে আবছা হয়ে গিয়েছে, কিছু আবার ভীষণ স্পষ্ট। ফিরে আসার পর দেখা গেল, দেশটা আর আগের মত নেই, তার চেনাপরিচিত চিহ্নগুলো আরো অচেনা সংযোজনের ভিড়ে বিসদৃশ ঠেকছে। নতুন ক্ষমতাশালী শ্রেণির পছন্দসই নকশায় বদলে গেছে তার ঘরবাড়ির আদল, রাস্তাঘাটের নাম। যেন একটা দেশ আরেকটা দেশের ওপর নিজেকে ঠেসে দিয়ে তাকে আড়াল করে রেখেছে। স্মৃতিমেদুর কল্পনায় অতীতের স্বদেশ তার এককালের বাসিন্দাকে বুকে টেনে নিত, যেন তার জন্যই সে সাজিয়ে বসে ছিল নিজেকে। অথচ বাস্তবের তালগোলপাকানো স্বদেশকে স্বদেশ বলতে দ্বিধা হয়, অক্ষাংশ-দ্রাঘিমার নিরিখে তার অবস্থান একই থাকলেও সে ভিনদেশ। প্রত্যাবর্তন শব্দের মধ্যে রয়েছে আবর্তিত হয়ে পুরোনো বিন্দুতে ফিরে যাওয়ার দ্যোতনা, কিন্তু কানাফানির লেখা অনুযায়ী সেই বিন্দুটি প্রত্যাবর্তনকারী-র কাছে অধরাই থেকে যায়, অথবা সেখানে পৌঁছে যাওবার পর টের পায়, নিজের দেশে সে অনুপ্রবেশ করেছে আগন্তুক হিসাবে। চেনা জায়গা থেকে তার বিযুক্তি ঘটে গেছে, যোগ চিহ্ন বদলে গেছে বিয়োগ চিহ্নে, অতীত আর বর্তমানের মধ্যে এসে গিয়েছে এক অনপনেয় ছেদ। কানাফানির গল্পে হাইফা ছেড়ে দ্বিতীয়বার চলে আসার আগে সইদ তার স্ত্রীকে বলে– তাদের মত যে-সব মানুষ ফিলিস্তিন ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়েছে, তাদের কাছে স্বদেশের খোঁজ হল ‘স্মৃতির ধুলোবালির নিচে চাপা পড়া একটা কিছুর সন্ধান।’ (১৬৭) তার পরেই সে স্বীকার করে– সেই অনুসন্ধানের ফলে উঠে আসে আরো ধুলো, আরো মালিন্য।
২
এই কথাগুলো যখন লিখছি, ঠিক সেই মুহূর্তে ইজরায়েল-অধিকৃত ফিলিস্তিনের গাজা স্ট্রিপ থেকে বাস্তুচ্যুত হচ্ছেন হাজার হাজার মানুষ। দীর্ঘদিন জবরদখল করে রাখার পর ইজরায়েল স্থির করেছে যে গাজা, নাকবার পরে যা ছিল ফিলিস্তিনি ভূখন্ডের বিপুল সংখ্যক আরব অধিবাসীর মাথা গোঁজার ঠাঁই, সেখানে তাদের আর কোনো চিহ্ন রাখতে দেওয়া যাবে না; অতএব জাতিসংঘের রক্তচক্ষু, আন্তর্জাতিক আদালতের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা, দেশের ভিতরে ও বাইরে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন–এ-সব কিছু অগ্রাহ্য করে বেপরোয়া বোমাবর্ষণ আর ড্রোন অ্যাটাকের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইজরায়েলি সরকার। সাতই অক্টোবরের পর থেকে ফিলিস্তিনিদের প্রতিনিধি হামাস একের পর এক শান্তিচুক্তির প্রস্তাব নিয়ে গেছে ইজরায়েলের কাছে, কিন্তু সাম্রাজ্যবিস্তারের লক্ষ্যে অটল সে দেশের শাসক তাতে কান দেওয়া দরকার মনে করেনি। গেরিলাদের নিশ্চিহ্ন করার নামে নির্বিচারে বোম্ মেরে গুঁড়িয়ে দিয়েছে ঘন বসতিপূর্ণ শহর, পথঘাট, হাসপাতাল, ইস্কুল, ইউনিভার্সিটি। শান্তিপূর্ণ মীমাংসা আর কোনো পথ নয় তার কাছে, কোনোদিন ছিল বলে মনেও হয় না2। সোশাল মিডিয়ায় ফিলিস্তিনে সক্রিয় সংবাদদাতাদের প্রোফাইল থেকে ভেসে আসা রক্তে ছোবানো ছবি দেখে আর কোনো সন্দেহ থাকে না– গাজা-সহ স্বাধীন ফিলিস্তিনের স্বপ্নকে ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়াই ইজরায়েল নামক ঘোরতর ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রের ‘ফাইনাল সলিউশন’।
ফিলিস্তিনিদের কাছে এটা কোনো সাম্প্রতিক ঘটনা নয়– ১৯৪৮ থেকে হয়ে আসা মুহূর্মুহূ সামরিক আক্রমণের চূড়ান্ত দানবিক পর্যায় বলা যায় একে। ইজরায়েলি হর্তাকর্তারাই সেটা তৎপর হয়ে মনে করিয়ে দিচ্ছেন। গত বছর অক্টোবর মাসে আরিয়েল কালনার (ইজরায়েলি সাংসদ এবং প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু-র লিকুদ পার্টির সদস্য) টুইট করে বলেছিলেন: ‘Right now, one goal: Nakba! A Nakba that will overshadow the Nakba of 48. Nakba in Gaza and Nakba to anyone who dares to join!’3 পাঠক হয়তো বুঝে গেছেন, ১৯৪৮ সালে ইংরেজদের থেকে জায়নবাদীদের হাতে ক্ষমতার হাতবদল হওয়ার পর ফিলিস্তিনিদের বাস্তুচ্যুত হওয়ার কালান্তক বিপর্যয়কে স্মরণ করা হয় আল নাকবা নামে। কালনারের মত আজকের যুদ্ধবাজ জায়নবাদীরা গাজার ওপর সেই একই বিপর্যয়কে দ্বিগুণ নৃশংসতায় ফিরিয়ে আনার ডাক দিচ্ছেন, এবং গত ছ’মাসের খবরে স্পষ্ট, সে-কাজে তাঁরা নির্মমভাবে সফল। গাজার পূর্বপ্রান্ত থেকে বোমাবর্ষণ শুরু করে ফিলিস্তিনিদের ক্রমশ ঠেলে দেওয়া হয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিমে রাফাহ-এ, এবার সেই শেষ আশ্রয়টি-কেও গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে। এরকম পরিস্থিতিতে যা হয়, আক্রান্ত মানুষের মনুষ্যত্ব এবং তার যাবতীয় লক্ষণগুলিকে অস্বীকার করা হয় ক্ষমতাশালী আক্রমণকারী রাষ্ট্রের তরফে। অর্থাৎ মানুষের পক্ষে যা যা কাম্য, যেসব জিনিস মানুষ হিসেবে তাকে পরিপূর্ণতা দেয়, তার সবই রাতারাতি কেড়ে নিয়ে তাকে সবার সামনে জঞ্জাল, উচ্ছিষ্ট বা নিদেনপক্ষে বর্বর জানোয়ার হিসেবে তুলে ধরা হয়– তা না হলে তাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার যে আর কোনো অজুহাত থাকে না। ক্ষমতাশালীর চোখে আক্রান্তের জমি, বাসা, ভাষা, পরিবার, ইজ্জত, বাঁচার অধিকার–এসবই অপ্রয়োজনীয়, বাড়তি; সে সেগুলোকে নিজের মত কেটেছেঁটে নেয়। শুধু নিজের স্মৃতির ওপর অধিকারটুকু ছাড়া আক্রান্তের হাতে আর কিছুই পড়ে থাকে না, সেই স্মৃতিকেই সে নিজের মনে লালন করে, চারিয়ে দেয় নিজের সন্তানের মনে। প্রজন্মান্তরে, ভাষান্তরে, অনুবাদে, ভিন্ন ভিন্ন আখ্যানে পরম মমতায় আগলে রাখা হয় সেই স্মৃতি, তার সাথে মিশে থাকে ভবিষ্যতের স্বপ্ন, স্বাধীনতার দাবি।
৩
এবার যে প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু করেছিলাম সেখানে ফেরা যাক: স্মৃতিতে যে দেশের ঠিকানা রয়েছে, সেখানে বর্তমানে বা ভবিষ্যতে পৌঁঁছান যেতে পারে কি না সেই সংশয় মানুষের, বিশেষ করে বাস্তুচ্যুত মানুষের অস্তিত্বের অন্তর্লীন সংকট। নাকবার দুই দশকের মাথায় ঘসসান কানাফানির লেখায় সে সংকট ধরা পড়েছিল। তবে আজ তা অন্য চেহারা নিতে বাধ্য। কারণ ফেরা মানে এখন কেবল জলজ্যান্ত হাইফা শহরে সশরীরে প্রত্যাবর্তন করা নয়, স্মৃতি মানেও শুধু বহুকাল আগের অভিজ্ঞতার বিবরণ নয়– প্রত্যাবর্তন ও স্মৃতি– এ দুই-ই ডিজিটাল গণমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে নতুন চেহারা নিয়েছে। আমাদের যাপনকে মুড়ে রেখেছে যে মিডিয়া, যে যন্ত্রের পেটের মধ্যে আমরা সেঁধিয়ে গেছি, তা পৃথিবীর সঙ্গে সত্তা ও স্মৃতির নতুন সংযোগস্থাপন করে, বা বলা ভালো, তাদেরকে গড়েপিটে নেয়। গুগল স্ট্রিটভিউয়ের মত প্ল্যাটফর্ম কি যে-কোনো পরিসরে ‘ইমার্সড’ হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় না? একআঙুলের চাপে আমরা সটান কোনো রাস্তায় সেঁধিয়ে গিয়ে আগুপিছু করে তার চারপাশ ঘেঁটে দেখতে পারি–দাবিটা এমন যেন চলন্ত গাড়িতে বসা যাত্রীর হাতে দূরবিন থাকলে সে এভাবেই তার চারপাশের দুনিয়াকে প্রত্যক্ষ করবে। নাকবার পর ফিলিস্তিন থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে অন্যত্র আশ্রয় নেওয়া অগণিত মানুষের মধ্যে যাঁরা আজও জীবিত, বা তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম–তাঁদের কাছে সেই স্মৃতির ফিলিস্তিনের আজকের হালহকিকত স্বচক্ষে দেখা আরো সহজ হয়ে গিয়েছে স্ট্রিটভিউয়ের দৌলতে। ফিলিস্তিনি শিল্পীরা কিন্তু প্রযুক্তির পরিবর্তনের সঙ্গে স্মৃতি ও ফেরা-র প্রশ্নটির পুনর্বিবেচনা করা থেকে বিরত থাকেননি। স্ট্রিটভিউ-কে ব্যবহার করে স্মৃতিকে ঝালিয়ে নেওয়ার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন রয়েছে রাজান আলসালাহ-র ছবিতে, যার নাম ইওর ফাদার ওয়াজ্ বর্ন হান্ড্রেড ইয়ার্স ওল্ড অ্যান্ড সো ওয়াজ্ দা নাকবা (২০১৭)4।
রাজান আলসালাহ রাজান আলসালাহ ফিলিস্তিনি ও লেবানিজ্ বংশোদ্ভুত পরিচালক5। তাঁর বাবা আর ঠাকুমা নাকবা-র সময় দেশান্তরি হতে বাধ্য হন। আলসালাহ-র জন্ম ১৯৮৭ সালে আবু ধাবি-তে, সেখানে তাঁর বাবা এরোনটিকাল ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। অচিরেই চাকরি হারিয়ে পাততাড়ি গুটিয়ে চলে আসতে হয় আরেক যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ লেবাননে। রাজান আলসালাহ তথ্যচিত্র বানিয়ে কেরিয়ার শুরু করেন, তারপর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে যোগদান। অল্পদিন পরে বিজ্ঞাপন দুনিয়ার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে চলে আসেন যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়ায়, এমএফএ পড়তে। ভিনদেশে পাড়ি দেওয়ার দরুণ যে বিচ্ছিন্নতা ও দেশের প্রতি টান তাঁকে পেয়ে বসেছিল, তাই একের পর এক ভিডিও-তে ফুটে ওঠে। দেশের ছবি তাঁর কাজে ধরা দেয় মূলত স্ট্রিটভিউয়ের মারফত। ডিজিটাল দুনিয়া যে অশরীরী পরিভ্রমণের প্রতিশ্রুতি দেয়, তার সাথে সশরীরে দেশে ফেরার আকাঙ্ক্ষার টানাপোড়েনে স্ট্রিটভিউয়ের সাজানো-গোছানো পরিসর ক্রমশ ভাঙচুর হতে থাকে, তাতে ঢুকে পড়ে অন্য স্মৃতি, চাপা পড়া অতীত, বিজাতীয় শব্দ ও ছবি। আলসালাহ-র নিজের ভাষায়: “The process thus happens through understanding how these images were made and then seeing who is missing in this image, what is missing, what has been disappeared from this image, what is on the outskirts of this image, what is this image hiding, what is in-between.”6 অর্থাৎ ছবির হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াকে খুঁটিয়ে দেখে, তাতে উহ্য এবং প্রান্তিক থেকে যাওয়া মানুষ জীবন ও ইতিহাসের খানাতল্লাশি করতে করতেই আলসালাহ-র কাজ এগোয়। ভিমিও অ্যাকাউন্টে ইওর ফাদার… ছবির বর্ণনা দিতে গিয়ে, আলসালাহ লিখেছেন: ‘Oum Ameen, a Palestinian grandmother, returns to her hometown Haifa through Google Maps Streetview, today, the only way she can see Palestine.’ একটি সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, ওইম আমিন প্রকৃতপক্ষে তাঁর নিজেরই ঠাকুমার নাম,“Oum Ameen is my silent teta, my grandmother” যিনি প্রবাসে কাটানোর সময়ে মৃত্যুর আগে অবধি একটি বারের জন্যেও মুখ ফুটে নাকবার কথা, ফেলে আসা দেশের কথা উচ্চারণ করেননি। আলসালাহ মনে করেন, তাঁর সমস্ত কাজের কার্যকারণসূত্র খুঁজতে হবে এই জাঁকিয়ে বসা নীরবতার মধ্যে। একদিকে যেমন দৈনন্দিন বাস্তব ফিলিস্তিনিদের ওপর ঘটে চলা অবিচারকে খুঁচিয়ে মনে করাতে ছাড়ে না, অন্যদিকে আত্মগ্লানি, সংকোচ ও অপমানবোধে কুঁকড়ে থাকা এক প্রজন্মের নীরবতা সেই বাস্তবকে আরো অসহ্য বৈপরীত্যে ভরিয়ে তোলে। আলসালাহ-র ধারণা, এই নীরবতার নেপথ্যে আছে ফিলিস্তিনি বাস্তুহারাদের গভীর অনুতাপ ও লজ্জাবোধ। জায়নবাদীদের চোখরাঙানি সত্ত্বেও দেশান্তরি হওয়া তাদের সামনে একমাত্র রাস্তা ছিল না– এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে থাকার জন্য তিনি কখনও গ্লানিমুক্ত হতে পারেননি। এই গ্লানিও আদতে ফিলিস্তিনিদের স্বাভিমানকে গুঁড়িয়ে দেওয়ারই কৌশল। নাকবা-র পরে ইজরায়েলের প্রচার করা অজস্র মিথ্যের মধ্যে একটা হল– ফিলিস্তিনি আরবদের-কে কেউ যেচে দেশ ছাড়তে বলেননি, তাঁরা নিজেদের সিদ্ধান্তেই দেশ ছেড়েছেন। অর্থাৎ রীতিমত সন্ত্রাসবাদী অত্যাচার চালিয়ে প্রায় অর্ধেক ফিলিস্তিনিকে দেশত্যাগ করতে বাধ্য করার জ্বলজ্যান্ত সত্যিটা ধামাচাপা পড়ে গেল আরেকটা নির্লজ্জ মিথ্যের তলায়! আলসালাহ যথার্থই মন্তব্য করেছেন, যে এটা আসলে কলোনিয়াল শাসকের আরেক কৌশল, জবরদখলের অর্থনৈতিক আর সামরিক হিংস্রতার ওপর নরম গালচে বিছিয়ে দিয়ে, বাস্তুচ্যুত হওয়ার দায় বাস্তুহারার ওপর চাপানো: “Somehow the brunt of colonial violence is placed on people and the colonial narrative of ‘Yeah they left!’, ‘Yeah we bought a lot of property!’–whether the economic violence or military violence–is kind of dumped on the people. And it was internalised.” এই ছবিতে সেই কুন্ঠাজর্জর নীরবতাকেই তিনি ভাঙতে চেয়েছেন নতুন বয়ানে। তিনি নিজেই ঠাকুমার নাম নিয়ে গোটা ছবি জুড়ে ভয়েসওভার দেন, তাঁর দেশে ফেরার অভিজ্ঞতাকে বর্ণনা করেন। যে দেশকে, যে সময়কে তিনি স্বচক্ষে দেখেননি, তার স্মৃতিকে বিভিন্ন আখ্যান থেকে আত্মস্থ করে তাকে আজকের ইমেজদুনিয়ার সাপেক্ষে নতুন করে পর্যালোচনা করছেন, আবার একইসঙ্গে কল্পনা করছেন নাকবার প্রত্যক্ষদর্শী পূর্বপ্রজন্মের সঙ্গে তাঁর একাত্মতা।
আলসালাহ-র ছবি শুরু হয় গুগল ম্যাপের ইমেজ দিয়ে। সেখানে হাইফার ওপর লোকেশন স্থির–সেখান থেকে সটান ঝাঁপ মারে স্ট্রিটভিউ লেভেলে। ভয়েসওভারে শোনা যায় একজন মহিলার কন্ঠ, ছবির বর্ণনায় যাঁকে ঠাকুমা ওউম আমিন বলে চিনিয়ে দেওয়া হয়েছে, তিনি আরেকজন আমিনের খোঁজে চলেছেন, অথচ আমিনকে উদ্দেশ্য করেই যেন সব কথা বলা। হাইফার সড়ক বেয়ে তিনি এগিয়ে যান, চারপাশের বাড়িঘরের দিকে চেয়ে দেখেন, তাদের ব্যালকনি, জানলার ওপর জুম ইন করে দেখেন সেখানে আমিন-কে দেখা যায় কি না, কিন্তু না। কোনো মহিলাকে হয়তো একনজরে চেনা মনে হয়, কিন্তু তার মুখ স্পষ্ট বোঝা যায় না। রাস্তায় দাঁড়ানো লোকদের উদ্দেশ্য করে কথা বলা এবং তাদের প্রত্যুত্তর না দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে যায় এই তথাকথিত ইমার্শনের অন্তঃসারশূন্যতা। একদম শুরু থেকেই বোঝা যায়, যে ইজরায়েলের দখলে থাকা হাইফার রাস্তাঘাট ফিলিস্তিনের সমস্ত উপসর্গ ঝেড়ে ফেলেছে, বদলে গেছে পথের ধারে ঝোলানো দোকানের নামধাম। স্ট্রিটভিউয়ের অসীম বদান্যতায় পায়ের তলার কংক্রিটের ওপর ভেসে আছে ইংরেজি অক্ষরে রাস্তার নাম–Shivat Tsiyon street, যার প্রথম দুটো শব্দের অর্থ ‘জায়নে প্রত্যাবর্তন’। শিভাত জিয়ন ইহুদী জাতির ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য সন্ধিক্ষণ–কথিত আছে, খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ব্যাবিলন থেকে পারস্য-অভিমুখে যাত্রা করে ইহুদীরা জেরুজালেমে পৌঁছায়, তারপর সেখানে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে–তারই নাম শিভাত জিয়ন। আজকের ফিলিস্তিনের সঙ্গে সেই প্রাচীন ঘটনার নাম জুড়ে দেওয়ার মধ্যে যে পোয়েটিক জাস্টিসের দাবি রয়েছে, সেটাই দেশচ্যুত ফিলিস্তিনি মহিলার চোখে দগদগে শ্লেষ হয়ে ধরা দেয়। স্বদেশ থেকে বিচ্যুতির ওপর নতুন স্তর যোগ হয়–এক, যন্ত্র তার কথা মত সম্পূর্ণ ইমার্শন ঘটাতে ব্যর্থ হয়, স্ট্রিটভিউ-এর ইন্টারফেসে ওউম আমিনের উপস্থিতি সত্ত্বেও শহরের ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মানুষ তার প্রতি নির্বিকার, তারা তার কথার প্রত্যুত্তরও দেয় না। স্ট্যাচু হয়ে যাওয়া মানুষ আর ভ্রাম্যমান অদৃশ্য দর্শকের অস্তিত্বের মধ্যে একটা গুণগত ফারাক প্রকট হয়ে ওঠে। দুই, বদলে যাওয়া শহরের পথঘাট এই পুরোনো বাসিন্দাকে কাছে টেনে নেওয়ার বদলে সরিয়ে দেয় দূরে। আমরা শহুরে আধুনিকতা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রায়শই বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্নতা বা এলিয়েনেশনের কথা বলি। ডিজিটাল এসে কীভাবে তার ওপর কাল্পনিক পরত চাপিয়ে তাকে আড়াল করছে, আবার তলে তলে বিচ্ছিন্নতার বোধকেই বাড়িয়েই চলেছে–সে কথাও বলি। কিন্তু ভুলে যাই এই বোধের মাত্রা দেশকালভেদে ভিন্ন।
আলসালাহ-র ছবিতে এটা অন্তত স্পষ্ট যে ডিজিটাল ইন্টারফেস উদ্বাস্তু মানুষের সঙ্গে ফেলে আসা দেশের কোনো কাল্পনিক একাত্মতা জোগায় না, বরং উদ্বাস্তুর স্মৃতিতে নিবিড় হয়ে থাকা স্বদেশকে বিপন্ন করে নতুন করে। স্ট্রিটভিউয়ের ছবি আদতে অত্যাধুনিক ফোটোগ্রাফিক প্রযুক্তির ফল– অর্থাৎ তাতে যা দেখা যাচ্ছে, তা ছবি তোলার সময়ে ক্যামেরার সামনে থাকার সম্ভাবনাই বেশি, তার সাথে স্ট্রিটভিউয়ের ত্রিমাত্রিকতা যোগ হয়ে বাস্তবতার দাবি আরো তীব্র হয়ে ওঠে। এই তীব্র হয়ে ওঠা বর্তমানের বাস্তব, যা আগাগোড়া আনক্যানি, তা স্মৃতির স্বদেশের চিরতরে মুছে যাওয়ার সত্যকে আরো মর্মান্তিক, অসহনীয়, এবং একই সঙ্গে অনস্বীকার্য করে তোলে। স্মৃতিকে জিইয়ে রাখে যে ভবিষ্যতের স্বপ্ন, চেনা পৃথিবীতে ফিরে যাওয়ার স্বপ্ন, তাদেরকে আরো অসম্ভাব্যতার দিকে নিয়ে যায়।
এর পাশাপাশি আলসালাহ সেই স্ট্রিটভিউয়ের ছবির ওপর যে কারিকুরি করছেন সেগুলোও খতিয়ে দেখা দরকার। ভয়েসওভারে যে মহিলার কন্ঠ শোনা যায়, যিনি কিনা একজন ফিলিস্তিনি ঠাকুমা–তাঁর কন্ঠে বার্ধক্যের লেশমাত্র ছোঁয়া নেই (আগেই বলেছি, আলসালাহ নিজে কন্ঠ দিয়েছেন), বরং তা কোনো তরুণীর শরীর থেকে বেরিয়ে আসছে এমন মনে আসাটাই স্বাভাবিক। অর্থাৎ এই ফিরে যাওয়ায় শরীর আর কন্ঠের মধ্যেও বিযুক্তি ঘটে গেছে। আজকের মিডিয়া, আজকের ছবি, আজকের পৃথিবীতে ঢুকে প্রৌঢ়া ওউম আমিনের কন্ঠ মনে করাচ্ছে ১৯৪৮ সাল, বা তারও আগের এক তরুণীর শরীরকে, কিন্তু সে পুরোমাত্রায় উপস্থিত এই বর্তমানে7। দ্বিতীয়ত, হাইফার সড়ক বেয়ে চলার সময় বা বন্দরের কাছে এসে যখন ওউম আমিনের পুরানো স্মৃতি ফিরে আসে, তখন স্ট্রিটভিউ-এর ইমেজের ওপর ভেসে ওঠে সে-সব লোকেশনের গত শতাব্দীর প্রাচীন সাদা কালো ফোটোগ্রাফ। নিউ মিডিয়ার ওপর ক্ষণিকের জন্য লেপটে থাকা প্রাচীন মিডিয়ার অবশেষ, যা অতীতের লক্ষণা (মেটোনিমি) এবং রূপক (মেটাফর) – দুই-ই। তৃতীয়ত, ছবির শেষে এসে কয়েক সেকেন্ডের জন্য আমিনের চোখ (নাকি কার্সর?) ঝট করে নেমে আসে বন্দরের জেটিতে: দেখা যায় সেখানে কয়েকটি বাচ্চা ট্রাইসাইকেল চালাচ্ছে, যদিও তাদের কারোর মুখই স্পষ্ট বোঝা যায় না। একজনের ওপর জুম ইন হয়, ভয়েসওভার তাকে আমিন বলে শণাক্ত করে, তারপর চোখ সরে যায় একটু দূরে, পাশের বাচ্চাটির ওপর, এবার তার উদ্দেশ্যে ‘আমিন’ ডাক শোনা যায়। তারপর আবার একটু দূরে, আরেকটি বাচ্চার ওপর, সেও ট্রাইসাইকেল চালাচ্ছে, এবং তাকেও ওউম আমিন স্নেহভরা গলায় আমিন বলে ডাকে। অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া প্রতিটি শিশুর মুখে যেন হারিয়ে যাওয়া আমিনের ছায়া রয়েছে।
যে তিনটি দৃষ্টান্ত তুলে দিলাম, তাতে একটা জিনিস পরিষ্কার– আলসালাহ কালের সরলরৈখিক প্রগতির বিকল্প একটি কালপ্রতিমা তুলে ধরতে চাইছেন, তা না হলে প্রৌঢ়ার শরীর থেকে তরুণীর কন্ঠ বেরোতে পারে না, স্ট্রিটভিউয়ের ওপর সেলুলয়েড ইমেজের প্রেত ফিরে আসতে পারে না, এমনকি প্রায় আট দশক আগে হাইফায় ফেলে আসা শিশুটিকে সন্ধান করতে এসে তাকে আজকের শিশুর মধ্যে আবিষ্কার করা–তাও অসম্ভব। এটা স্মৃতির বিপন্নতার উপসর্গ। স্মৃতি আর অতীতের ঘটনার নিরাপদ আধার থাকে না, স্ট্রিটভিউয়ের ইন্টারফেসের ভিতর দিয়ে দেখা বীভৎস আনক্যানি শহর স্মৃতির আবরণ কেটে অতীতের লক্ষণাগুলিকে বের করে আনে; বর্তমানকে অতিক্রম করে ভবিষ্যতে সঞ্জীবিত হওয়ার যে আশা স্মৃতিতে দ্যুতিময় হয়ে ছিল, তার সামনে দাঁড়ি টেনে দেওয়ার চেষ্টা চালায়। স্বাধীন ফিলিস্তিনের স্বপ্নের সামনে মিডিয়ার জঠরে থাকা এই বাস্তব হয়ে দাঁড়ায় প্রতিবন্ধকতা, প্রায় অনতিক্রম্য এক প্রাচীর।
প্রায় অনতিক্রম্য। ছবির শেষে, সূর্যাস্তের আলো-মাখা ভাঙাচোরা সমুদ্রের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে, দিগন্তে বিলীয়মান জাহাজের দিকে চেয়ে ধীরকন্ঠে ওউম আমিন বলেন, ‘আমায় ফিরতেই হবে। বেহেস্তে যাওয়ার আগে ফিরতেই হবে আমায়।’ শেষ বাক্যটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই একটা অন্ধকার আকাশ থেকে নেমে এসে ফ্রেমটাকে গিলে নেয়। স্ট্রিটভিউয়ের সীমান্তে পৌঁছানোর পর, সমুদ্র এবং আকাশ চিড়ে যন্ত্রের ফাটা খোল থেকে বেরিয়ে আসে অন্ধকার, পোশাকি ভাষায় যাকে গ্লিচ বলে। মিডিয়া-প্রসূত বাস্তবের পরপারে যে আঁধার, যাকে এখনও সিনেমা বা স্ট্রিটভিউ– কেউই দেখতে পায়নি, তার দ্যোতনা অসীম; একদিক থেকে দেখলে তা অনির্দেশ্যতার দ্যোতক। আলসালাহ সে অর্থে একজন বিষণ্ণ তবু বাস্তববোধসম্পন্ন পরিচালক: তিনি যন্ত্রের জঠরে থাকা ফিলিস্তিনের কোনো উত্তরণ স্বপ্ন দেখাননি, কিন্তু তার কফিনে পেরেক পড়ে গেছে–এমন নৈরাশ্যজনক সিদ্ধান্তেও পৌঁছাননি। যন্ত্র চাক্ষুষ করাচ্ছে কীভাবে ফিলিস্তিনকে ঢেলে সাজিয়েছে ইজরায়েল, যেন ১৯৪৮-এর আগে তার কোনো অতীত ছিল না! এক যৌথ ষড়যন্ত্রে ফিলিস্তিনিদের স্বপ্নের সামনে তুলে দেওয়া হয়েছে আকাশজোড়া পাঁচিল8। কিন্তু সমুদ্রের সীমান্তে এসে এই বাস্তবও চিড় খায়। সেই চিড় খাওয়া বাস্তবের সামনে নেমে আসা আঁধার ওউম আমিনের দৃষ্টির শুশ্রূষা করবে, তার স্মৃতিকে লালন করার অবকাশ দেবে নতুন শক্তিসঞ্চয় করে আবার ফিরে আসার আগে।
এই ছবিটি নিয়ে বলতে গিয়ে আলসালাহ মন্তব্য করেন, ‘What return looks like as a structure is unknown’, ফেরার ধরণটা ঠিক কী, তা আজও অজানা। কিন্তু তিনি এও জানান, যে নেশন-স্টেট নামক কাঠামোটিতে তাঁর কোনো আস্থা নেই, এবং ফিলিস্তিন নিয়ে কোনো জাতিরাষ্ট্র-নির্ভর রোম্যান্টিকতায় মজে থাকাও তাঁর কাছে অসহ্য, কারণ জাতিরাষ্ট্রের কাঠামো অনেকটা ক্লাব আর কাল্ট-এর মত; তাতে ঢুকে পড়া মানেই নতুন বিভাজনের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়া, আমরা-ওরা, আমার-তোমার— এসব জল-অচল খোপে আটকা পড়ে যাওয়া; তিনি স্পষ্ট বলে দেন, ‘Palestine is not a nation-state project’। গর্ব প্রকাশ করে বলেন, ফিলিস্তিন সেসব মানুষের জন্য, এককালে যাঁদের জাতিরাষ্ট্রের অধিকারকে অস্বীকার করা হয়েছে, এবং যারা স্বয়ং সেই ‘জাতিরাষ্ট্র’ নামক ক্লাব বা কাল্টটিকে প্রত্যাখ্যান করে ফেরা ও মিলেমিশে থাকা-র আনকোরা এক আঙ্গিকের জন্ম দেবে। সুতরাং আজকাল দুনিয়া জুড়ে দক্ষিণপন্থীরা যে অতীতে ফিরে যাওয়ার ডাক দিচ্ছেন, তার সাথে ফিলিস্তিনি প্রত্যাবর্তনের দাবি ও তার স্মৃতির রাজনীতির আকাশ পাতাল তফাৎ। প্রথমটাতে উদ্দেশ্য হল জাতিরাষ্ট্রের ভিত আরো মজবুত করা, সোনালি অতীতের ধুয়ো তুলে তাকে ট্রাইবে পরিণত করা, যা আসলে যৌথ পরিবারেরই বৃহত্তর রূপ, কারণ সেখানে প্রত্যেক সদস্য এক বর্ণের, একই ধর্মের, একই ব্লাডলাইনের অংশ; অতএব সেখানে অতীতের নির্মাণও হয় খুব ছক কষে, রোম্যান্টিকতার আরকে মজিয়ে। অপরদিকে, আলসালাহ-র কাজে যে ফিলিস্তিনের সম্ভাবনা ও দাবি চাপাস্বরে নিজেদের জানান দেয়, তা শুধু একটি ভূখন্ডে স্বায়ত্তশাসন কায়েম করা নয়, বরং জাতিরাষ্ট্রের কাঠামোকে ভেস্তে দিয়ে, আমরা-ওরার বিভাজনকে অবিন্যস্ত করে এক নতুন ভবিষ্যত নির্মাণ করা। কানাফানির গল্পের নায়ক সইদের উক্তি একটু রদবদল করে নিয়ে বলতে হয়, স্বদেশ মানে তাই, যেখানে কেউ-ই অপর হয়ে যায় না। এখানে স্মৃতি ও অতীতের ভূমিকা ভিন্ন, বা বলা ভালো, এখনও অস্পষ্ট, তা একটি সতত পরিবর্তনশীল ও জটিল প্রক্রিয়ার সচেতন অংশ। অর্থাৎ ওউম আমিনের ফেরার যে পৌনঃপুনিকতার আভাস তাঁর শেষ সংলাপে রয়েছে, তার ব্যঞ্জনা শুধু বারবার ফেরায় সীমিত থাকে না। তার অর্থ নতুন করে নতুন পথে ফেরা9, যাতে অতীতের স্বদেশ ও ভবিষ্যতের স্বপ্নের ফারাক ও সাযুজ্যকে একটু একটু করে চিনে নেওয়া যায়। জাতিরাষ্ট্রের ক্রমশ স্থিতিশীলতার দিকে একমাত্রিক অভিযাত্রার যে আঙ্গিক, তার পরিবর্তে একটি অসমসত্ত্ব ও জটিল পুনরাবৃত্তিময় কালিক চেতনার আভাস দেওয়ার মাধ্যমেই আলসালাহ-র ছবি শেষমেশ হয়ে ওঠে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে এক অজানা ভবিষ্যতের দিকে কন্টকবিদীর্ণ পথে যাত্রার রূপক।
৪
স্মৃতি তো অতীতের আঁকাড়া স্মরণ নয়। স্মৃতি আসলে অতীতকে আখ্যানে পরিণত করার প্রক্রিয়া–তার সাথে জড়িয়ে আছে ভবিষ্যতে ন্যায়ধর্ম প্রতিষ্ঠার আশা। সংকটের মুখে নির্মম আশাবাদকে জিইয়ে রাখার অন্যতম উপাদান হল স্মৃতি। মিডিয়া প্রযুক্তি সেই স্মৃতিকে মানুষের মগজ থেকে বেরিয়ে ছবি, শব্দ, লেখা প্রভৃতিকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকার সুবিধে করে দেয়। রাজান আলসালাহ-র কাজে গুগল স্ট্রিটভিউয়ের দুনিয়ায় সেই মিডিয়া-বিধৃত স্মৃতির বিপন্নতাই ফুটে ওঠে। এককালের চেনা দেশ কীভাবে ক্রমশ ডিজিটাল মিডিয়ায় হারিয়ে যায়, চেখের সামনে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখে স্মৃতি ও আশাভরসা সবই যে আহত হয়, তা সেখানে স্পষ্ট। ঠিক যেমন এই মুহূর্তে দুনিয়াজুড়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে গাজায় ইজরায়েলি সৈন্যের নাশকতার ছবি, জায়নবাদী যোদ্ধা, জনতা ও নেতানেত্রীদের নারকীয় জয়োল্লাসের ক্লিপ, শক্তিশালী মিসাইল-হানার পর গাজার ধ্বংসস্তূপের ড্রোন ভিডিও। গাজায় বসবাস করা মানুষদের জীবন, সম্পত্তি, অধিকারের পাশাপাশি, গোটা পৃথিবীর মানুষের কাছে ইজরায়েল বার্তা পাঠাচ্ছে যে ফিলিস্তিনের শেষ এখানেই; নেতানিয়াহু হুংকার ছেড়ে বলছে, “ইজরায়েল যা প্রতিক্রিয়া দেখাবে, তা গোটা মধ্যপ্রাচ্যকে বদলে দেবে। আগামী কয়েক দিনে আমরা শত্রুদের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা নেব, তার স্মৃতি তাদের কয়েক প্রজন্ম ধরে তাড়া করবে।”10 অর্থাৎ ১৯৪৮ সালের আগের ফিলিস্তিন নয়, বা অটোমান শাসনাধীন পরধর্মসহিষ্ণু, বিভিন্ন জাতির সহাবস্থানের ফিলিস্তিন নয়– ইজরায়েলের এই ধ্বংসলীলার ছবিই হয়ে উঠবে আগামী প্রজন্মের কাছে ফিলিস্তিনের একমাত্র স্মারকচিহ্ন।
কিন্তু সেই আস্ফালনের মুখে চুনকালি দিয়ে উল্টোদিক থেকে উঠে আসছে প্রতিস্পর্ধী কন্ঠ। আকাশ থেকে বোমা পড়ার ভয়কে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে, সোশাল মিডিয়া বিশেষত ইন্স্টাগ্রামের অসংখ্য সংবাদদাতা ও ইউজার গাজা, ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক এবং মিশর, জর্ডন প্রভৃতি প্রতিবেশী দেশের শরণার্থী শিবির থেকে বানিয়ে চলেছেন একের পর এক ভিডিও। তাতে দেখা যাচ্ছে– চারপাশের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে তাঁরা বাজারে যাচ্ছেন, বেশি দাম দিয়ে রুটি কিনছেন, ঈদের আয়োজন করছেন, পাড়াপড়শির সঙ্গে গান গাইছেন কোনো তাঁবুর ছাওয়ায় বসে। কিছু ভিডিও-তে দেখি, শরণার্থী শিবিরের আশেপাশে ফাঁকা জমি পেয়ে সেখানে অনেকে মেতে উঠছেন বিভিন্ন খেলায় (বিশেষ করে parkour)। তাঁদের সহজ সরল দেহভঙ্গিমা, দেহকে অস্বাভাবিক উচ্চতায় ছুঁড়ে দিয়ে কিছুক্ষণ বাতাসে ভেসে থাকার পর আবার নিরাপদে মাটিতে নেমে আসার সাবলীলতা— এসব যেন বর্তমানের একবগ্গা পুনরাবৃত্তিকে ছাপিয়ে গিয়ে, মৃত্যু আর কোনো মতে বেঁচে থাকার বাঁধা ছককে ভেঙে, এক অনন্য শরীরী অস্তিত্ব কল্পনা করতে বদ্ধপরিকর11।
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অগণিত সোশাল মিডিয়া ইউজারের কাছে উঠে আসছে অন্য ফিলিস্তিনের ছবি। অনবরত ধ্বংস আর মৃত্যুর প্রতিবেদন দেখে শুনে ক্লান্ত হতাশ হয়ে ওঠা প্রাণে তাঁরা পুঁতে দিচ্ছেন নতুন আশার বীজ। পৃথিবী জুড়ে ফিলিস্তিনের সপক্ষে এবং ইজরায়েল ও তার বন্ধুরাষ্ট্রদের বিরুদ্ধে যে জনমত গড়ে উঠেছে, তাকে অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছেন। সে-সব ভিডিও ঘিরে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে লাইক, কমেন্ট, উচ্ছ্বাস আর অভিনন্দনের যে ঢল নামে, যে সংহতির ভিত গড়ে ওঠে, তা আসলে রাজান আলসালাহ-র প্রত্যয়কেই আরো দৃঢ়তা দেয়: ফিলিস্তিন কোনো জাতিরাষ্ট্রের একক প্রকল্প নয়, তা একটি বিশ্বজনীন প্রকল্প– বিশ্বজোড়া নিপীড়িত বাস্তুচ্যুত মানুষ আর তাঁদের পাশে দাঁড়ানো জনগণের উপনিবেশ, সাম্রাজ্য ও পুঁজিবাদ-বিরোধী সংগ্রামের অপর নাম। তাঁদের স্মৃতি ও স্বপ্নের জোগান কোনোদিনই ফুরোবার নয়।
শিরোনামের ‘যন্ত্রের জঠর’ শব্দবন্ধটি রোববার পোর্টালে প্রকাশিত অধ্যাপক অনিন্দ্য সেনগুপ্তের একটি সাম্প্রতিক নিবন্ধ থেকে নেওয়া। এখানে মানে প্রায় এক থাকলেও আমি একটি অন্য তাৎপর্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। অধ্যাপক সেনগুপ্ত যন্ত্রের পেট বলতে এখনকার ডিজিটাল মিডিয়া আর তার ইন্টারফেস-কে বুঝিয়েছেন; হাতের মুঠোয় ধরা স্মার্টফোনের হরেকরকমবা-এ মজে থাকতে থাকতে ইউজারের সত্তা সাময়িকভাবে যে আপাত পরিপূর্ণতা-র আরাম পায় সেদিকটায় জোর দিয়েছেন। আমি দেখাতে চাইছি যে ইউজার-বিশেষে এর সম্পূর্ণ বিপরীত প্রতিক্রিয়া সম্ভব, অর্থাৎ যন্ত্রের পেটে ঢুকে বিচ্ছিন্নতাবোধ সাময়িকভাবে লাঘব হওয়ার পরিবর্তে আরো তীব্র হয়ে উঠতে পারে।
অনিন্দ্য সেনগুপ্ত, “চার্লির মত আমরাও কিন্তু যন্ত্রের পেটেই আছি” রোববার ডিজিটাল, ১৬ই এপ্রিল ২০২৪. https://robbar.in/daily-update/charlie-chaplins-modern-times-and-our-modern-times/.
- হাইফায় ফেরা-র সব কটি উদ্ধৃতি ক্যারেন রাইলি-কৃত ইংরেজি ভাষান্তর অনুসারে তরজমা করেছি। Ghassān Kanafānī, “Returning to Haifa” in Palestine’s Children : Returning to Haifa and Other Stories, trans. Barbara Harlow and Karen E. Riley. (Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 2000), 149-188.
↩︎ - অর্ক ভাদুড়ি, “ইজরায়েলের গাজা আক্রমণ যুদ্ধ নয়, সুপরিকল্পিত গণহত্যা”, নাগরিক.নেট, ২০ অক্টোবর ২০২৩.https://nagorik.net/politics/international-politics/israel-is-not-in-war-it-is-carrying-out-well-planned-genocide/.
Ilan Pappe, “Palestine: Endless Occupation, Permanent Crisis”, Marxist XXXIX, no. 3-4, (July-December 2023): 10-32. ↩︎ - “Israel MK calls for a second Nakba in Gaza”, Middle East Monitor, October 9, 2023
https://www.middleeastmonitor.com/20231009-israel-mk-calls-for-a-second-nakba-in-gaza/. ↩︎ - ছবিটি আমার নজরে আনার জন্য ধন্যবাদ বন্ধু খুশবু ভুটানি-কে। খুশবু পিটসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিলিস্তিনি ছবি নিয়ে গবেষণা করছেন, এ-বিষয়ে সে আমার চেয়ে অনেক সুচিন্তিত অভিমত দিতে পারবে। সম্প্রতি রাজান আলসালাহ-র কাজে প্রত্যাবর্তনের ব্যঞ্জনা ও প্রযুক্তির ভূমিকা নিয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে ফিল্ম-ফিলোসফি জর্নালে, আগ্রহ থাকলে পড়ে দেখতে পারেন। Samira Makki. “Even the Sea is Broken: Return and Loss in Razan AlSalah’s Video Works,” Film-Philosophy 28, no. 2 (June 2024):248-268.
এখানে বলে রাখি, ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে স্ট্রিটভিউ ও স্মৃতির রাজনীতি নিয়ে কাজ করার চমৎকার উদাহরণ হল সুনীল সানজ্গিরি-র ছবি। তার নাম Letter From Your Far-Off Country (2021)।
↩︎ - https://razanalsalah.com/info ↩︎
- Shahrzad Arshadi and Caroline Kunzle. ‘Conversation With Razan Al-Salah’. Future is Now (podcast), July 20, 2022 (accessed May 13, 2024)
https://podcasters.spotify.com/pod/show/future-is-now-podcast/episodes/Conversation-With-Razan-Al-Salah-e1lffdl. ↩︎ - শব্দ সবসময়ই আংশিক বা খন্ডিত। উৎস থেকে নাড়ি ছিঁড়ে বেরিয়ে এসে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অস্তিত্ব দাবি করা তার পক্ষে অসম্ভব। ঠুংঠাং শব্দ শুনলে আমরা তৎক্ষণাৎ ধরে নিই সেটা পেয়ালা পিরিচের ঠোকাঠুকির শব্দ। ঠুংঠাং, মচমচ, ধপাস, গুরুম্, টাপুরটুপুর –এদের কোনো নিজস্ব অস্তিত্ব নেই। একই ভাবে, কন্ঠস্বরও কখনও সম্পূর্ণ বিদেহী হয়ে উঠতে পারে না, কারণ তা শোনা মাত্র তার উৎস অর্থাৎ একটি জলজ্যান্ত শরীর নিজের অস্তিত্ব জানান দিয়ে ওঠে। আমরা শুধু সেই ব্যক্তিবিশেষের বাগযন্ত্র নয়, তার বয়স, রূপ, অভিজ্ঞতা ইত্যাকার বিশেষত্ব মনে মনে কল্পনা না করে পারি না। স্টিভ কনর এর নাম দিয়েছেন ‘ভোকালিক বডি’ বা স্বরসৃষ্ট শরীর। Steven Connor, ‘What I Say Goes’ in Dumbstruck: A Cultural History of Ventriloquism (Oxford, 2000), 3–44. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198184331.003.0001, accessed 13 May 2024. আরো দ্রষ্টব্য, Christian Metz, “Aural Objects.” trans. Georgia Gurrieri, Yale French Studies 60 (1980): 24–32. https://doi.org/10.2307/2930002. ↩︎
- এখানে বলে রাখা দরকার, গুগল আর ইজরায়েলের যৌথ ষড়যন্ত্র বললে কিছুই বাড়িয়ে বলা হয় না। ইজরায়েলকে সার্ভেলেন্স প্রযুক্তি জোগানোর জন্য গুগল চালু করেছে প্রোজেক্ট নিম্বাস, তাতে বিপুল অনুদান জোগাচ্ছে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি। এ-কাজে তার স্যাঙাত অ্যামাজন। প্রোজেক্ট নিম্বাসের অনেক অসাধু উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি হল– ড্রোন ও সিসিটিভি ক্যামেরায় ফিলিস্তিনিদের আচরণ-অভিব্যক্তি বিচার করে তাদের ‘প্রকৃত অভিসন্ধি’ ঠাহর করা (সেন্টিমেন্ট অ্যানালিসিস)। দুই টেক-প্রতিষ্ঠানের ভিতরেই একদল কর্মী এই প্রোজেক্টের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। তেইশে এপ্রিল অবধি যা খবর সে অনুযায়ী শান্তিভঙ্গের অপরাধে গুগল তার ৫০ জন আন্দোলনরত কর্মীকে ছাঁটাই করেছে।
Sam Biddle. “Documents Reveal Advanced AI Tools Google Is Selling to Israel”. The Intercept, July 24, 2022 (accessed May 18, 2024).
↩︎ - ফিলিস্তিনের প্রেক্ষিতে প্রত্যাবর্তনের রাজনীতি সম্বন্ধে আরো বিশদ আলোচনা-র জন্য দ্রষ্টব্য, Rayya El Zein, “To have many returns: Loss in the presence of others”, World Records, 4 (2020): 41–54. ↩︎
- অর্ক ভাদুড়ি, “ইজরায়েলের গাজা আক্রমণ যুদ্ধ নয়” ↩︎
- সঙ্গের স্ক্রিনশটগুলি Bisan Owda (wizard_bisan 1) আর amirgharabawi-র ইন্স্টাগ্রাম প্রোফাইল থেকে নেওয়া
https://www.instagram.com/wizard_bisan1/?hl=en.
https://www.instagram.com/amirgharabawi/. ↩︎
- হাইফায় ফেরা-র সব কটি উদ্ধৃতি ক্যারেন রাইলি-কৃত ইংরেজি ভাষান্তর অনুসারে তরজমা করেছি। Ghassān Kanafānī, “Returning to Haifa” in Palestine’s Children : Returning to Haifa and Other Stories, trans. Barbara Harlow and Karen E. Riley. (Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 2000), 149-188.
-
অন্দরে সন্ত্রাসঃ গ্যাংস্টার জঁর ও মাইসেলফ অ্যালেন স্বপন
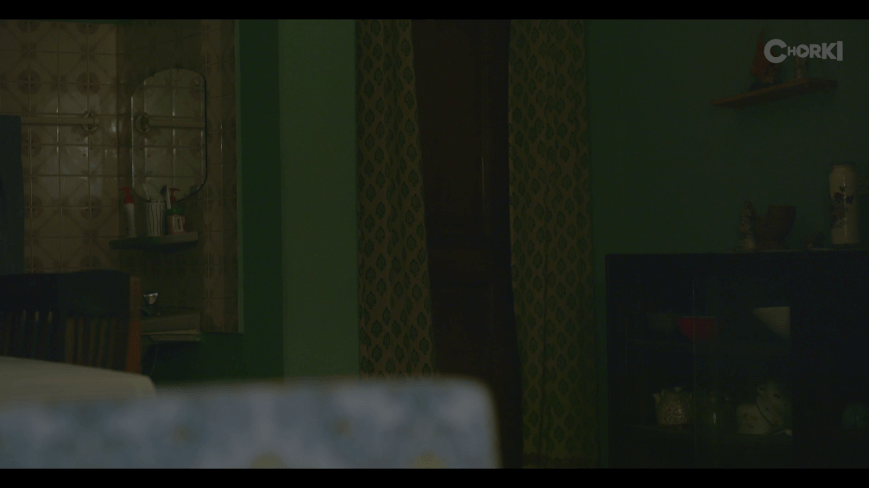
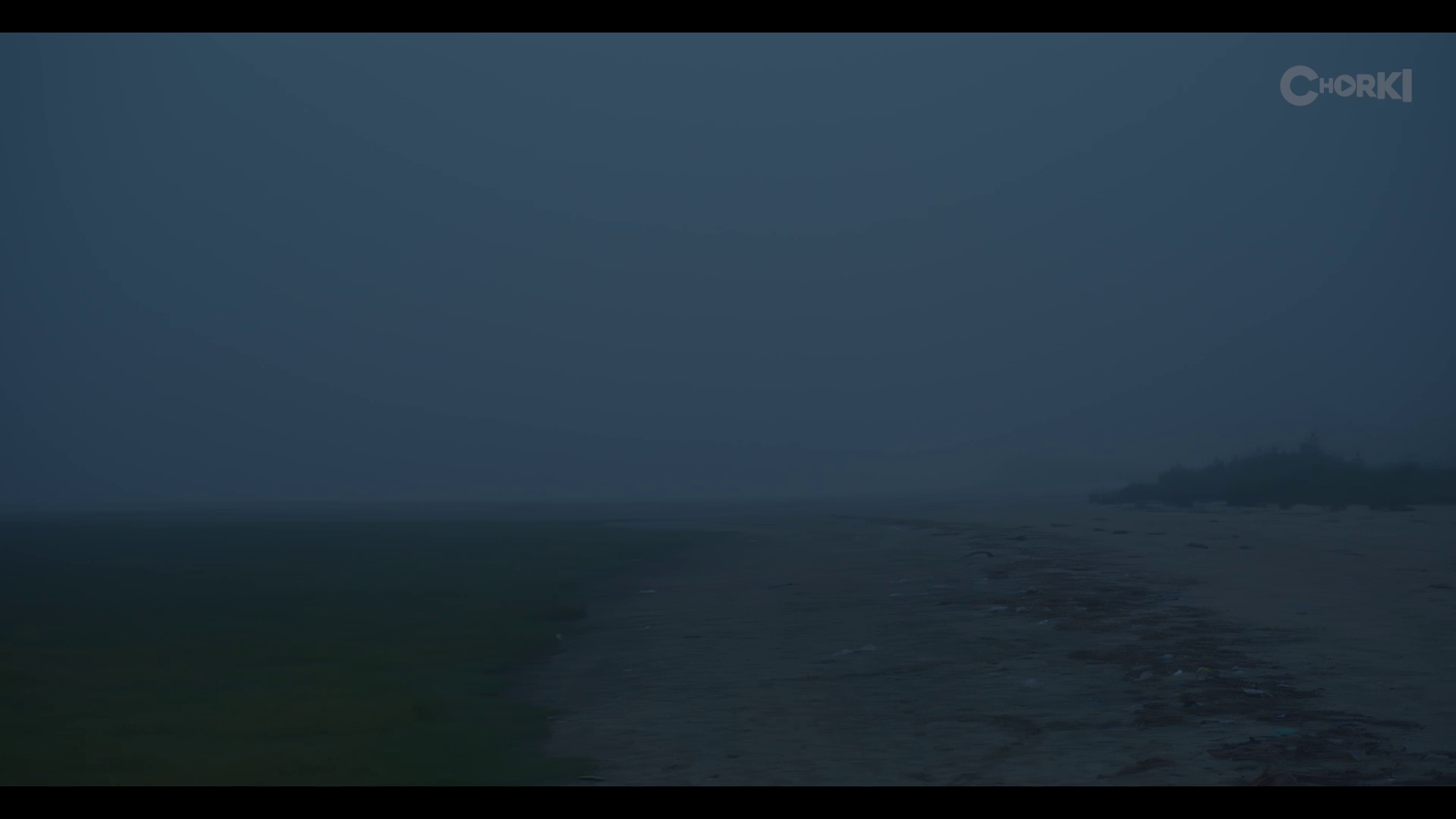
ধূ ধূ নীল জলাভূমি, দিগন্তরেখায় মিশে গেছে আকাশ মাটি আর সমুদ্র। বেশ ধীর গতিতে ক্যামেরা প্যান করছে। আদিগন্ত নীল আকাশ, জল, আর সবুজ ঘাসজমির কানাকানি দেখতে দেখতে প্রথমে আমরা বুঝতেই পারি না, দূরে কখন যেন অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে একটি বা দুটি নৌকার আকৃতির কিছু। স্ক্রীনে ততক্ষণে টাইটেল পড়ে গেছে – কক্সবাজার, ২০১৮। আমরা যারা বাঙালি অথচ বাংলাদেশে থাকি না, তাদের কাছে এই কক্সবাজার নামটি নানান বিচিত্র অনুষঙ্গ নিয়ে আসে – আমার ক্ষেত্রে যেমন মনে পড়ে যায় শক্তি চট্টপাধ্যায়ের কক্সবাজারে সন্ধ্যা কাব্যগ্রন্থের কয়েক লাইন। “নিরবয়ব মূর্তি তার, নদীর কোলে জলাপাহার / বনতলের মাটির ঘরে জাতক ধান ভানছে”। কিন্তু নীলাভ এই আলো যতই কবিতার অনুষঙ্গ নিয়ে আসুক না কেন, শব্দের ট্র্যাকে ততক্ষণে আমরা শুনতে পাই, শুরু হয়ে গেছে অশুভ এক ইঙ্গিত। মন্দ্র সপ্তকে গম্ভীর ধ্বনিতে চলতে থাকা আবহ সঙ্গীত আমাদের জানিয়ে দেয় খুব দ্রুত কিছু না কিছু অঘটন ঘটতে চলেছে।
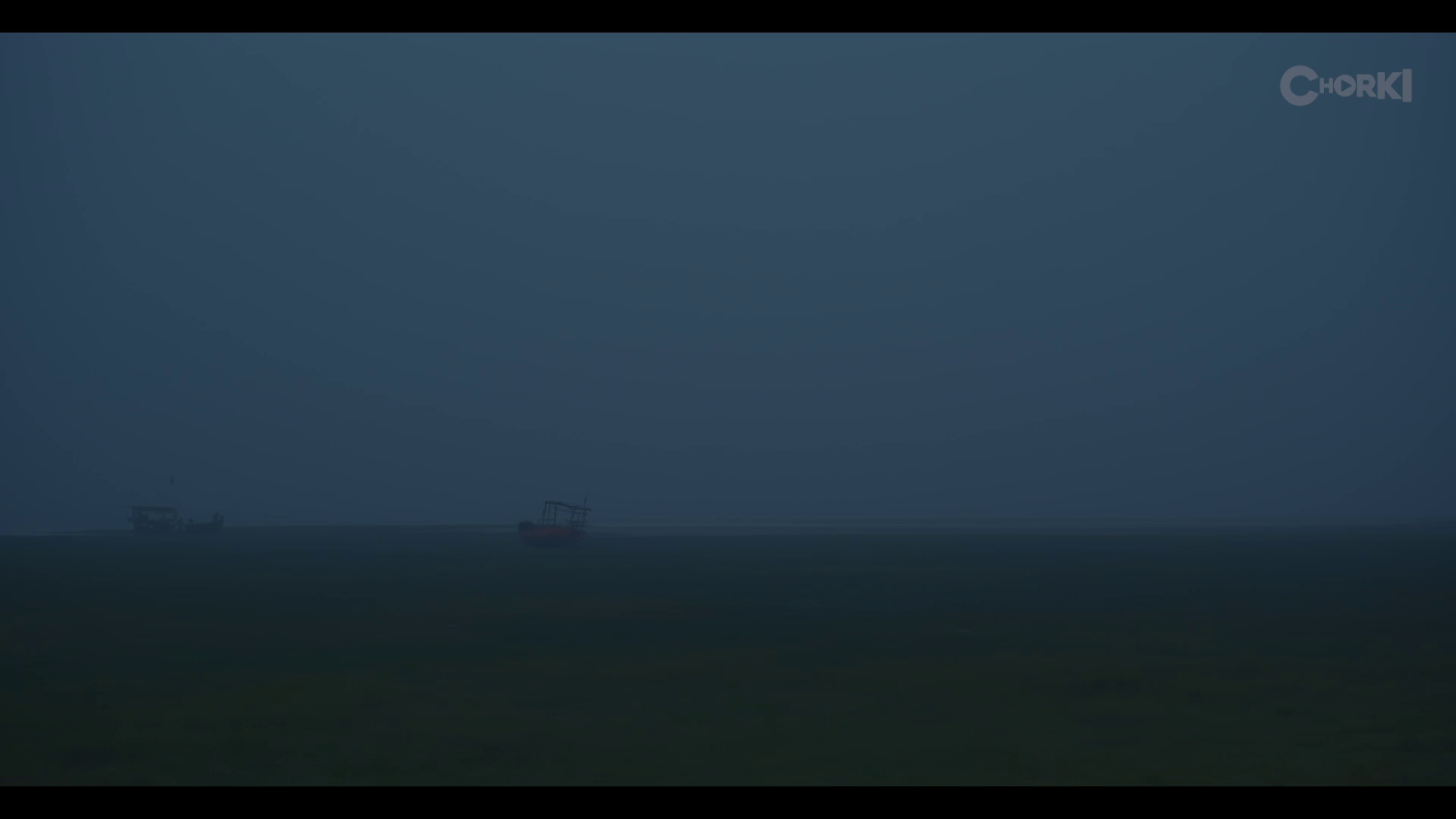
বাংলাদেশের ‘চরকি’ নামক প্ল্যাটফর্মে গতবছর মুক্তি পাওয়া মাইসেল্ফ অ্যালেন স্বপন (২০২৩) সিরিজটি শুরু হয় খানিকটা এইভাবে। ফুটতে থাকা ভাতের হাঁড়ির একটিমাত্র চাল টিপলেই যেমন চাল থেকে ভাত হয়েছে কীনা বোঝা যায়, তেমনই, শুরুর এই দুই তিনটে শটেই সিরিজের নির্মাতারা বুঝিয়ে দেন, চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা, অভিনয় ইত্যাদি চলচ্চিত্রের প্রাথমিক ক্রাফটের দখলে উন্নতমানের মুড নির্মাণে তাঁরা অত্যন্ত দক্ষ। সিরিজ শুরু হচ্ছে – শুধু গল্পে বা সংলাপেই ঘটনার বর্ণনা নয়, বরং শব্দ এবং দৃশ্য সম্বলিত চিত্রভাষা ব্যবহারের দক্ষতায় ঘনিয়ে আসা বিপদের ইঙ্গিতে দর্শকেরা টানটান হয়ে বসেন। নৌকা থেকে লাফ দিয়ে নামে একটি চরিত্র, ক্যামেরা মিড শটে তাকে ফলো করতে করতেই পিছন থেকে নৌকার অন্য যাত্রীদের কথাবার্তা শোনা যায়। কলকাতা কিংবা ঢাকার প্রমিত বাংলায় অভ্যস্ত দর্শকের জন্য স্ক্রীনে সাবটাইটেল আসে – একটু চমকে উঠলেও আমরা বুঝতে পারি, পিছনের সমস্ত কথা হচ্ছে চট্টগ্রামের ভাষায়, যার অধিকাংশটাই আমাদের পক্ষে বুঝে ওঠা সম্ভব নয়।
এই লেখায় আমরা মাইসেল্ফ অ্যালেন স্বপন সিরিজটির বিশেষ একটি দিক নিয়ে কথা বলব – কিন্তু সেটা করার জন্য আমাদের সিরিজের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ স্পয়েলারটি দিয়ে দিতেই হবে। তাই যাঁরা সিরিজটি এই লেখা পড়ার আগে দেখেননি, তাঁরা লেখাটি এরপর থেকে পড়লে কাহিনির অত্যন্ত জরুরি একটি উন্মোচন সম্পর্কে আগে থেকে জেনে যাবেন। তাই আগে সিরিজটি দেখে নিয়ে তারপর লেখার বাকি অংশে এগোলে পাঠক এবং লেখক – উভয়ের জন্যই সুবিধের হয়।
******

সিরিজ শুরুর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা বুঝতে পেরে যাই – আমরা একটি গ্যাংস্টার জঁরের সিরিজ দেখছি। অ্যালেন স্বপন নামের বাংলাদেশের এক মাদক পাচারকারী হঠাৎই বিপদে পড়ে যায় সরকারি ভাবে পুলিশের রেড শুরু হতে। কক্সবাজারে তার নৌকো ভেড়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই বন্দুক হাতে উর্দিধারীরা ওই নৌকোর দিকে ধেয়ে যায় – আর স্বপন জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে প্রাণ বাঁচানোর জন্য। পুলিশের রক্তচক্ষু থেকে পালিয়ে একের পর এক ফাঁড়া টপকে কীভাবে সে এক পোড়োবাড়ির মধ্যে আশ্রয় নেয়, সেই আখ্যান সিরিজে যারা দেখেছেন, নিশ্চয়ই তাঁদের স্মৃতিতে আছে – আমি ভাষায় বর্ণনা করে তার রস লঘু করে দিতে চাই না। প্রথম এপিসোডের প্রায় গোটাটাই এই পালাই-পালাই করতে করতে একদম শেষ মুহূর্তে আমরা হঠাৎ দেখি, এক আগন্তুক পুলিশে ফোন করে মৃত স্বপনকে ধরিয়ে দিতে চাইছে। দর্শককে চূড়ান্ত অবাক করে দিয়ে এই আগন্তুক যখন পিছন ফেরে, দেখা যায় সেও হুবহু স্বপনের মতোই দেখতে – শুধু পোশাক এবং চুলদাড়ির ছাঁচ আলাদা। দ্বিতীয় এপিসোডের শুরুতেই এই রহস্য সমাধান হয় – আমরা জানতে পারি স্বপনের এক যমজ দাদা আছে যে ঢাকা শহরেই একটি ছোটোখাটো ইনশিওরেন্স কোম্পানির ম্যানেজার। স্বপন বিপদে পড়ে কায়দা করে দাদাকে তার ডেরায় টেনে আনে – তারপর সুযোগ বুঝে দাদাকে খুন করে তার পোশাক দাদাকে পরিয়ে দেয়। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ড্রাগপাচারকারী অ্যালেন স্বপন তার দাদার ভেক ধরে, শামসুর রহমান নাম দিয়ে দাদার বাড়িতে এসে থাকতে শুরু করে।
এই অবধি সিরিজটি যাঁরা দেখেছেন, কিংবা আমার বলা গল্প অনুসরণ করে যাঁরা কল্পনা করে নিতে চাইছেন, তাঁদের এই সিরিজটিকে গ্যাংস্টার জঁর হিসেবে বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। সিনেমার ইতিহাসে গ্যাংস্টার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জঁর – গ্যাংস্টার বা ‘ক্রাইম ফিল্ম’ নামে ডাকা এই জঁরের ইতিহাসে ফ্রান্সিস ফোর্ড কপোলার বিখ্যাত গডফাদার ট্রিলজি থেকে শুরু করে মার্টিন স্করসেসের হালের দ্য আইরিশম্যান (২০১৯) – এই সবই সিনেফিলদের পছন্দের ছবির তালিকায় প্রথম সারিতে থাকবে। শুধুমাত্র আমেরিকান ছবিতেই নয়, আমাদের এদিকে, উপমহাদেশেও এই জঁরে বেশ উন্নতমানের কাজ হয়েছে হিন্দী মূলধারার ছবিতে – রামগোপাল ভার্মার সত্যা (১৯৯৮) কিংবা অনুরাগ কাশ্যপের একাধিক ছবি এই গোত্রে পড়ে। মাইসেলফ অ্যালেন স্বপন-ও শুরু থেকে উপরে বর্ণিত কাহিনি অবধি নিঃসংকোচে গ্যাংস্টার জঁরের মধ্যে থাকে – পুলিশের তাড়া খেয়ে পালাতে থাকা কুখ্যাত ড্রাগপাচারকারী ক্রিমিনাল, নির্দ্বিধায় দাদাকে খুন করে ফেলা নির্দয় নেগেটিভ চরিত্রকে কেন্দ্রে রেখে পোড়োবাড়ি, ক্রাইম সিন, হাসপাতাল, মর্গ ইত্যাদি স্পেসে সিরিজটি সুন্দর নিজেকে সাজাতে সাজাতে এগিয়ে চলে। কিন্তু এরপরেই সিরিজে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মোড় আসে – এবং সেটিই আমাদের এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়। তাই মূল প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে আমাদের সংক্ষেপে গ্যাংস্টার জঁর সম্পর্কে দুকথা জেনে নেওয়া যাক!
******
আমরা জানি, মূলধারার ছবির ইতিহাস নিয়ে কথা বলতে গেলেই জঁর জিনিসটা খুব দ্রুত সামনের সারিতে চলে আসে। জঁর একটি ফরাসী শব্দ, যারা ইংরেজী সমার্থক হিসেবে ‘কাইন্ড’ কিংবা বাংলা সমার্থক হিসেবে ‘ধারা’ শব্দটি (আমার ব্যক্তিগত পছন্দের শব্দ যদিও ‘গোত্র’) ব্যবহার করা যেতে পারে। চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞ ব্যারি কিথ গ্রান্ট জঁর বোঝাতে গিয়ে চমৎকার একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন, যা সহজেই গোটা বিষয়টিকে এককথায় ব্যাখ্যা করে দেয় – ‘জঁর ফিল্ম সাধারণত সেই ধরণের পূর্ণদৈর্ঘ্যের বাণিজ্যিক ছবি যেগুলি একদিকে পুনরাবৃত্তি, অন্যদিকে সামান্য রদবদলের মাধ্যমে চেনা গল্প, চেনা চরিত্র এবং চেনা পরিস্থিতির মাধ্যমেই কাহিনির বিস্তার করে’১। অর্থাৎ থ্রিলার, হরর, গ্যাংস্টার, সায়েন্স ফিকশন মেলোড্রামা, মিউজিক্যাল, কমেডি – সিনেমার ক্ষেত্রে এই যে বিশেষ বিশেষ জঁর – আমরা জানি, তাদের নাম বললেই আমাদের চোখের সামনে এক ধরণের চেনা দৃশ্য, চেনা পরিসর, চেনা শব্দ এবং চেনা আইকোনোগ্রাফি; সঙ্গে একইধরণের চরিত্র, ঘটনার মোচড় ইত্যাদি ভেসে ওঠে। আমরা জানি থ্রিলার ছবি বললে সেখানে গোয়েন্দার উপস্থিতি প্রায় বাধ্যতামূলক। ওয়েস্টার্ন ছবি বললে পশ্চিম আমেরিকার ধূ ধূ প্রান্তর এবং বন্দুক হাতে ঘোড়ায় চড়া কাউবয় থাকতেই হবে। হরর ছবির ক্ষেত্রে বাস্তবের অতিরিক্ত অশরীরী কিছু প্রত্যাশা করতে আমরা অভ্যস্ত। জঁরের চেনা এলিমেন্ট বলতে এগুলোই – একদিক থেকে দেখলে ফরমুলার সঙ্গে এর খুব পার্থক্য নেই।
মূলধারার সিনেমার ইতিহাসে মূলত হলিউড স্টুডিও যখন থেকে সিনেমাকে মাস প্রোডাকশন – অর্থাৎ বৃহত্তর ইন্ডাস্ট্রির প্রোডাকশন ব্যবস্থা অবলম্বন করে একসঙ্গে অনেক সংখ্যায় উৎপাদন করা শুরু করে, তখন থেকেই জঁর ফিল্মের রমরমা। সহজ বুদ্ধিতেই বোঝা যায়, বাজারে বিক্রির জন্য যে কোনো পণ্যদ্রব্য প্রচুর মানুষের ব্যবহারের কথা ভেবে নির্মাণ করতে চাইলে তাতে একটা না একটা ছাঁচ লাগে – যেমন ফোর্ড কোম্পানীর মোটরগাড়ির প্রতিটিই নির্দিষ্ট কোনো ছাঁচ মেনে একই আকারে তৈরী। কিন্তু একই সাথে – ছাঁচ যেমন জরুরি, তেমনই জরুরি ছাঁচের মধ্যেও সামান্য পরিবর্তনের। শুধুই রিপিটেশন হলে পণ্যবাজারে দ্রব্য মূল্যবান থাকবে না, দরকার ভ্যারিয়েশন। জঁর ফিল্মের ক্ষেত্রে এই রিপিটেশন ভ্যারিয়েশনের খেলাটিই সবচেয়ে জরুরী – একটি জঁরের প্রায় সব ছবিরই ছাঁচ যেন এক – যেমন থ্রিলার বললে সেখানে ক্রাইম, ক্রিমিনাল, সাসপেন্স, গোয়েন্দা, রহস্য, তদন্ত এবং রহস্য উদ্ঘাটন – এই চেনা উপাদানগুলো আছেই। কিন্তু এর মধ্যেই শিল্পীরা তাঁদের মুনশিয়ানায় নানান ভ্যারিয়েশন তৈরী করেন – সময়ের সাথে সাথে এই ভ্যারিয়েশনের জন্যই জঁরের নানান প্রাথমিক বৈশিষ্ট্যও পালটে পালটে যায়। থ্রিলার গল্পের যেমন দীর্ঘদিনের প্রাথমিক ছাঁচ ছিল হুডানইট (whodunit?) কাঠামো – অর্থাৎ জটিল একটি নকশা বুনে ক্রিমিনালকে খুঁজে বের করাই গোয়েন্দার আসল উদ্দেশ্য। ফেলুদা-ব্যোমকেশের অধিকাংশ গল্পই এই হুডানইট ছাঁচে ফেলা। কিন্তু ক্রমশ গোয়েন্দা গল্পের বিবর্তনে এই কাঠামোর পরিবর্তে দেখা গেছে সাসপেন্সের প্রাবল্য – অর্থাৎ অপরাধ কে করেছে, তার বদলে কীভাবে অপরাধীকে ধরা হবে, সেইটিই হয়ে উঠেছে থ্রিলারের মূল আকর্ষণ বিন্দু। সত্যজিৎ স্বয়ং যখন সোনার কেল্লা অবলম্বনে ছবি করেছেন, প্রথম দৃশ্যেই অপরাধী কে, আমরা জেনে গেছি – বাকি রয়েছে সাসপেন্স – কীভাবে ফেলুদা অপরাধীকে পাকড়াও করবে। থ্রিলার জঁরের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ফিল্মমেকার আলফ্রেড হিচকক বারবারই বলতেন, কে অপরাধ করেছে সেটা তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং কীভাবে অপরাধীর মনের ভেতর ঢুকে গিয়ে তার যাত্রাপথের সঙ্গে দর্শককে একাত্ম করে তার অপরাধ শনাক্ত করা হবে – সেইটিই তাঁর ছবির প্রধান যাত্রাপথ। শ্যাডো অফ আ ডাউট (১৯৪৩) থেকে সাইকো (১৯৬০) অবধি প্রায় সমস্ত ছবিতেই আমরা গল্পের এইরকম চলন দেখতে পাই।
*****
এই প্রবন্ধে আমাদের আলোচ্য মূলত গ্যাংস্টার জঁর – কিন্তু তা সত্ত্বেও খানিক ইচ্ছে করেই ‘থ্রিলার’ নিয়ে আমি কিছু কথা বলতে চাইলাম। সাধারণত ‘থ্রিলার’ জঁর অনেকগুলো বিভিন্ন জঁরকে এক ছাতার তলায় ধরে রাখে। চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞ স্টিভ নিল তাঁর থ্রিলার সংক্রান্ত আলোচনায়২ স্পষ্ট দেখিয়েছেন – অপরাধী, অপরাধ, অপরাধের শিকার (ভিক্টিম), আইনের রক্ষক অর্থাৎ পুলিশ কিংবা গোয়েন্দা – এই ধরণের চরিত্র এবং তাদের কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া ঘটনা মূলত তিন ধরণের অপরাধকেন্দ্রিক ছবির প্রধাণ বিষয় হিসেবে উঠে আসে। তিনি থ্রিলারের ছাতার তলায় এই তিনধরণের ছবিকে নামকরণ করেছেন এইভাবে – ডিটেকটিভ ফিল্ম, গ্যাংস্টার ফিল্ম এবং সাসপেন্স থ্রিলার (ইংরেজী এই শব্দগুলির আমি বাংলা করছি না – কারণ এই ধরণের কাজ বলতে মূলত ইংরেজী ভাষার আমেরিকান ছবিই আমাদের দেখার অভ্যেস – তাই সবার কাছেই এই শব্দগুলো অত্যন্ত পরিচিত)। সিনেমার ইতিহাসের একদম শুরুরদিকের তিনটে ছবি – The Monogrammed Cigarette (1910), The Bold Bank Robbery (1904) এবং The Lonely Villa (1909) – পাশাপাশি রেখে স্টিভ নিল আমাদের মনে করিয়ে দেন যে তিনটিই অপরাধ-কেন্দ্রিক থ্রিলার গোত্রের ছবি – কিন্তু এই তিনটিতেই ছবির চলনে গুরুত্বের হেরফের হওয়ার কারণে কীভাবে আলাদা আলাদা জঁরের জন্ম নেওয়ার সম্ভাবনা দেখা গেছে। প্রথম ছবিটির মূল চলন নির্ধারিত হয় এক প্রখ্যাত গোয়েন্দার মেয়ের অপরাধ শনাক্ত করার কাহিনির মাধ্যমে। দ্বিতীয় ছবির ক্ষেত্রে প্রাথমিক গুরুত্ব দেওয়া হয় সংগঠিত অপরাধে – কীভাবে একদল ডাকাত একটি ব্যাংক লুঠ করছে। অন্যদিকে তৃতীয় ছবিতে কেন্দ্রে চলে আসে অপরাধের শিকার ভিক্টিম মানুষেরা – এক মহিলা এবং তার সন্তান ডাকাতদের হাত থেকে বাঁচতে বাড়িতে আটকে পড়ে আছে। স্টিভ নিল আমাদের দেখান – প্রথম ছবিতে গোয়েন্দা এবং অপরাধ শনাক্তকরণের প্রক্রিয়া, দ্বিতীয় ছবিতে অপরাধীদের অপরাধ করার প্রক্রিয়া এবং তৃতীয় ছবিতে ভিক্টিমদের অসহায়তা এবং শেষ মুহূর্তে তাদের উদ্ধার হওয়ার সম্ভাবনার প্রক্রিয়া, যথাক্রমে ডিটেকটিভ, গ্যাংস্টার এবং সাসপেন্স – সিনেমার ইতিহাসে এই তিনধরণের থ্রিলারের উৎস হিসেবে খুঁজে নেওয়া যায়। অর্থাৎ ছবির প্রেক্ষিতে সাদৃশ্য থাকলেও আমরা ছবিগুলিকে আলাদা করতে পারি তাদের চলন এবং ভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বের পার্থক্যের উপর।
*****
অতএব বোঝা গেল, গ্যাংস্টার জঁরের কেন্দ্রে থাকে অপরাধ, মূলত গোষ্ঠীবদ্ধ অপরাধীদের আখ্যান। গোয়েন্দা কিংবা পুলিশ সেখানে গৌণ – অপরাধী শণাক্তকরণের প্রক্রিয়াও গৌণ – মূল বিষয় অপরাধী স্বয়ং। এই প্রবন্ধে আমরা গ্যাংস্টার জঁর বিষয়ে দীর্ঘ সাধারণ আলোচনা করতে পারব না, কারণ সেই আলোচনা আমাদের আলোচ্য সিরিজ সম্পর্কে বিশেষ আলোকপাত করতে সক্ষম হবে না। সাধারণ ভাবে গ্যাংস্টার জঁরের বিখ্যাততম ছবি, গডফাদার ট্রিলজি-র কথা পাঠকদের ভাবতে অনুরোধ করি। সংগঠিত অপরাধ চক্র, তাদের আমেরিকান সমাজের সর্বস্তরে সংযোগ এবং সেই সূত্র ধরে ‘ক্ষমতা’ নামক বিষয়টিই এই (ধরণের) ছবির মূল কেন্দ্রবিন্দু। ফ্রান্সিস ফোর্ড কপোলা স্বয়ং উল্লেখ করেছিলেন, কীভাবে গডফাদারের উত্থানের মাধ্যমে আমেরিকান পুঁজিবাদের একটি রূপকধর্মী আখ্যান তিনি উপন্যাসটি পড়তে পড়তেই খুঁজে পেয়েছিলেন।
শুধুমাত্র আমেরিকান গ্যাংস্টার ছবিই নয় – অপরাধ এবং মাফিয়া চক্র যে কোনো গ্যাংস্টার ছবিরই মূল কেন্দ্রে থাকে। আমরা যদি উপমহাদেশ থেকে উদাহরণ খুঁজতে চাই – ধরা যাক ম্যাকবেথের কাহিনী অবলম্বনে বিশাল ভরদ্বাজের মকবুল (২০০৩)। এই ধরণের ছবি আধুনিক পৃথিবীর বড় বড় মেট্রোপলিটন শহরের পেটের ভিতর লুকিয়ে থাকা আরেকটি শহর – ইংরেজী ভাষায় যাকে বলে আন্ডারওয়ার্ল্ড – মূলত সেই ধরণের জগতের উপর প্রাথমিক জোর দেয়। আন্ডারওয়ার্ল্ডে থাকা পরিবারকেন্দ্রিক অপরাধ চক্র – যেখানে বংশানুক্রমে, মূলত পিতৃতান্ত্রিক ভাবে বংশের পুরুষেরা ক্রমশঃ আন্ডারওয়ার্ল্ডের রাজা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।
উদাহরণ বাড়িয়ে পাঠককে ভারাক্রান্ত করতে চাইবো না – তবে এইটুকু শুধু মাথায় রাখতে বলবো – গ্যাংস্টার ছবির আইকনোগ্রাফির৩ কথা। আমরা শুরুতেই বলেছি, যে কোনো জঁরেই আখ্যান, চলন, চরিত্রের মত আইকনোগ্রাফিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস। এদেশে কিংবা বিদেশে, গ্যাংস্টার জঁরের ক্ষেত্রে আমাদের পরিচিত ইমেজগুলির কথা আমরা জানি – যা দেখলেই কোনো ছবিকে গ্যাংস্টার বলে চেনা যায়। আন্ডারওয়ার্ল্ডের অন্ধকার, হাই কনট্রাস্ট সিনেমাটোগ্রাফির মাধ্যমে গ্যাংস্টার ছবিতে আমরা অপরাধীদের বাসস্থান দেখি, অন্ধকার রাতের শহর এবং ছুটন্ত গাড়ি সেখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সঙ্গে থাকে অপরাধ-গোষ্ঠীর নেতা এবং তার অনুগত সাঙ্গোপাঙ্গোর দল। প্রয়োজনে পরিবার, পরিজন, এবং মহিলা চরিত্র আসতে পারে, গডফাদার ট্রিলজি তে মহিলা চরিত্রদের উপস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ – কিন্তু তা আসে মূলত সংশ্লিষ্ট অপরাধ গোষ্ঠীর পিতৃতান্ত্রিক রূপটিকে বিশেষ করে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যই। এর সঙ্গেই থাকে সমাজের উচ্চতম অংশের মানুষজনদের বিনোদনের পরিসর – বেশীরভাগ গ্যাংস্টার ছবিই অপরাধী গোষ্ঠী কীভাবে উচ্চতম এবং নিম্নতম সামাজিক গোষ্ঠীকে ক্ষমতার এক সূত্রে বেঁধে রাখে, তা স্পষ্ট করে দেখাতে চায়। অর্থাৎ অত্যন্ত ধনী ব্যক্তিদের নাইটক্লাব এবং শহরের ঘিঞ্জি বস্তি কিংবা বেশ্যাপাড়া – এই আপাত দুই মেরুর পরিসর এবং আইকোনোগ্রাফির মধ্যে গ্যাংস্টার ছবির অবাধ চালচলন ঘটে থাকে।




*****



আমরা শুরুতেই উল্লেখ করেছি, মাইসেলফ অ্যালেন স্বপন বেশ সচেতনভাবেই এই ধরণের পরিসরের মধ্যে থেকে তার যাত্রা শুরু করে। প্রথম এপিসোডে শহরে না হলেও, গ্রামের আন্ডারওয়ার্ল্ড দেখতে পাই আমরা – ইললিগ্যাল ইমিগ্র্যান্ট হিসেবে মংপু নামক চরিত্রটির বাসস্থান এবং মংপুর পালিয়ে যাওয়ার পরে অ্যালেন স্বপনের লুকানো পোড়োবাড়ি – এই সবই গ্যাংস্টার ছবির আইকোনোগ্রাফি হিসেবে আমাদের চেনা ছক। কিন্তু গন্ডগোল শুরু হয় এরপরেই – দ্বিতীয় এপিসোডের শুরুতেই সিরিজটি হঠাৎই প্রায় হ্যাঁচকা টানে ঢাকা শহরের নিতান্ত মধ্যবিত্ত একটি পরিবারের দৈনন্দিনতার মধ্যে আমাদের নিয়ে আসে। এতক্ষণের আলোচনা থেকে এইটুকু আমাদের স্পষ্ট হয়েছে – গ্যাংস্টার ছবির সঙ্গে মধ্যবিত্ত সমাজের খুব একটা সম্পর্ক থাকার কথা নয়। কারণ সাতে পাঁচে না থাকা মধ্যবিত্ত সমাজ সাধারণত অপরাধচক্র কিংবা সেই ধরণের ক্ষমতার সিঁড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে থাকতেই পছন্দ করে। অ্যালেন স্বপনের যমজ দাদা শামসুর রহমানের স্ত্রী-কন্যা নিয়ে ঢাকা শহরের যে বাড়ি, সেই বাড়িও খুব স্বাভাবিক ভাবেই গ্যাংস্টার জগতের চেয়ে অনেক দূরে। কিন্তু সাত এপিসোডের এই সিরিজের প্রায় সত্তরভাগেরও বেশী অংশ – পাঁচটি এপিসোড – মূলত এই মধ্যবিত্ত বাড়ির দৈনন্দিনতার মধ্যেই আটকে। এই লেখার বাকি অংশে আমরা আপাত ভাবে এই কন্ট্রাডিকশন নিয়ে চিন্তা করতে চাইব – কীভাবে আপাদমস্তক গ্যাংস্টার ছবি হয়েও সিরিজটি নিজেকে মধ্যবিত্ত গার্হস্থ্য জীবনের আঙিনায় নিজেকে সঁপে দেয়।
সিরিজটির কাঠামো ভাষায় ব্যাখ্যা করতে গেলে ব্র্যাকেটের কথা মনে আসে। ব্র্যাকেট যেভাবে দুইদিক থেকে কোনো বাক্যকে ধরে রাখে, সেরকম ভাবেই সিরিজের শুরু আর শেষে আমরা দেখতে পাই গ্যাংস্টার ছবির আইকোনোগ্রাফি – আন্ডারওয়ার্ল্ড, অন্ধকার রাস্তা, মৃতদেহ, পুলিশি তদন্ত, অপরাধচক্র, অপরাধীদের নেতা ইত্যাদিকে। কিন্তু ব্র্যাকেটের মাঝের অংশে – এক্ষুণি আমরা যা বললাম – ছাপোষা মধ্যবিত্ত গার্হস্থ্য জীবন। আপাতভাবে গল্পের চলনে একে সহজেই বোঝা যায় – অ্যালেন তার দাদা শামসুর রহমানের ভেক ধরে অন্য জীবনে লুকিয়ে থাকতে ঢাকায় এসে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটি এই এক লাইনে বলে দিলে আসলে কিছুই বলা হয় না।
সিরিজে মধ্যবর্তী এই পাঁচটি এপিসোডের কিছু কিছু অংশের দিকে আমরা মনোনিবেশ করতে পারি। যে মুহূর্তে অ্যালেন স্বপন শামসুর রহমান সেজে দাদার বাড়িতে প্রবেশ করে, সেই মুহূর্তে থেকে ছবির ভরকেন্দ্র আগে বর্ণিত সাসপেন্সের দিকে ঘুরে যায় – অপরাধী কে আমরা জেনে গেছি – সে কি তবে আদৌ ধরা পড়বে? দর্শক তো জানে যে এই লোকটি শামসুর রহমান নয়, অ্যালেন স্বপন – কিন্তু শামসুরের স্ত্রী, সিরিজের অন্যতম প্রধাণ চরিত্র – সে তো জানে না তার স্বামীর ভেক ধরে ঘরে প্রবেশ করেছে এক আততায়ী। সে কি তবে বুঝতে পারবে?
এই সময় থেকেই সিরিজটির কেন্দ্রে চলে আসে মধ্যবিত্ত দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট ঘটনা। অ্যালেন কি তার দাদার মতো জুতো পড়েই গটগট বাড়িতে ঢুকে পড়বে? ঘরের আলমারির চাবিটা কি সে দাদার মতোই বালিশের তলায় রাখবে? চাবির গোছায় যে চাবিতে আলমারি খোলে, যা দৈনন্দিনতার অভ্যাসে দাদা একবারেই পারত, সে কি সেটা একবারে পারবে? সে কি দাদার মতো স্কুটার চালিয়ে অফিস যেতে পারবে? দীর্ঘদিনের যৌনতাহীন দাম্পত্য জীবন কী একইরকম থেকে যাবে? দাদার মতোই সে ব্রেকফাস্টে খাবার খেতে পারবে? দাদার মতোই সে মেয়েকে আদর করতে পারবে?



দর্শক হিসেবে এই প্রশ্নগুলো আমাদের একভাবে সাসপেন্সের দিকে ঠেলে দেয় বটে – কিন্তু সাসপেন্সেরও প্রাথমিক স্তরের দিকে আমরা যদি তাকাই, তাহলে একটি জরুরি পরিবর্তন দেখতে পাবো। যে গ্যাংস্টার ছবির মূল কেন্দ্রবিন্দু হত তাড়া খাওয়া অপরাধী, বন্দুকের নল কিংবা রাতের শহর, সেই গ্যাংস্টার ছবিই এখন ঘরের জুতো পরতে পারা, আলমারির চাবি খোলা, স্কুটার চালাতে পারা কিংবা না পারা, চেনা দোকানিকে শনাক্ত করতে পারার দিকে ঘুরে গেছে। আমরা জানি, মধ্যবিত্ত জীবনের এই ছোট ছোট ডিটেল সাধারণত গ্যাংস্টার ছবিতে আসার কথাই নয়, কারণ গ্যাংস্টার ছবি মধ্যবিত্ত জীবনের গল্প বলে না। অ্যালেন স্বপনের ভেক ধরার গল্পের ছুতো ধরে এই সিরিজের নির্মাতারা আমাদের সরাসরি এনে ফেলেছেন মধ্যবিত্ত জীবনের ঘেরাটোপে – আপাত শান্ত স্থির দৈনন্দিনতাতেই এবার নির্মাণ হচ্ছে রহস্যের ঘনঘটা।
গ্যাংস্টার ছবি হঠাৎ করে মধ্যবিত্ত বাস্তবতায় পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার ঘটনা আমাদের সিনেমার ইতিহাস তথা বর্তমান সম্পর্কে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু মন্তব্য তুলে ধরে। ঐতিহাসিক ভাবেই মধ্যবিত্ত জীবনের তুচ্ছ দৈনন্দিনতা যে ধরণের (জঁর নয়৪) ছবির আখ্যানে এনেছে, তা হল বাস্তবধর্মী সামাজিক আখ্যান। ইতালীয় নিওরিয়ালিস্ট ছবি উম্বের্তো ডি-র সেই বিখ্যাত রান্নাঘরের দৃশ্য আমরা সবাই দেখেছি। বাড়ির কাজ করতে করতে অল্পবয়সী কাজের মেয়েটি চুপ করে বসে আছে – ক্যামেরাও তার সঙ্গে অপেক্ষা করছে দৈনন্দিনতার ঘেরাটোপে। উপমহাদেশের ছবিতে এই ধরণের বাস্তবধর্মী আখ্যান আমরা দেখেছি সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে। সারা পৃথিবী জুড়েই বাস্তবধর্মী ছবি তার চলনে মধ্যবিত্ত কিংবা নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের দৈনন্দিনতাকে প্রধান গুরুত্ব দিয়ে এসেছে – যার চূড়ান্ত একটি রূপ পাওয়া যায় ফরাসী চলচ্চিত্রকার শাঁতাল আকেরম্যানের জঁ দিয়েলম্যান (১৯৭৫) ছবিতে।
এখন প্রশ্ন হল – দৈনন্দিনতাই যদি একটি ছবি/সিরিজের মূল বিষয় হয়, তাহলে সে কি রহস্য সৃষ্টি করতে পারে না? বাস্তবধর্মী সামাজিক ছবি সাধারণত গ্যাংস্টার থ্রিলার হয় না (অবশ্যই ব্যতিক্রম আছে), আবার অন্যদিকে গ্যাংস্টার গল্প মধ্যবিত্ত জীবন নিয়ে খুব একটা কথা বলে না। কিন্তু আমরা জানি, শিল্পে অসম্ভব বলে কিছু নেই – সব যুগের শিল্পীরাই তাঁদের নিজেদের কাজের পরিসরকে ক্রমশ উন্মুক্ত করেছেন একের সাথে অন্যকে মিশিয়ে দিয়েই। মাইসেলফ অ্যালেন স্বপন সিরিজটি খুব সচেতন ভাবেই এই মাস্টারস্ট্রোক তৈরী করে – সে গ্যাংস্টার ছবিকে মধ্যবিত্ত গৃহস্থালীর আওতায় নিয়ে চলে আসতে চায়, যা অত্যন্ত কঠিন একটি প্রক্রিয়া। এর ফলে কিছু জরুরি অর্জনও হয়, যা আমরা খানিকটা আলোচনা করার চেষ্টা করবো।
যেমন ধরা যাক একটি নির্দিষ্ট মোটিফ। অ্যালেন স্বপন যখন তার দাদার বৌকেও নিজের দলে টেনে নিয়ে যৌনতায় লিপ্ত হয়, তখন বারবার ঘরের দরজা বন্ধ করে দেওয়ার দৃশ্য আসে – ধরের বাইরে থেকে নির্মাতারা আমাদের দেখান/শোনান, দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং ভিতর থেকে দুই নারী-পুরুষের শীৎকার মিশ্রিত হাসির শব্দ ভেসে আসছে। বাড়ির অন্য যে সদস্যরা রয়েছে, তারা মাঝে মাঝেই এই দুই মানুষের দরজা বন্ধ করে দেওয়ার ঘটনায় খানিক অবাক হয় – ফলে দরজা বন্ধ করে দেওয়ার ক্রিয়াটি আরও বেশি করে আন্ডারলাইন করে দেওয়া হয়। আপাতভাবে ঘরের দরজা বন্ধ করে দেওয়ার ঘটনাটি সাধারণ মধ্যবিত্ত ডিটেল হিসেবেই আমাদের কাছে পরিচিত – কিন্তু গ্যাংস্টার ছবির ইতিহাসে এই দরজা বন্ধ করে দেওয়ার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দ্যোতনা রয়েছে।


গডফাদার ছবিটি নিয়ে শুরু থেকেই কথা বলছিলাম আমরা – এই ছবির অন্তিম লগ্নে দরজা বন্ধ করে দেওয়ার অত্যন্ত কাব্যিক এবং ইঙ্গিতপূর্ণ একটি দৃশ্য রয়েছে। আল পাচিনো অভিনীত ‘সোনি’-র চরিত্র, যে তার এককালীন প্রেমিকা ডায়ানা কিটন অভিনীত ‘কে’ নামের মেয়েটিকে কথা দিয়েছিল, তার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সব কথাই ভাগ করে নেবে – সে-ই এখন কোরলিওনে পরিবারের অধিপতি হয়ে ওঠার মুহূর্তে, পারিবারিক বেআইনি ব্যবসার কথা আড়াল করার জন্য ‘ঘর’ নামক সত্তাটিকে আলাদা করে দেয় প্রেমিকার কাছ থেকে। ঘরে থেকেও অধিপতি পুরুষের ঘরকে আলাদা করে দেওয়ার, কিংবা গ্যাংস্টার হয়ে ওঠার এই ম্যাসকুলিন যাত্রাপথে তার প্রেমিকাকে ছেঁটে ফেলার জরুরি একটি চিহ্নক হিসেবে দরজা বন্ধ করে দেওয়ার এই শটটি সিনেমার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দ্যোতনা হয়ে থেকে যাবে।
মাইসেলফ অ্যালেন স্বপন-এ, বলা বাহুল্য, দরজা বন্ধ করে দেওয়ার দ্যোতনা সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে – কিন্তু গডফাদার ছবির সঙ্গে এই অবশ্যম্ভাবী আত্মীয়তার দিকটি আমরা এড়িয়ে যেতে পারি না। একদিকে যেমন সিনেমার ইতিহাসকে নিজের শরীরে খোদাই করে রাখার সিনেফিলিক প্রচেষ্টা খুঁজে পাওয়া যায়, অন্যদিকে গ্যাংস্টার ছবির ঘরানায় থেকেও সে যে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরিবর্তনের পথে হাঁটছে, তাও আমাদের কাছে এই শটগুলির মাধ্যমেই স্পষ্ট হয়ে যায়।
কিন্তু গ্যাংস্টার ছবি হয়েও মধ্যবিত্ত দৈনন্দিনতার ঘেরাটোপে নিজেকে আটকে ফেলার যাওয়ার এই প্রক্রিয়া শুরুমাত্র সিনেফিলিক ট্রিবিউট বললে আমরা অনেকটাই ভালো করে দেখতে পাবো না। এই সক্রিয় সিদ্ধান্তে একদিকে যেমন গ্যাংস্টার জঁরেই জরুরি কিছু অন্তর্ঘাত ঘটানো সম্ভব হয়, একই সাথে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ‘ঘর’, নিরাপত্তা এবং সন্ত্রাসের ধারণাটিও৫। কিন্তু তার সাথে একইভাবে জরুরী হয়ে ওঠে বাস্তবতাবাদ (রিয়েলিজম) বিষয়ে সমকালীন বাংলাদেশ তথা দক্ষিণ এশিয়ার ছবির কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনে। এই প্রসঙ্গে সামান্য কিছু আলোচনা করেই আমরা এই প্রবন্ধের ইতি টানবো।
সিনেমার ইতিহাসে দীর্ঘকাল বাস্তবতাবাদী ছবি এবং মূলধারার ছবির মধ্যে বেশ আড়াআড়ি এক বিভাজন ছিল। ক্লাসিকাল হলিউড ছবির আপাত বাস্তবতাবাদী মোড়ক থেকে যুদ্ধ পরবর্তী ইতালির বাস্তবতাবাদী ছবিকে আলাদা করার জন্য যেমন নয়া-বাস্তববাদ (নিও রিয়েলিজম) শব্দটি ব্যবহার করা হয়। শুধু শব্দেই নয় – চলচ্চিত্রের প্রাথমিক বোধের জায়গা থেকেই মূলধারার ছবির বাস্তবতাবাদ এবং সমান্তরাল ছবির বাস্তবতাবাদ অনেকটা আলাদা ছিল। প্রথম ধরণের ছবি যদি তুচ্ছ দৈনন্দিন ডিটেলে নজর দেয়ও, তা হবে অঙ্কের নিয়মে মাপা – কোথাও কোনো বাড়তি কথার জায়গা থাকবে না। কিন্তু নয়া-বাস্তববাদী ছবি এই সাধারণ জীবনের সাধারণ ঘটনাকেই তাদের ছবির প্রধান বিষয় বলে দাবি করে – সেখানে ঘটনার গতির থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে দৈনন্দিনতার ডিটেল।
মূলত বিশ্বায়ন-পরবর্তী পৃথিবীর চলচ্চিত্র এবং পরবর্তীকালের ওয়েব সিরিজেই এই বিভাজন অনেকখানিই ধুয়ে গেছে। চলচ্চিত্রের ডিজিটাল রূপান্তর হওয়ার সাথে সাথে বেশ কিছু চলচ্চিত্রবেত্তা রিয়েলিজম জিনিসটাই বাতিলের খাতায় ফেলে দিতে চেয়েছিলেন এই যুক্তিতে, যে পোস্ট-প্রোডাকশন ম্যানিপুলেশনে এখন কম্পিউটার এবং সফটওয়্যার কার্যত চিত্রকরের কল্পনার সমতুল্য ইমেজ জন্ম দিতে পারে। যদি চলচ্চিত্রের ইনডেক্সিকাল সম্পর্কই৬ নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে আর ‘রিয়েল’ বলে কিছু থাকে কি?
কিন্তু ঘটনাচক্রে দেখা গেছে, চলচ্চিত্র এবং ওয়েব সিরিজে বাস্তববাদ জিনিসটা প্রায় নতুন রূপে ফিরে এসেছে। শুধুমাত্র সমান্তরাল ধারার ছবিই নয়, বরং মূলধারার রীতিমত ঘোষিত জঁর ছবিও ইদানীং বাস্তবতাবাদী ছবির নানান স্ট্র্যাটেজি অনুসরণ করতে শুরু করেছে। মাইসেলফ অ্যালেন স্বপন এই ধারায় শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ একটি সংযোজনই নয়, বরং বলা চলে জরুরি একটি মাত্রা – কারণ ধ্রূপদী বাস্তববাদী চলচ্চিত্রের প্রধানএকটি বৈশিষ্ট্য, মধ্যবিত্ত জীবনধারার খুঁটিনাটি-কে, সিরিজটি গল্পের প্রায় প্রাথমিক ভরকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করে। প্রকারান্তরে গ্যাংস্টার গোত্রের ছবি/সিরিজের ধারায় মাইসেলফ অ্যালেন স্বপন রীতিমত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এই সিদ্ধান্তের জন্যই – রহস্য, রোমাঞ্চ, সাসপেন্স, অপরাধ দেখানোর জন্য শুধুমাত্র চেনা ছকের চেনা আইকোনোগ্রাফিই নয়, বরং মধ্যবিত্ত গৃহস্থালীর অন্দরের ছবিও একইরকম কার্যকরী হতে পারে। গ্যাংস্টার ছবির আতঙ্ক কিংবা ত্রাসকে এই সিরিজ সদর থেকে অন্দরে টেনে আনে। এই স্ট্র্যাটেজির জন্যই নতুন ধরণের বাস্তবতাবাদী ছবি/সিরিজ নিয়ে যাঁরা চিন্তিত, মাইসেলফ অ্যালেন স্বপনতাঁদের জন্য অত্যন্ত জরুরী একটি কাজ হিসেবে গুরুত্ব পাবে।
তথ্যসূত্র ও টীকাঃ
১) ব্যারি কেইথ গ্রান্ট, “ইন্ট্রোডাকশন”, ফিল্ম জঁর রিডার, অস্টিন, ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাস প্রেস, পৃঃ ix.
২) স্টিভ নীল, জঁর অ্যান্ড হলিউড, রাটলেজঃ লন্ডন ও নিউ ইয়র্ক, পৃঃ ৬৫।
3) চলচ্চিত্রে আইকোনোগ্রাফি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস। জঁর ফিল্মের ক্ষেত্রে বারবার ব্যবহৃত হতে হতে নির্দিষ্ট ধরণের যে ইমেজ একটি জঁরের সাথে সংযুক্ত হয়ে যায়, সেই ইমেজকেই আইকোনোগ্রাফি বলা হয়। যেমন উন্মুক্ত অ্যারিজোনার রুক্ষ প্রান্তর ওয়েস্টার্নের আইকোনোগ্রাফি। মহাশূণ্য থেকে দেখা পৃথিবী, স্পেসশীপ, রকেট, মহাকাশচারী ইত্যাদিদের ইমেজ সায়েন্স ফিকশন ছবির আইকোনোগ্রাফি।
৪) ‘রিয়েলিজম’ বা বাস্তবতাবাদকে অনেকে জঁর বলেন বটে, তবে জঁরের সংজ্ঞায় রিয়েলিজমকে ফেলা যায় না। বাস্তবতাবাদ একটি ‘মোড’ হিসেবে আমরা পড়ে থাকি। যে কোনো জঁরের ছবিই বাস্তববাদী হতে পারে। কিন্তু বাস্তববাদী ছবি কোনো জঁর ছাড়াও বানানো হয়ে থাকে।
৫) সিনেমার ইতিহাসের দীর্ঘ একটা সময় জঁর ফিল্মে সদর আর অন্দরের খুব মোটাদাগের ব্যবধান ছিল। অপরাধ কেন্দ্রিক ছবিতে সদর যদি হয় দুষ্কর্ম কিংবা আতঙ্কের জায়গা, অন্দর সেখানে নিশ্চিত নিরাপত্তার ক্ষেত্র – এ মোটামুটি সাধারণ নিয়ম হিসেবে মেনে চলা হত। তবে ঠিক যেভাবে জঁরের মধ্যেই নানান ভ্যারিয়েশন হয়, সেভাবেই ঘরের মধ্যেই মূল বিপদ লুকিয়ে আছে – এই জাতীয় বিষয় নির্বাচন করে দীর্ঘদিন ধরে জঁর-ভিত্তিক সাহিত্য কিংবা সিনেমা বানানো হয়েছে। ১৯৪৬ সালের ছবি দ্য স্পাইরাল স্টেয়ারকেস এই বিষয়ে প্রথম সারিতে থাকবে। তবে সদর থেকে অন্দরে সন্ত্রাসের যাত্রা বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতার সেরা কাজ রে ব্র্যাডবেরীর লেখা ছোট্ট একটি গল্প, ‘দ্য হোল টাউন ইজ স্লিপিং’, যা ১৯৫০ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।
৬) যেকোনো বাস্তব বস্তু আর তার রিপ্রেজেন্টেশন, অর্থাৎ চিত্র, লেখা ইত্যাদি – এই দুইয়ের মধ্যে তিন ধরণের সম্পর্ক দেখা যায় (আমেরিকান ভাষাতত্ত্ববিদ সি এস পিয়ার্স এই ভাবে শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন)। আইকন, ইনডেক্স এবং সিম্বল। এর মধ্যে ইনডেক্স হল সেই ধরণের সম্পর্ক, যেখানে রিপ্রেজেন্টেশন হওয়ার জন্য বাস্তবের বস্তুটির প্রত্যক্ষ উপস্থিতি জরুরী। যেমন আঙুলের ছাপ – ছাপটি যদি রিপ্রেজেন্টেশন হয়, তাহলে রিয়েলিটি হিসেবে কোনো একটি মানুষ আছেই, ধরে নিতে হবে। ডিজিটাল রেভোল্যুশনের আগে পর্যন্ত ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রেও এই ইনডেক্সিক্যাল রিলেশনশিপ অত্যন্ত জরুরী ছিল – অর্থাৎ ফটো তুলতে গেলে বাস্তব বস্তুটির অস্তিত্ব অপরিহার্য। চলচ্চিত্রের ধ্রুপদী বাস্তবতাবাদী তত্ত্ব এই সম্পর্কের উপরজোর দিয়েই তৈরি হয়েছে।
-
ছিল সিংহ হয়ে গেল বেড়াল: অ্যাগনেস ভার্দার অবস্থান্তর ও উন্মোচনের সিনেমা

একটি নির্দিষ্ট শব্দসংখ্যার লেখার মধ্যে যেকোনও বড় মাপের শিল্পী বা তাঁর কাজের মূল্যায়ন করা নিঃসন্দেহে চ্যালেঞ্জিং। আর অ্যাগনেস ভার্দার ক্ষেত্রে এই কাজ এক কথায় অসম্ভব। তার বিভিন্ন কারণ আছে। প্রথমত, ফিল্মমেকার হিসাবে ভার্দার কর্মজীবন সাড়ে ছয় দশক জুড়ে বিস্তৃত ফলত তাঁর কাজের পরিমাণও বিপুল। এই কাজের যথাযথ এবং সামগ্রিক মূল্যায়ন যে সময় ও ব্যুৎপত্তির দাবী রাখে, তা একমাত্র একাধিক খণ্ডের পূর্ণদৈর্ঘ্যের বই পূরণ করতে পারে। দ্বিতীয়ত, শিল্পী হিসাবে অ্যাগনেস ভার্দা নিজেকে শুধুমাত্র চলচ্চিত্র মাধ্যমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। তাঁর শিল্পীজীবনের সূচনা ঘটে ফটোগ্রাফির হাত ধরে এবং চলচ্চিত্রকার হিসাবে আত্মপ্রকাশ ও খ্যাতিলাভের পরেও তিনি ফটোগ্রাফির চর্চা শুধু চালিয়েই যাননি, তাঁর সার্বিক শিল্পকর্ম ও শিল্পীসত্তার মধ্যে এই চর্চার প্রভাব নানাভাবে সুস্পষ্ট থেকেছে। আবার ফটোগ্রাফি ও সিনেমার সাথে দীর্ঘ পথচলার পরে শেষজীবনে প্রায় আচমকাই তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে ভিডিও ইন্সটলেশন আর্টিস্ট হিসাবে। সেই চর্চাও তিনি তাঁর জীবনের শেষ দশক জুড়ে টানা নিয়মিতভাবে চালিয়ে গেছেন। অর্থাৎ অ্যাগনেস ভার্দার শৈল্পিক মূল্যায়ন সদর্থে করতে গেলে, বিবিধ শিল্পমাধ্যম, তাদের চর্চার ইতিহাস, এবং এই সবের মধ্যে দিয়ে ভার্দার অনায়াস যাতায়াতকে পাঠ করতে হবে উপযুক্ত ভাবনার ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে দিয়ে। পরিশেষে, এই ফ্রেমওয়ার্কের প্রসঙ্গেই অ্যাগনেস ভার্দা বিষয়ক আলোচনার জটিলতা বেশ কিছু মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে তাঁর বিভিন্ন শিল্পমাধ্যমে সংগঠিত বিবিধ কাজের সামগ্রিকতাকে মাথায় রেখেও, অ্যাগনেস ভার্দাকে পাঠ করা কীভাবে সম্ভব? একজন ইন্টারমিডিয়াল আর্টিস্ট হিসাবে? সিনেম্যাটিক মডার্নিজমের নিরিখে? নারীবাদী অ্যাক্টিভিজমের অনুষঙ্গ ধরে একজন মহিলা শিল্পী হিসাবে? নাকি, ফরাসী নবতরঙ্গের প্রবাদপ্রতিম মুহূর্তের অন্যতম পুরোধারূপে, যা গত পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় জুড়ে গড়ে ওঠা গোদার-ত্রুফো ও কাহিয়ে পত্রিকা-কেন্দ্রিক যেই ইতিহাস চর্চা, তাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করে?
প্রবন্ধের গোড়াতেই বিস্তৃতি ও জটিলতা নিয়ে এতটা আলোচনা করার উদ্দেশ্য মূলত দুটি কারণে। প্রথমত, শুরুতেই পরিষ্কারভাবে বলে নেওয়া যে এই লেখায় উপরে আলোচিত কোনও ফ্রেমওয়ার্ক বা মেথডের প্রচেষ্টা করা হবেনা। অর্থাৎ এই প্রবন্ধে কোনও ধরণের সর্বাত্মক তত্ত্ব খাড়া করার কোনও উদ্দেশ্য নেই। বরং দু’একটি ভাবনা ও ধারণার সূত্র ধরে কিছু আলোচনা করা হবে, যার দ্বারা হয়তো অ্যাগনেস ভার্দার সিনেমার নান্দনিক ও দার্শনিক জগতে প্রবেশ করার কিছু প্রাথমিক অভিমুখ পাওয়া যেতে পারে। এই লেখা সেই অর্থে পোলেমিকাল; এখানে তত্ত্বের নৈর্ব্যক্তিকতা অন্বেষণ না করাই শ্রেয়। এই কথার সূত্রেই উপরোক্ত দ্বিতীয় কারণটি ব্যক্ত করা যেতে পারে। মূলত সিনেমার আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকলেও, এই প্রবন্ধে কোনোভাবেই ভার্দার সব ছবির উল্লেখ বা আলোচনা করা যাবে না, এবং এখানে আলোচ্য কোনও ভাবনার সূত্রই সম্ভবত তাঁর সব ছবির ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য হবে না।
২০১৯ সালের ২৯ মার্চ অ্যাগনেস ভার্দার মৃত্যুর দশ দিন আগে মুক্তি পায় তাঁর শেষ ছবি, ভার্দা বাই অ্যাগনেস। অল্পবয়সী ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতিতে একটি মাস্টার ক্লাসের আকারে এই ছবিজুড়ে আছে অ্যাগনেস ভার্দার সিনেমা ও ইমেজ নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা, তাঁর নিকট সহকর্মীদের সাথে কথোপকথন, এবং তাঁর বিবিধ কাজকে ফিরে দেখার মধ্যে দিয়ে তাঁর সিনেমা বিষয়ক ভাবনাচিন্তা ও দার্শনিক প্রতিফলন। বলা যেতে পারে তাঁর শৈল্পিক আত্মজীবনীর কাছাকাছি একটি আখ্যান। এই আলোচনায় স্বাভাবিকভাবেই উঠে আসে ১৯৬২-তে মুক্তি পাওয়া ক্লিও ফাইভ টু সেভেন-এর প্রসঙ্গ, যা বহু সমালোচক ও দর্শকের কাছে ভার্দার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় ছবি। বহুচর্চিত এই ছবি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছ। কখনও বাস্তববাদের প্রসঙ্গে, বা কখনও সিনেমায় সময়ের চলনের নিরিখে, এবং সর্বোপরি ছবির ন্যারেটিভে, ফর্মে, ও ছবি তৈরির প্রক্রিয়ায় নারীর অবস্থান ও এজেন্সির প্রশ্নে চলচ্চিত্র ইতিহাসের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ছবি ক্লিও ফাইভ টু সেভেন। ছাত্রছাত্রীদের সাথে কথোপকথনে এই ছবির প্রসঙ্গে ভার্দা বলেন যে ছবির মূল সূত্র এক ধরণের অবস্থান্তরের (Transformation)। নির্ভুল জ্যামিতির মতো দুই ভাগে বিভক্ত এই ছবিতে পপস্টার নায়িকা ক্লিওর সার্বিক অবস্থান্তর লক্ষ করা যায়। অ্যালবাম কভার বা পোস্টারজুড়ে ছেয়ে থাকা ক্লিও, অন্যের দেখার ও কামনার লক্ষ্যবস্তু থেকে ক্রমে নিজে তার পারিপার্শ্বিক বাস্তবতা অবলোকনে সক্ষম হয়। এই অবস্থান্তরের ধারণা অ্যাগনেস ভার্দার বিভিন্ন ছবিতে বিভিন্ন রূপে চেনা মোটিফের মতো ফিরে ফিরে আসে। শুধুমাত্র আখ্যানের চরিত্র নয়, ভার্দার ছবিতে বস্তু, স্পেস, শরীর, সবকিছুরই অবস্থান্তর ঘটে, এবং পালাক্রমে এই অবস্থান্তরের কারণে ছবির পরতে পরতে অর্থনির্মাণের নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়।
চিত্র ১ – ক্লিও ফাইভ টু সেভেন: ছবির মাঝামাঝি নায়িকার নিজেকে ও পারিপার্শ্বিক বাস্তবকে দেখা
আমরা যদি অ্যাগনেস ভার্দার প্রসঙ্গ থেকে বেরিয়ে এসে, চলচ্চিত্র মাধ্যমটির প্রাথমিক ভিত্তি হিসাবে ফটোগ্রাফির কথা বিবেচনা করে দেখি, তাহলে লক্ষ করা যেতে পারে যে একধরণের অবস্থান্তরের ধারণা সেখানে অন্তর্নিহিত। ফটোগ্রাফি বাস্তবের প্রত্যেক মুহূর্তকে রূপান্তরিত করে একটি জমাট-বাঁধা স্থির ইমেজে। স্থানকালের মধ্যে দিয়ে বহমান ইতিহাসের ধারাকে এক যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় থামিয়ে দিয়ে, তাকে রূপান্তরিত করে একটি স্পৃশ্য বস্তুতে (উল্লেখ্য, এখানে অবশ্যই ফটোগ্রাফির ইতিহাস ও অ্যাগনেস ভার্দার জীবনের সিংহভাগজুড়ে থাকা অ্যানালগ প্রক্রিয়ার কথাই আলোচনা হচ্ছে; ডিজিটাল প্রযুক্তির আগমনে এই অনেক ধারণাই বেশ কিছু পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাবে)। শেষ অবধি সেই ফটোগ্রাফের স্থান দেওয়ালে, খবরের কাগজের পাতায়, পারিবারিক অ্যালবামে, বা কোনও নিকটজনের বুকপকেটে, যেখানেই হোক না কেন, প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাস্তবের স্থানান্তর ও অবস্থান্তর লক্ষ্য করা যায়। এই অবস্থান্তর আবার পালাক্রমে এক অদ্ভুত অভিন্নতাও তৈরি করে। প্রত্যেক ঘটনা, আচরণ, শরীর, অভিজ্ঞতা ক্যামেরার সম্মুখীন হয়ে শাটারের চাপে আচমকাই স্থির ও বিমূর্ত হয়ে ঠাঁই পায় চতুষ্কোণ ফ্রেমের অভিন্নতায়। সুজ্যান সনট্যাগের মতে, এই আরোপিত অভিন্নতায় যা হারিয়ে যায় তা হল এই সকল মুহূর্তের নির্দিষ্ট অর্থ। তাঁর ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত বই অন ফটোগ্রাফি থেকে এই উদ্ধৃতিটি এখানে উল্লেখযোগ্য,
“Taking photographs has set up a chronic voyeuristic relation to the world which levels the meaning of all events”.
এই প্রসঙ্গে বিবেচনা করে দেখলে, ফিল্মমেকার হিসাবে অ্যাগনেস ভার্দার ভূমিকা অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। ফ্রেমবন্দী ইমেজের এই আপাত অভিন্নতা, তাঁর সচেতন মধ্যবর্তিতার ফলে নতুন নতুন সম্ভাব্য অর্থনির্মাণের স্বকীয়তা লাভ করে। বলা যেতে পারে, সিনেমা যে চলনের প্রতিশ্রুতি দেয়, তাকে ভার্দা সচেতনভাবে ব্যবহার করেন ইমেজের স্থিতাবস্থাকে স্বাধীনতা প্রদানে। অর্থাৎ তাঁর ছবির ন্যারেটিভ একটি দ্বিতীয় পর্যায়ের অবস্থান্তর সাধনে সক্ষম। একজাতীয় ফ্রি অ্যাসোসিয়েশনের বিস্তীর্ণ যুক্তিতে ভার্দার ছবির প্রতিটি মুহুর্ত, প্রতিটি ইমেজে, প্রতিটি উপাদান সর্বদাই নতুন অনুষঙ্গ খুঁজে নিয়ে অর্থনির্মাণের প্রক্রিয়ায় লিপ্ত। সেই ফ্রী অ্যাসোসিয়েশনের যুক্তি কখনও গ্রাফিক, কখনও শব্দগত বা আক্ষরিক, আবার কখনও ঐতিহাসিক। এই প্রসঙ্গে মনে করা যেতে পারে গর্ভাবস্থার উদ্বেগ নিয়ে তৈরি ডায়েরি অফ আ প্রেগন্যান্ট উওম্যান (১৯৫৮) ছবিতে পর পর দুই দৃশ্য- যেখানে গর্ভবতী নারীর পেটের কিছু ‘নান্দনিক’ ইমেজ থেকে কাট হয়ে পরবর্তী দৃশ্যে দেখা যায় একই রকম আকৃতির একটি কুমড়োকে ধারালো ছুড়ি দিয়ে কাটার ইমেজ। বিংশ শতাব্দীর আভাঁ গার্দ চর্চার অথবা আরও নির্দিষ্টভাবে লুই বুনুয়েল ও সালভাদোর দালির আঁ শিয়েন আন্দালু (১৯২৯) ছবির সেই কিংবদন্তী প্রথম দৃশ্যের প্রভাব এখানে সুস্পষ্ট। অ্যাগনেস ভার্দার সিনেমা এবং সুররিয়ালিজম, যেখানে ফটোগ্রাফির ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, নিঃসন্দেহে দীর্ঘ গবেষণা ও আলাদাভাবে বিশদ আলোচনার দাবি রাখে।
চিত্র ২ – ডায়েরি অফ আ প্রেগন্যান্ট উওম্যান: ফিল্মমেকারের চোখে অবস্থান্তরিত বাস্তব
তবে ভার্দার ছবিজুড়ে ছড়িয়ে থাকা এইরকম ফ্রি অ্যাসোসিয়েশনের অজস্র নিদর্শনের মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে তাঁর শেষের দিকে নির্মিত স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি দ্য থ্রি বাটনস (২০১৫)। সিন্ডেরেলার কাহিনির ছায়াবলম্বনে তৈরি এই ছবি রূপকথার কাঠামো থেকে বেরিয়ে আবারও এজেন্সির প্রশ্নে ফিরে যায়। ছবির নায়িকার কাছে জাদুবলে এসে পৌঁছানো গাউন দেখে প্রাথমিকভাবে মোহিত হলেও, তার মনের প্রশ্ন তাকে এই গাউনের বহিরাভরণ ভেদ করে সক্ষম করে গাউনের ‘অভ্যন্তরে’ প্রবেশ করতে। ফলস্বরূপ উঠে আসে এক অন্য সত্য; খনির ভিতরের মতো একটি স্পেস এবং সেখানে পড়ে থাকা শ্রমিকদের ব্যবহার করা জামাকাপড়, লণ্ঠন, হেলমেট, ইত্যাদি (এখানে একটি সুন্দর শব্দের খেলাও পাওয়া যায় Miner (খনির শ্রমিক) এবং Minor (অপ্রাপ্তবয়স্ক)-এর মধ্যে)। এই ম্যাজিকের মতোই, অ্যাগনেস ভার্দার সিনেমায় অবস্থান্তরের ধারণা কখনোই নিছকই আকস্মিক নয়। পারিপার্শ্বিক বাস্তব, দৈনন্দিনতায় ছড়িয়ে থাকা, বা আপাতভাবে অদৃশ্য হয়ে থাকা উপাদানের দিকে ভার্দার সিনেমা প্রাথমিকভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এবং সেই উপাদানের অবস্থান্তর বা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে, উপাদানগুলির সুনির্দিষ্ট সামাজিক ও ঐতিহাসিক ভূমিকা থেকে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে, তাদের মধ্যে নিহিত অন্যান্য সম্ভাবনাগুলি উন্মোচন করেন।
চিত্র ৩ – দ্য থ্রি বাটনস: ম্যাজিক, রূপান্তর, ও নতুন অর্থের সম্ভাবনা
যে আপাতভাবে অদৃশ্য উপাদানের কথা উপরে বলা হল, তার মধ্যে প্রায়শই অ্যাগনেস ভার্দার সিনেমার কেন্দ্রে উঠে আসে শ্রমের ধারণা। তাঁর সিনেমায় ছবি তৈরির নেপথ্যে যে গোটা কর্মকান্ড ও নির্মাণপ্রক্রিয়া, তা মাঝেমাঝেই অনাবৃত হয়। মডার্নিজমের চর্চার ইতিহাসের অতিপরিচিত এই রিফ্লেক্সিভিটির ধারণা নিঃসন্দেহে সিনেমার আদি মুহুর্ত থেকেই মূলত হলিউডের হাত ধরে গড়ে ওঠা এক ধরণের ধ্রুপদী ন্যারেটিভ ছবির বিপরীতে এক প্রতিরোধী অবস্থান। কিন্তু ভার্দার সিনেমায় এই বিশেষ ইঙ্গিতটি আপাত ক্লাসিকাল আর্ট-মডার্ন আর্টের তর্কের বাইরে গিয়ে মূলত শ্রমের প্রশ্নের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিল্পচর্চায় চিরকালই অনুপ্রেরণা, শিল্পগুণ, নান্দনিকতা, ইত্যাদির প্রশ্নের প্রাধান্য ও কৌলিন্য বেশি, শ্রমের প্রশ্ন সেখানে সদাই ব্রাত্য। এই প্রসঙ্গে হানা আরেন্টের বক্তব্য মনে করা যেতে পারে, যেখানে তিনি বলছেন — কনজিউমার সোসাইটির যে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা, সেখানে প্রত্যেক কর্মরত মানুষই শ্রমিক কারণ তাদের প্রত্যেকের শ্রমের ফলই তাৎক্ষণিক কনজাম্পশন বা ভোগের জন্য নির্ধারিত। একজন পেশাদার ফিল্মমেকার বা শিল্পী হিসাবে ভার্দা স্পষ্টতই এই ধারণার সাথে একাত্মবোধ করেন। সাধারণ ডিটেলের প্রতি ভার্দার যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, এবং তিনি যে দৈনন্দিন বাস্তবের উপাদানকেও খুঁটিয়ে দেখছেন, তার নিরিখে বলা যায় যে তিনি আবশ্যিকভাবেই সেই শ্রমের প্রশ্নের অনুসন্ধানে লিপ্ত, যে শ্রম মূলধারার ইতিহাসের ধারাবিবরণীতে অদৃশ্য। তাঁর সিনেমার সাথে কমবেশি পরিচিত সকল দর্শকই তাঁর অধিকাংশ ছবিতে হাতের ক্লোজ শটের সাথেও পরিচিত। হিচককের ক্যামিওর মতোই আলাদা করে নেওয়া হাতের ইমেজ অ্যাগনেস ভার্দার সিনেমার নান্দনিক এবং রাজনৈতিক পরিচিতি। এই শ্রমের প্রশ্নের অনুসন্ধান প্রায়শই তাঁর সিনেমাকে টেনে নিয়ে যায় প্রান্তিকতায়; প্রান্তিক স্থানে, প্রান্তিক শরীরের কাছে, এবং প্রান্তিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণে।
অবস্থান্তর, প্রান্তিকতা, ও শ্রমের ধারণাগুলি সম্ভবত সবচেয়ে পরিপূর্ণরূপে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে ২০০০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি দ্য গ্লিনারস অ্যান্ড আই-এ। এই ছবিতে মূলত দুটি প্রেরণা লক্ষ করা যায়। প্রথমত, অবশ্যই আধুনিক সময়ে দাঁড়িয়ে এই গ্লিনিং-এর প্রথাকে ঘিরে বর্তমানের বাজার অর্থনীতি, উৎপাদন, দারিদ্র্য, ক্ষুধা, ও অপচয় বিষয়ক একটি বৃহত্তর ডিসকোর্স তৈরি করা। এর বাইরে ছবির আরেকটি তুলনামূলক অনুচ্চারিত অভীষ্ট হল, সেই সময় সদ্য আগত ডিজিটাল প্রযুক্তির হাত ধরে সিনেমা নির্মাণের বিবিধ আঙ্গিকগুলির নতুন করে অন্বেষণ। দুটি আপাতভাবে ভিন্ন উদ্দেশ্য মনে হলেও, ছবিতে তারা একে অপরের পরিপূরক। ডিজিটাল প্রযুক্তির ফলে ইমেজের রেকর্ডিং-এর স্বাচ্ছন্দ্য, তার সংরক্ষণ, বা তার সম্পাদনা, প্রভৃতি সব দিকগুলিতেই আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, যা ছবি নির্মাণের চর্চা ও সিনেমার ফর্মের উপর স্থায়ী প্রভাব ফেলে। অন্যদিকে গ্লিনিং-এর প্রথা অ্যাগনেস ভার্দার এই সিনেমা চর্চাকে ঐতিহাসিকভাবে প্রাসঙ্গিক করে তোলে।
আধুনিক সিনেমার মাস্টারপিস হিসাবে স্বীকৃত এই ছবির সামগ্রিক মূল্যায়ন এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয়ের নিরিখে এই ছবির শুরুর দৃশ্যাবলী অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। ভার্দার সিনেমার চিরপরিচিত ফ্রি অ্যাসোসিয়েশনের যুক্তিতে গ্লীনার শব্দের আভিধানিক অর্থ থেকে দৃশ্য এসে পৌঁছোয় জঁ ফ্রাঁসোয়া মিলের পেন্টিং-এ। ফরাসী বিপ্লব পরবর্তী সময়ের এই শিল্পকর্মে চিত্রিত মহিলাদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, ভার্দা এই প্রথার ঐতিহাসিক প্রান্তিকতাকে আরেকবার মনে করিয়ে দেন। একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের পুরোনো ফিল্ম ক্লিপের হাত ধরে গ্লিনিং-এর স্মৃতি অয়েল পেন্টিং-এর প্রাক্-আধুনিক পরিসর থেকে বিংশ শতাব্দীতে এসে পৌঁছোয়। অবশেষে একটি আইকনিক দৃশ্যে, ভার্দা একজন একক গ্লেনেউস-এর (গ্লিনার-এর স্ত্রীরূপ) পেন্টিং-এর সামনে দাঁড়িয়ে নিজের হাতে ক্যামেরা তুলে নেন। গ্লিনার (বা গ্লেনেউস) হিসাবে তাঁর একাত্মবোধ পরিপূর্ণতা লাভ করে। বাকি ছবি জুড়ে আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন প্রান্তিক মানুষদের, এবং তাঁদের স্মৃতিচারণ ও অভিজ্ঞতার সাক্ষী হই। গ্লিনিং-এর প্রথাগত অর্থ থেকে বেরিয়ে ছবি খুঁজে বেড়ায় সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ধরণের খারিজ, বাতিল, উচ্ছিষ্ট উপাদান এবং সে-সবের উপর নির্ভরশীল অভাবী মানুষ, শিল্পী মানুষ, রাজনৈতিক মানুষ। তবে এই ছবি কখনোই দর্শকদের থেকে সহানুভূতি বা কৃপাভিক্ষা করে না, আবার প্রবল দায়িত্ববোধে জর্জরিত হয়ে নীতিশিক্ষাও দেয়না। এই ছবির প্রান্তিক মানুষেরা কোন সামাজিক ক্যাটাগরি নন, বরং ছবির নিজস্ব ছন্দ অনেক সময়ই তাঁদের ব্যক্তিগত কথা, তাঁদের পছন্দ-অপছন্দ, তাঁদের মতামত, বা তাঁদের শখ ও খেয়ালের প্রতিও একইরকম যত্নশীল। এই প্রতিটি স্বতন্ত্র চরিত্র একটি সূত্রেই বাঁধা পড়ে: একটি বৃহৎ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার স্বার্থে এঁদের মজুরিহীন শ্রম। এবং আপাতদৃষ্টিতে, গোটা ছবির আপাত যে অসম ফর্ম, তার মধ্যেও একমাত্র যোগসূত্র হল ভার্দার ফিল্মমেকার হিসাবে শ্রম, দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত অবধি তাঁর যাতায়াত, বিভিন্ন দৃশ্যে তাঁর নানারকম কায়িক কার্যকলাপ, ইত্যাদি — যা পুনরায় মনে করিয়ে দেয় যে শিল্পজগৎ ও শৈল্পিকচর্চায় শ্রমের ধারণা প্রান্তিক ও অদৃশ্য। একটি অভিধানের পৃষ্ঠা থেকে একটি শব্দ এই ছবিতে অবস্থান্তরিত হয়ে ক্রমে ইতিহাসের এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের পরতে পরতে শ্রম ও প্রান্তিকতাকে উন্মোচিত করে।
চিত্র ৪ – দ্য গ্লিনারস অ্যান্ড আই: শব্দ সংগ্রহ, অবশিষ্ট সংগ্রহ, ইমেজ সংগ্রহ
অন্যদিকে ডিজিটাল প্রযুক্তির হাত ধরে সচেতনভাবে অ্যাগনেস ভার্দা যেভাবে ছবিজুড়ে নিজের শ্রমকে ‘ইমেজের জন্য গ্লিনিং’ হিসাবে আখ্যা দেন, তাতে ভার্দার সিনেমার যে বিবিধ পরিসরগুলি, যেমন ব্যক্তিগত বা গার্হস্থ্য, নান্দনিক বা শৈল্পিক, অথবা সামাজিক বা রাজনৈতিক, সবই একটি নির্দিষ্ট ধারণার অন্তর্গত হয়ে ওঠে। এই ছবি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে কনটেম্পোরারি ফিল্ম ডিরেক্টরস সিরিজের অ্যাগনেস ভার্দা শীর্ষক বইতে কেলি কনওয়ে লিখছেন,
“Figures that might be marginalized in another sort of documentary the homeless, the alcoholic, the poor—are elevated by the film’s insertion of them into a distinguished pictorial universe that includes the paintings of Millet, Jules Breton, Rembrandt van Rijn, and Rogier van der Weyden as well as the photographs of Etienne-Jules Marey.”
এই উদ্ধৃতিতে “elevation” এবং “distinguished pictorial universe”-এর মতো শব্দবন্ধের ব্যবহারে যে প্রকট রক্ষণশীলতা আছে, তাকে সাময়িক উপেক্ষা করে তিনি যে ধারণাটি ব্যক্ত করার চেষ্টা করছেন, সেদিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে, যে আপাতভাবে সাযুজ্যহীন ইমেজের সারি একত্রিত হয়ে সঙ্গতি লাভ করছে শুধুমাত্র এক গ্লেনেউসের প্রচেষ্টার ফলে। চলচ্চিত্রকার হিসাবে এই বৃত্তি মনে করিয়ে দেয় ওয়াল্টার বেনিয়ামিনের সংগ্রাহকের (collector) ধারণাকে। বেনিয়ামিনের মতে একমাত্র সংগ্রাহকের হাতেই সংগ্রহের উপাদান, তার বাজারদর বা ব্যবহারিক মূল্যের পরিসর থেকে মুক্তি পায়। সংগ্রহের উপাদান ও সংগ্রাহকের সম্পর্ক সেখানে একান্তই ব্যক্তিগত; সংগ্রাহকের অভ্যাস ব্যতীত সেখানে আর কোনও অনুক্রমের যুক্তি খাটে না। ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহারে, ভার্দার হাতে সিনেমার সেই দিগন্ত উন্মোচিত হয়, যেখানে ইমেজ এবং ইমেজ সংগ্রাহকের সম্পর্ক সত্যিই ব্যক্তিগত। বেনিয়ামিনের সংগ্রহের মতোই ভার্দার ‘গ্লিন’ করা ইমেজে নির্মিত ছবিতে ছবির যেকোনও উপাদান, যেমন আখ্যান, চরিত্র, সংলাপ, ক্যামেরার কাজ, সম্পাদনা, ইত্যাদি সবকিছুর মধ্যেই তাদের সুনির্দিষ্ট অনুষঙ্গের থেকে বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষণীয়। সেই কারণেই হয়তো অ্যাগনেস ভার্দার সিনেমায় তিনি সেই দৃষ্টিকে গুরুত্ব দেন, যা দিয়ে প্যারিসের দীর্ঘ রাজনৈতিক ইতিহাসের ঐতিহ্যবাহী সিংহের ভাস্কর্য মুহূর্তেইবদলে যেতে পারে এক সুবিশাল মার্জারে। ২০০৩ সালে তৈরি শর্টফিল্ম দ্য ভ্যানিশিং লায়ন-এর শেষ দৃশ্যে ভার্দার পোষ্য গুগুর (Zgougou) আবির্ভাব যেমন ম্যাজিক আবার তেমনই দৈনন্দিন ইমেজের উপাদানের মধ্যে নিহিত সম্ভাবনাকে সিনেমায় উন্মোচিত করাও বটে। কেউ বলতে পারেন ব্যক্তিগত দ্বারা রাজনৈতিক পরিসরকে প্রতিস্থাপন করা। কিন্তু সে তো কেবল এই ছবি নয়; অ্যাগনেস ভার্দার সব ছবিই রাজনৈতিক কারণ সেগুলি সবই একান্ত ব্যক্তিগত।
চিত্র ৫ – দ্য ভ্যানিশিং লায়ন: ছিল সিংহ হয়ে গেল বেড়াল
উল্লেখপঞ্জি
1. Sontag, Susan, 2011. On Photography. Picador, New York. eBook Edition
2. Arendt, Hannah, 1998. The Human Condition. The University of Chicago Press, Ltd., London. 2nd Edition
3. Benjamin, Walter, 2007. Illuminations: Essays and Reflections. Schocken Books, New York. 1968 Reprint
4. Conway, Kelley, 2015. Agnès Varda. University of Illinois Press, Urbana, Chicago, and Springfield. 1st Edition
(লেখাটি এর আগে বামা পত্রিকায় ২০২১ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। এখন অনলাইনে শুধুমাত্র এই লিংকেই পড়া যাবে)
